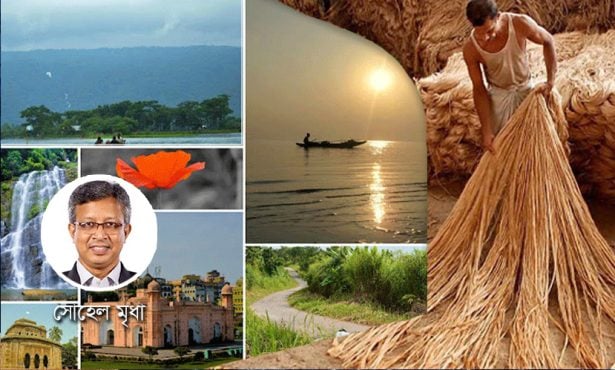বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ই-কমার্স খাত এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এটি কেবল নতুন কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করছে না, বরং দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময়, যখন অফলাইন ব্যবসাগুলো স্থবির হয়ে পড়েছিল, তখন ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সময়ে অনলাইন কেনাকাটার প্রতি ক্রেতাদের আস্থা বেড়েছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তারা এই খাতে যুক্ত হয়েছেন।
সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালের শেষে বাংলাদেশের ই-কমার্স বাজারের আকার ছিল প্রায় ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০২৬ সাল নাগাদ ১০.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হতে পারে। এই খাতে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন লক্ষ লক্ষ উদ্যোক্তা, যাদের মধ্যে একটি বিশাল অংশই ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা (এসএমই) এবং অনলাইন ভিত্তিক এফ-কমার্স বিক্রেতা।
কিন্তু এই সম্ভাবনাময় খাতটি বর্তমানে ভ্যাট এবং ট্যাক্স-সংক্রান্ত জটিলতার এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি, যা অনেক সম্ভাবনাময় উদ্যোগকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করছে। ভ্যাট ও ট্যাক্সের চাপ, সুস্পষ্ট নীতির অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতা এই উদ্যোক্তাদের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রতিবেদনটিতে বাংলাদেশের ই-কমার্স উদ্যোক্তাদের ওপর ভ্যাট ও ট্যাক্সের প্রভাব, এর পেছনের পরিসংখ্যান এবং এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
ই-কমার্স খাতে ভ্যাট-ট্যাক্সের বাস্তবতা: পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ _
ই-কমার্সের মতো একটি আধুনিক ও গতিশীল খাতকে প্রথাগত ব্যবসার মতো একই মানদণ্ডে মূল্যায়ন করা হচ্ছে, যা এর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশেষ করে, ভ্যাট ও ট্যাক্সের চাপ ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য এক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ভ্যাট আরোপের ইতিহাস ও বর্তমান চিত্র: ই-কমার্স খাত কখনোই ভ্যাট ও ট্যাক্সের আওতামুক্ত ছিল না। ২০১৯ সালের নতুন ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক আইন অনুযায়ী, ই-কমার্স বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ওপর ১৫% হারে ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়াও, ভার্চুয়াল ব্যবসাগুলোকে (যেমন: ডিজিটাল কনটেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং ইত্যাদি) ৫% হারে ভ্যাটের আওতায় আনা হয়েছে। কাগজে-কলমে এই হারগুলো সুনির্দিষ্ট মনে হলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিয়ে রয়েছে বহুবিধ জটিলতা।
ভ্যাট নিবন্ধন ও প্রতিপালনের চাপ: বর্তমানে, বার্ষিক লেনদেন ৩০ লক্ষ টাকার বেশি হলেই ভ্যাট নিবন্ধন বাধ্যতামূলক। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইক্যাব) এর তথ্য অনুযায়ী, দেশে নিবন্ধিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হাজার তিনেক হলেও, ফেসবুক ভিত্তিক বিক্রেতা বা এফ-কমার্স উদ্যোক্তার সংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষের বেশি। এদের অধিকাংশই নারী উদ্যোক্তা, যাদের ভ্যাট নিবন্ধন এবং মাসিক রিটার্ন দাখিলের মতো জটিল প্রক্রিয়া সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই। এই প্রক্রিয়াগুলো এতটাই জটিল যে, এর জন্য হিসাবরক্ষক বা পরামর্শকের সাহায্য নেয়া আবশ্যক, যা ছোট উদ্যোক্তাদের জন্য বাড়তি আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে। এই চাপ সামলাতে না পেরে অনেকেই ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন।
ভ্যাট ও ট্যাক্সের দ্বৈত চাপ: ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়শই দ্বৈত করের শিকার হয়। যেমন- একজন বিক্রেতা যখন একটি মার্কেটপ্লেস (যেমন: দারাজ, চালডাল ও অন্যান্য ) ব্যবহার করে পণ্য বিক্রি করেন, তখন প্ল্যাটফর্মটি বিক্রেতার থেকে ১৫ শতাংশ ভ্যাট কেটে নেয়। একই সঙ্গে, বিক্রেতাকে তার লাভের ওপর আবার আয়কর দিতে হয়। এতে করে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতারা নিরুৎসাহিত হয়, যা সামগ্রিক বাজারের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
বিভিন্ন প্রকার অনলাইন ও ই-কমার্স ব্যবসার ওপর প্রভাব _
ভ্যাট ও ট্যাক্স নীতিমালা সকল অনলাইন ব্যবসার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়, যার ফলে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোক্তা বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন।
পণ্য কেনাবেচা (ই-কমার্স এবং এফ- কমার্স): সরাসরি পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে ভ্যাট সরাসরি পণ্যের মূল্যের ওপর যুক্ত হয়। যখন একজন ক্রেতা অনলাইনে ১০০ টাকার একটি পণ্য কেনেন, তখন তাকে ১৫ শতাংশ ভ্যাটসহ ১১৫ টাকা পরিশোধ করতে হয়। এই বাড়তি খরচ অনেক ক্রেতাকে অনলাইন কেনাকাটা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যা ছোট বিক্রেতাদের জন্য সরাসরি ক্ষতির কারণ। অন্যদিকে, এফ-কমার্স উদ্যোক্তারা প্রায়শই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের বাইরে থেকে ব্যবসা পরিচালনা করেন, যা আইনত সঠিক না হলেও, প্রশাসনিক জটিলতা এড়ানোর জন্য তাদের জন্য একটি কৌশল।
অনলাইন সেবা প্রদান (সার্ভিস বেজড ই-কমার্স): ডিজিটাল সার্ভিস, যেমন- ডিজিটাল মার্কেটিং, সফটওয়্যার বা আইটি সার্ভিস, কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট এগুলোর ওপরও ভ্যাট আরোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, সরকারের পক্ষ থেকে ৫ শতাংশ ভ্যাট নির্ধারণ করা হলেও, বিভিন্ন জটিলতার কারণে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করা হয়। এই সমস্যাগুলো ডিজিটাল সেবা প্রদানকারী ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যবসা পরিচালনা কঠিন করে তোলে।
পেমেন্ট গেটওয়ে এবং অন্যান্য সার্ভিস: পেমেন্ট গেটওয়েগুলোও সেবার বিনিময়ে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ কেটে নেয়, যার ওপরও ভ্যাট প্রযোজ্য। এই অতিরিক্ত খরচ অনলাইন লেনদেনের খরচ বাড়িয়ে দেয়, যা নগদ লেনদেনকে উৎসাহিত করে। বাংলাদেশে এখনও প্রায় ৭৫% ই-কমার্স লেনদেন ক্যাশ অন ডেলিভারির মাধ্যমে হয়, যার অন্যতম প্রধান কারণ হলো ডিজিটাল পেমেন্টের ওপর অতিরিক্ত খরচ।
আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয় _
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটকে আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য অন্যান্য দেশের ই-কমার্স ভ্যাট-ট্যাক্স নীতির দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের ই-কমার্স খাতকে উৎসাহিত করতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। যেমন- অনেক দেশেই একটি নির্দিষ্ট আয়ের সীমা পর্যন্ত অনলাইন বিক্রেতাদের ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এটি তাদের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যবসা সম্প্রসারণে সাহায্য করে। এই দেশগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলাদেশ একটি সুনির্দিষ্ট ও সহায়ক ভ্যাট কাঠামো প্রণয়ন করতে পারে।
আর্থিক প্রভাবের বিশ্লেষণ: ভ্যাট ও ট্যাক্সের কারণে পণ্যের চূড়ান্ত মূল্য কতটা বাড়ছে এবং এটি ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতার ওপর কীভাবে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তা সংখ্যা দিয়ে বোঝালে এই সমস্যার গভীরতা আরও স্পষ্ট হবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পণ্য ১০০ টাকায় বিক্রি হলে ভ্যাট-ট্যাক্সসহ এর মূল্য ১১৫ টাকা হয়, যার ফলে অনেক ক্রেতা এটি কিনতে নিরুৎসাহিত হতে পারেন। এটি কেবল বিক্রেতার ক্ষতি নয়, বরং সামগ্রিক অর্থনীতির জন্যও নেতিবাচক।
উত্তরণের উপায়: সহযোগীকরণ ও সহজীকরণ _
ই-কমার্সকে দেশের অর্থনীতির মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে হলে ভ্যাট ও ট্যাক্স-সংক্রান্ত নীতিমালায় একটি আমূল পরিবর্তন আনা জরুরি। কিছু কার্যকর পদক্ষেপ এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে পারে-
একটি নির্দিষ্ট, স্তরভিত্তিক ভ্যাট কাঠামো: ই-কমার্স খাতের জন্য একটি নির্দিষ্ট, স্তরভিত্তিক ভ্যাট কাঠামো প্রস্তাব করা যেতে পারে। যেমন, ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয়ের জন্য শুন্য শতাংশ ভ্যাট, ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ৫ শতাংশ এবং তার ওপর ১৫ শতাংশ। এতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা উপকৃত হবেন।
প্রশাসনিক সরলীকরণ: ভ্যাট নিবন্ধন ও মাসিক রিটার্ন দাখিলের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইন এবং সহজ করা প্রয়োজন। একটি ব্যবহারকারী-বান্ধব প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে ছোট উদ্যোক্তারা সহজে এবং স্বল্প সময়ে তাদের ভ্যাট-সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। এই ক্ষেত্রে অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।
সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন: সরকারের উচিত ই-কমার্স খাতের জন্য একটি আলাদা ও সুনির্দিষ্ট ভ্যাট নীতি প্রণয়ন করা। এই নীতিতে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, বিক্রেতা, এবং ডেলিভারি সার্ভিস প্রদানকারীদের জন্য আলাদা আলাদা ভ্যাট কোড এবং নিয়ম থাকতে হবে। এটি দ্বৈত করের মতো জটিলতা নিরসন করবে এবং সকল পক্ষের জন্য একটি স্বচ্ছ পরিবেশ তৈরি করবে।
প্রণোদনা ও সহযোগিতা: নতুন অনলাইন উদ্যোগগুলোকে প্রথম ২-৩ বছরের জন্য কর অবকাশ প্রদান করা যেতে পারে। এটি তাদের বাজার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান তৈরিতে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে, নারী উদ্যোক্তা ও প্রান্তিক অনলাইন বিক্রেতাদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা উচিত।
বাংলাদেশে ই-কমার্স খাত কেবল একটি ব্যবসা নয়, এটি ডিজিটাল রুপান্তরের স্বপ্ন বাস্তবায়নের এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী এবং নারী উদ্যোক্তা এই খাতের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ভ্যাট ও ট্যাক্সের বেড়াজাল তাদের এই পথচলাকে কঠিন করে তুলছে। যদি এই চাপ অব্যাহত থাকে, তবে আমাদের এই সম্ভাবনাময় খাতটি তার পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হবে।
সরকারের উচিত, ই-কমার্সকে একটি উদীয়মান খাত হিসেবে বিবেচনা করে তার জন্য সহযোগিতামূলক নীতি প্রণয়ন করা। একটি সহজ, স্বচ্ছ এবং সহায়ক ভ্যাট ও ট্যাক্স কাঠামো তৈরি করা গেলে বাংলাদেশের ই-কমার্স খাত আরও দ্রুত প্রসারিত হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।
লেখক: প্রতিষ্ঠাতা কিনলে ডটকম, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ই-ক্যাব