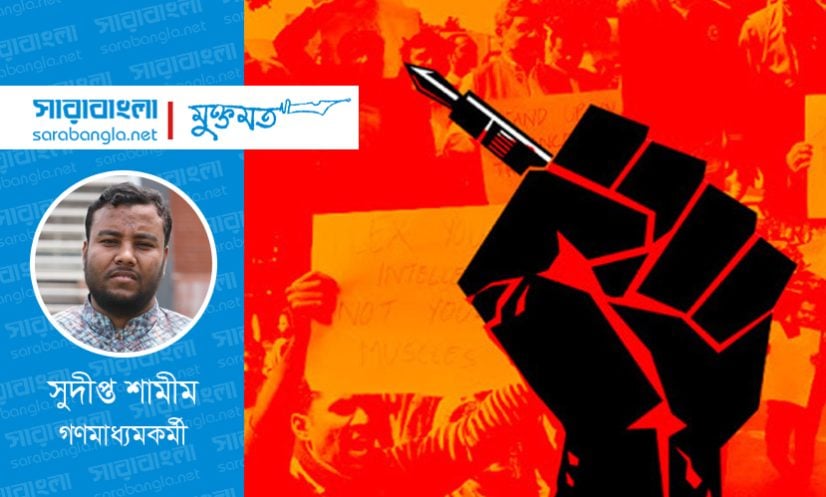মফস্বলের সাংবাদিকতা কোনো চাকরি নয়, এ যেন এক মানসিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। শহরের ঝলমলে প্রেস কনফারেন্স বা চায়ের আড্ডার সাংবাদিকতা থেকে আলাদা এ জগত। এখানে নেই স্বস্তির ঘরোয়া অফিস, নেই গাড়ি, নেই মাসশেষের নিশ্চিত বেতন। আছে কাঁদাপথ, চরের বালু, নদীর স্রোত, মাঠের জোৎস্না আর মানুষের জীবনের রুক্ষ সত্য। আর সেই রুক্ষ বাস্তবতার আলেখ্য লেখে একদল অবহেলিত কিন্তু অদম্য মানুষ- মফস্বলের সাংবাদিকেরা।
তারা পেশায় আসেন না চাকরি খুঁজতে, আসেন মানুষের কথা বলার দায়ে। এসেই জড়িয়ে পড়েন এক অনিরাপদ যুদ্ধের ভেতরে, যেখানে প্রতিপক্ষ হতে পারে স্থানীয় চাঁদাবাজ, রাজনৈতিক দস্যু, প্রভাবশালী ভূমিখেকো, এমনকি প্রশাসনের কোনো একাংশও। একদিন সকালবেলায় তারা হাঁটেন সাইকেল চেপে নদীপাড়ের দুর্গম গ্রামে, আর রাত নেমে আসে তাদের ফিরতি পথেও। হাতে থাকে শুধু মোবাইল ফোন, ভাঙা হেডফোন আর ঝাঁপসা ক্যামেরার আলো।
এই সাংবাদিকেরা যেসব সংবাদ সংগ্রহ করেন, তার অনেকগুলিই পরে ঢাকার সাংবাদিকদের নামে চলে যায়। আর প্রকৃত সংগ্রাহকের নামটি লুকিয়ে যায় ফাইলের শেষ লাইনে—যেন তিনিই অপ্রাসঙ্গিক! একবার এক মফস্বল সাংবাদিক ‘চর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের ধাক্কা’ নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন। প্রতিবেদনটি পাঠানোর পর তিনদিন তাকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। পরে জানা যায়, নদীর ওপাড় থেকে ফেরার পথে তিনি ধরা পড়েছিলেন স্থানীয় চাঁদাবাজদের হাতে, কারণ তারা চাইছিলেন খবর যেন চাপা পড়ে। অথচ সেই সংবাদ ছাপা হলো ঢাকার একজন ‘জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদকের’ নামে।
অনেকে মনে করেন সাংবাদিকতা একটি গ্ল্যামার-পূর্ণ পেশা। কিন্তু মফস্বলে এই পেশা মানে– অস্পষ্ট পরিচিতি, অবহেলিত মর্যাদা আর চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রতিদিন বেঁচে থাকা। কোন পত্রিকা ‘প্রতিনিধি কার্ড’ দিলেও, সেটির পেছনে নেই কোনো দায়িত্বশীলতা, নেই কোনো সুরক্ষা। ফোনের মেসেজে বলা হয়—‘এই রিপোর্টটা চাই কাল সকাল ৯টার মধ্যে।’ অথচ খবর সংগ্রহ করে, নিজের টাকায় মোবাইল ডেটা কিনে, ক্যাপশন লিখে, ফটো এডিট করে, সব পাঠানোর পরও তাদের বলা হয়—‘দেখা যাক, ছাপা হবে কিনা।’
এই অবহেলার নির্মমতা সবচেয়ে বেশি টের পাওয়া যায় কোনো দুঃসময়ে। একজন সাংবাদিক বন্যার পানিতে ভিজে, বুকসমান জলে হেঁটে খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে অসুস্থ হন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তিনি পত্রিকা অফিসে জানালে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ তো দূরের কথা, বরং জিজ্ঞেস করা হয়—‘আপনার বদলি কে পাঠাবে রিপোর্ট?’
প্রেস ক্লাব- যা হওয়ার কথা ছিল সাংবাদিকদের সংগঠিত ও রক্ষাকারী প্ল্যাটফর্ম– তাও অনেক জায়গায় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ভাগাভাগির আসর। যেখানে পদ-পদবি ভাগ হয় দলের ভিত্তিতে, সমস্যা সমাধান নয়। অনেকে ক্লাব গঠন করে একে রাজনৈতিক পদে যাওয়ার সিঁড়ি বানিয়েছেন। তাই কোনো সাংবাদিক হুমকির মুখে পড়লেও, মামলা হলে বা হামলার শিকার হলেও, তার পাশে দাঁড়ায় না কেউ। বরং ক্লাবের ‘সভাপতি’ ফোন বন্ধ করে দেন, সম্পাদক ‘ব্যস্ত’ হয়ে পড়েন।
পারিবারিক দিকও এখানে বিবেচ্য। একজন মফস্বল সাংবাদিকের ঘরে যখন নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটে না, সন্তান স্কুলে যেতে চায় নতুন ব্যাগে কিন্তু তার পিতা দিতে পারেন না– তখন পরিবার সেই পেশাটিকেই দোষারোপ করে। স্ত্রী চোখের কোণে কান্না লুকিয়ে বলে, ‘বাচ্চার দুধটা তো আনো, খবর পরে লিখো।’ এই বাস্তবতা সেই সাংবাদিক জানেন, যার দিনরাত কেটেছে জনগণের অধিকার নিয়ে লিখতে লিখতে নিজের অধিকারই উপেক্ষিত হয়েছে।
সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয়– জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে মঞ্চে বসে বড় সাংবাদিকরা মফস্বলের ‘অবদান’ নিয়ে বক্তৃতা দেন, কিন্তু ক’জন তাদের প্রয়োজনীয় বেতন কাঠামো কিংবা স্বাস্থ্যের সুরক্ষার জন্য চাপ দেন মিডিয়া মালিকদের ওপর? মফস্বল সাংবাদিকদের জন্য নেই স্বাস্থ্য বীমা, নেই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, নেই প্রযুক্তি উন্নয়নের ব্যবস্থা। অথচ এই সাংবাদিকই প্রথম চোখে দেখেন নদীভাঙনের হাহাকার, কৃষকের কান্না, বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবন, কিংবা সমাজে নারীর লাঞ্ছনা।
এর সমাধান কী? শুধু সাংবাদিকের অভ্যন্তরীণ শক্তিই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন রাষ্ট্রের, মিডিয়া হাউসের ও সমাজের সম্মিলিত সচেতনতা। কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হতে পারে _
ন্যায্য পারিশ্রমিক ও নিয়োগ কাঠামো
মফস্বল সাংবাদিকদের অধিকাংশই স্বেচ্ছাশ্রমে কাজ করে থাকেন, কোনো নির্ধারিত বেতন ছাড়াই। অনেকেই দীর্ঘদিন কাজ করেও কোনো নিয়োগপত্র পান না, ফলে আইনত তাদের অবস্থান দুর্বল থাকে। একটি আদর্শ কাঠামোতে সাংবাদিকদের একটি লিখিত নিয়োগপত্র থাকতে হবে, যেখানে দায়িত্ব, অধিকার, সম্মানী ও সুবিধাসমূহ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে। পত্রিকা অফিসগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে মাসিক সম্মানী প্রদান করতে হবে, কাজের মান অনুযায়ী মূল্যায়নের সুযোগ রাখতে হবে। এটি সাংবাদিকের পেশাগত মানসিকতা এবং জীবনমান উভয়ই উন্নত করবে।
আইনি সুরক্ষা ও বীমা কাভারেজ
সাংবাদিকদের ওপর হামলা, হুমকি ও হয়রানি এখন নিত্যদিনের ঘটনা। বিশেষ করে মফস্বলের সাংবাদিকরা রাজনৈতিক বা প্রভাবশালী মহলের খবর করলে হামলার শিকার হন। এ অবস্থার পরিবর্তনে প্রত্যেক জেলার প্রশাসনের অধীনে একটি ‘সাংবাদিক সুরক্ষা সেল’ গঠন করা দরকার, যেখানে সাংবাদিকরা দ্রুত সহায়তা চাইতে পারবেন। পাশাপাশি প্রত্যেক সাংবাদিকের জন্য স্বাস্থ্যবীমা ও দুর্ঘটনাবীমা চালু করতে হবে, যা কোনো বিপদে অন্তত ন্যূনতম সহায়তা নিশ্চিত করবে। মিডিয়া হাউসগুলোও তাদের প্রতিনিধিদের এই সুবিধা দিতে বাধ্য থাকবে—এমন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহায়তা
প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের যুগে সাংবাদিকতাও আধুনিক দক্ষতা ও টুলসের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। অথচ মফস্বল সাংবাদিকদের অনেকেই এখনো পুরনো ধ্যানধারণা নিয়ে কাজ করেন। তাই তাদের জন্য মোবাইল সাংবাদিকতা, ভিডিও এডিটিং, ফ্যাক্ট চেকিং, ডেটা বিশ্লেষণ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা—এই সব বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করা জরুরি। এ ছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে প্রযুক্তি সহায়তা হিসেবে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা ইন্টারনেট ভাতা প্রদানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।
স্থানীয় সংগঠনগুলোর শুদ্ধিকরণ
অনেক মফস্বল প্রেস ক্লাব এখন ব্যক্তি-স্বার্থ ও রাজনৈতিক প্রভাবের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছে। এতে সাংবাদিকদের পেশাগত ঐক্য ও স্বার্থ রক্ষা দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রেস ক্লাব পরিচালনায় স্বচ্ছ নির্বাচন, নিরপেক্ষ নেতৃত্ব ও গঠনতন্ত্র অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সাংবাদিকদের পেশাগত উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণে প্রেস ক্লাবগুলোর ভুমিকা বাড়াতে হবে। নিয়মিত সেমিনার, আলোচনা সভা এবং জরুরি সহায়তা প্রকল্প চালু থাকাও জরুরি। এ ছাড়া ক্লাবের আর্থিক স্বচ্ছতা এবং সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পরিচালনার সংস্কৃতি চালু করতে হবে।
রাষ্ট্রীয় তহবিল ও মিডিয়া কাউন্সিল
তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কেন্দ্রীয় ‘সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল’ গঠন করা যেতে পারে, যেটি অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, আইনি হয়রানি বা জরুরি পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা দেবে। এ তহবিলে আবেদনপ্রক্রিয়া সহজ করতে হবে এবং মফস্বলের সাংবাদিকদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। পাশাপাশি একটি স্বাধীন মিডিয়া কাউন্সিল গঠন করে সাংবাদিকদের অভিযোগ, হয়রানি, পারিশ্রমিক ও আচরণবিধি সংক্রান্ত বিষয়গুলো সুষ্ঠুভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাউন্সিল গণমাধ্যমের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণেও ভূমিকা রাখতে পারে।
সামাজিক সম্মান ও সচেতনতা
মফস্বল সাংবাদিকদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক সময়ই নেতিবাচক। অনেকেই মনে করেন, তারা ‘বিনা কারণে ছবি তোলে’ বা ‘খবর দিয়ে লাভ করে’। এই ভুল ধারণা দূর করতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, শিক্ষক, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে। গণমাধ্যম যে সমাজের দর্পণ ও গণতন্ত্রের হাতিয়ার, তা বোঝাতে স্কুল, কলেজ ও সামাজিক অনুষ্ঠানে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। পাশাপাশি সংবাদকর্মীদের সম্মান জানাতে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে বার্ষিক ‘সাংবাদিক সম্মাননা’ অনুষ্ঠান আয়োজন করাও ফলপ্রসূ হতে পারে।
সবশেষে মফস্বলের সাংবাদিকদের নিজেদের মাঝেও একটি শক্ত ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এ লড়াই সহজ নয়। প্রয়োজনে স্থানীয় সাংবাদিকরা নিজেরাই একটি ট্রাস্ট বা সহায়তা তহবিল গঠন করতে পারেন, যেখানে বিপদে কেউ পড়লে অন্যরা পাশে দাঁড়াতে পারে।
এই কঠিন সময়েও যারা শুধু সত্য বলার দায়ে কাদামাটি মাড়িয়ে, নদী পেরিয়ে, পকেট খালি করে, গলা শুকিয়ে খবর পাঠান—তারা শুধু সাংবাদিক নন, তারা ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষী। রাষ্ট্র যদি তাদের পাশে না দাঁড়ায়, তবে ইতিহাস একদিন রাষ্ট্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে।
লেখক: কলামিস্ট, গণমাধ্যমকর্মী ও সংগঠক