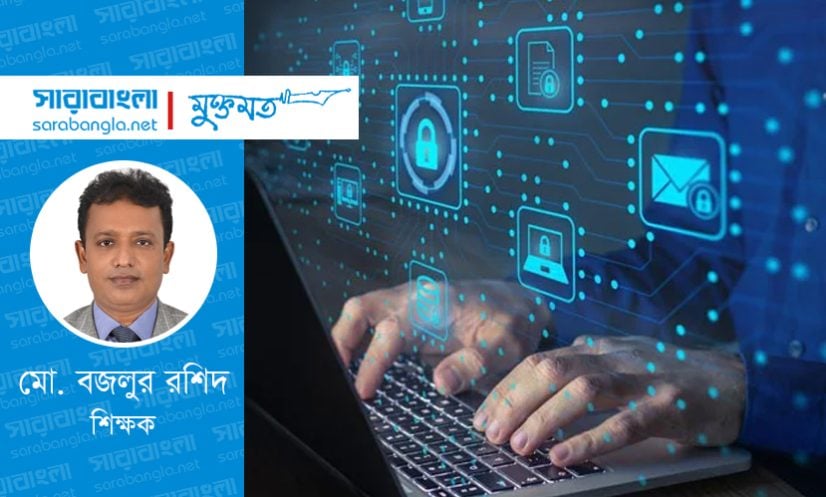বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমাজবিজ্ঞানে ম্যানুয়েল কাস্টেলসের ‘নেটওয়ার্ক সমাজ’ তত্ত্বটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই তত্ত্বটি সমসাময়িক সমাজের মৌলিক পরিবর্তনগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো প্রদান করে, যেখানে তথ্যপ্রযুক্তি সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কাস্টেলসের মতে, তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব এবং বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের প্রসারের ফলে একটি নতুন ধরনের সমাজের উদ্ভব হয়েছে, যা ‘নেটওয়ার্ক সমাজ’ নামে পরিচিত।
এই সমাজের মূল ভিত্তি চারটি প্রধান উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত: তথ্যপ্রযুক্তি, যা যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে; নেটওয়ার্ক, যা ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করে; ক্ষমতার নতুন কাঠামো, যা তথ্য প্রবাহের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গঠিত হয়; এবং স্থান ও কালের নতুন ধারণা, যা বিশ্বায়নের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। কাস্টেলসের এই তত্ত্ব শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলোর জন্যই প্রযোজ্য নয়, বরং বাংলাদেশের মতো দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেও এটি গভীর প্রাসঙ্গিকতা বহন করে। নগরায়ণ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার এবং বিশ্বব্যাপী সংযোগ বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশেও নেটওয়ার্ক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই কারণে, কাস্টেলসের তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং এর ভবিষ্যৎ গতিপথ অনুধাবন করা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।
ম্যানুয়েল কাস্টেলসের নেটওয়ার্ক সমাজ তত্ত্বের কেন্দ্রে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি এবং নেটওয়ার্কের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তথ্যপ্রযুক্তির অসাধারণ অগ্রগতি প্রচলিত সামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দিয়েছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও ব্যাপক ব্যবহার মানুষের দৈনন্দিন জীবন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিনোদন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সহ প্রায় সব ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সমাজের মৌলিক সংগঠন এবং মানুষের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ধরণকে রূপান্তরিত করেছে। কাস্টেলস বিশ্বাস করেন যে এই তথ্যপ্রযুক্তিই আধুনিক নেটওয়ার্কের উত্থানের মূল ভিত্তি। বর্তমানে নেটওয়ার্ক সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান এমনকি রাষ্ট্রও বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইন এবং রাজনৈতিক জোট সবই নেটওয়ার্কের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই নেটওয়ার্কগুলো ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং তথ্য আদান-প্রদানকে সম্ভব করে তুলেছে, যা স্থানীয় ও বৈশ্বিক স্তরের মিথস্ক্রিয়াকে আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত ও সহজ করে দিয়েছে।
কাস্টেলস ‘নেটওয়ার্ক লজিক’ ধারণার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন, যা নেটওয়ার্কের গঠন, পরিচালনা এবং বিবর্তনের নিয়ম ব্যাখ্যা করে। নেটওয়ার্কের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো এর নমনীয়তা, যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সহজে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে; সম্প্রসারণযোগ্যতা, যা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি পেতে সক্ষম; এবং টিকে থাকার ক্ষমতা, যেখানে নেটওয়ার্কের একটি অংশের বিচ্ছিন্নতা পুরো নেটওয়ার্ককে অচল করে দেয় না। এই বৈশিষ্ট্যগুলো নেটওয়ার্ককে আধুনিক সমাজের একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিণত করেছে। তথ্যপ্রযুক্তি এই নেটওয়ার্কগুলোকে সম্ভব করে তুলেছে এবং এর মাধ্যমেই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিথস্ক্রিয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।
নেটওয়ার্ক সমাজে ক্ষমতার ধারণা ঐতিহ্যবাহী সমাজের ধারণার থেকে ভিন্ন। কাস্টেলস যুক্তি দেন যে ক্ষমতা এখন আর কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত নেই, বরং এটি নেটওয়ার্কের সংযোগগুলোতে বিকেন্দ্রীভূতভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এই নতুন ক্ষমতা কাঠামোতে ক্ষমতার মূল উৎস হলো তথ্য, জ্ঞান এবং যোগাযোগের প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য। যারা তথ্য তৈরি, প্রক্রিয়া এবং বিতরণের নেটওয়ার্কের নকশা ও পরিচালনা করতে পারে, তারাই এই ক্ষমতা কাঠামোর কেন্দ্রে অবস্থান করে। তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং জ্ঞান সৃষ্টি এই সমাজের ক্ষমতার প্রধান উৎস। ইন্টারনেট তথ্যের অবাধ প্রবাহের সুযোগ তৈরি করলেও, অ্যালগরিদম, ডেটা বিশ্লেষণ এবং নীতিমালার মাধ্যমে এই প্রবাহ প্রভাবিত হতে পারে। কে কী তথ্য পাবে, কোন তথ্য প্রাধান্য পাবে এবং কিভাবে জ্ঞান তৈরি ও বিতরণ হবে—এই প্রক্রিয়াগুলো নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
কাস্টেলস ‘প্রোগ্রামার’ এবং ‘সুইচ’ ধারণা দুটি ব্যবহার করে এই ক্ষমতা কাঠামো ব্যাখ্যা করেন। ‘প্রোগ্রামার’ হলো তারা যারা নেটওয়ার্কের নিয়ম, কোড এবং সফটওয়্যার তৈরি করে, যা তথ্যের প্রবাহ নির্ধারণ করে। তারা নেটওয়ার্কের স্থাপত্য তৈরি করে এবং এর কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, ‘সুইচ’ হলো নেটওয়ার্কের সংযোগকারী বিন্দু যারা বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে এবং তথ্য প্রবাহকে নির্দেশিত করে। তাদের ক্ষমতা নির্ভর করে নেটওয়ার্কে তাদের অবস্থানের এবং তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যের উপর। প্রোগ্রামাররা নিয়ম তৈরির মাধ্যমে ক্ষমতা ধারণ করে, আর সুইচরা সেই নিয়ম প্রয়োগে ভূমিকা পালন করে। এই দুটি ধারণা নেটওয়ার্ক সমাজের জটিল, বিকেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামোকে বুঝতে সাহায্য করে।
নেটওয়ার্ক সমাজে স্থান এবং সময়ের ধারণা ঐতিহ্যবাহী ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা এবং রৈখিক সময়ক্রম থেকে ভিন্ন। কাস্টেলস ‘স্পেস অফ ফ্লোস’ (প্রবাহের স্থান) এবং ‘টাইমলেস টাইম’ (সময়হীন সময়) ধারণা দুটি ব্যবহার করে এই নতুন বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করেন। ‘স্পেস অফ ফ্লোস’ হলো সেই অস্থানিক বা ভার্চুয়াল স্থান যেখানে তথ্য, যোগাযোগ, পুঁজি, প্রযুক্তি এবং মানুষ বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। এটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং ইলেকট্রনিক যোগাযোগ এবং পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে গঠিত নেটওয়ার্কের একটি আন্তঃসংযুক্ত জাল। ইন্টারনেট এবং বৈশ্বিক আর্থিক বাজার এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে দূরত্ব তেমন কোনো বাধা নয় এবং তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব। ঐতিহ্যবাহী স্থানের ধারণা যেখানে ভৌগোলিকতা মুখ্য, সেখানে ‘স্পেস অফ ফ্লোস’ সেই ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং প্রবাহের গতিশীলতার উপর নির্ভরশীল হয়।
অন্যদিকে, ‘টাইমলেস টাইম’ হলো সময়ের একটি অ-রৈখিক ধারণা। তথ্যপ্রযুক্তির ফলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়েছে। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ, ডেটা সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার এবং ভার্চুয়াল রিয়ালিটি সময়ের অভিজ্ঞতাকে বদলে দিয়েছে। যেকোনো সময়ের তথ্য দ্রুত পাওয়া যায় বা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে একই সাথে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়। এটি ঐতিহ্যবাহী ঘড়ির সময় বা কালপঞ্জির ধারণা থেকে ভিন্ন; সময় এখানে নমনীয় এবং পরিবর্তনশীল, যা প্রয়োজন অনুযায়ী সংকুচিত বা প্রসারিত হয়। এই ‘স্পেস অফ ফ্লোস’ এবং ‘টাইমলেস টাইম’ ধারণা বিশ্বায়নের জটিল প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় ও বৈশ্বিক স্তরের মিথস্ক্রিয়াকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্বায়নের যুগে স্থানীয় ঘটনা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং বৈশ্বিক প্রক্রিয়া স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে তাৎক্ষণিক প্রভাবিত করতে পারে। এই মিথস্ক্রিয়া জ্ঞান ও প্রযুক্তির আদান-প্রদানের মতো সুযোগ তৈরি করলেও, সাংস্কৃতিক আধিপত্য এবং স্থানীয় অর্থনীতির উপর বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার মতো চ্যালেঞ্জও নিয়ে আসে।
নেটওয়ার্ক সমাজে সামাজিক পরিচয় গঠনও প্রথাগত সমাজের থেকে ভিন্ন। পরিচয় এখন আর শুধু জাতি, ধর্ম বা লিঙ্গের মতো স্থির বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এটি গতিশীল ও বহুস্তরীভূত। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি বিভিন্ন অনলাইন কমিউনিটির সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদের ধারণা, আগ্রহ ও মূল্যবোধ ভাগ করে নেয়। এই ভার্চুয়াল মিথস্ক্রিয়া নতুন পরিচয়ের দিক উন্মোচন করে এবং একাধিক পরিচয় ধারণে উৎসাহিত করে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে নিজের পছন্দ অনুযায়ী প্রোফাইল তৈরি, বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হওয়া এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার মাধ্যমে ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে তার সামাজিক পরিচয় গঠন ও পরিবর্তন করতে পারে।
সংস্কৃতির উপর তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব বহুমুখী। প্রযুক্তি সংস্কৃতির উৎপাদন, বিতরণ এবং গ্রহণের পদ্ধতিকে বদলে দিয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সাংস্কৃতিক উপাদান বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে, যা বিভিন্ন সংস্কৃতির মিথস্ক্রিয়া বাড়াচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বাড়ছে, তেমনি একটি বিশ্বজনীন সংস্কৃতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইন্টারনেট নতুন ধরনের লোকসংস্কৃতি এবং অনলাইন কমিউনিটি-ভিত্তিক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। মিডিয়া কন্টেন্ট তৈরিতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ায় সংস্কৃতির সংজ্ঞা ও উৎপাদক-ভোক্তার চিরাচরিত বিভাজন কমছে। তবে, প্রযুক্তির মাধ্যমে ভুল তথ্য, বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্য এবং বাণিজ্যিক সংস্কৃতির আধিপত্য বিস্তারের ঝুঁকিও রয়েছে।
কাস্টেলস ‘নেটওয়ার্কড মুভমেন্টস’ ধারণার মাধ্যমে দেখান কিভাবে নেটওয়ার্ক সামাজিক আন্দোলনকে রূপান্তরিত করেছে। ইন্টারনেট ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম আন্দোলনকারীদের দ্রুত সংগঠিত হতে, তথ্য ছড়াতে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হতে সাহায্য করে। আরব বসন্ত বা বিভিন্ন পরিবেশবাদী আন্দোলনে অনলাইন প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার এর উদাহরণ। নেটওয়ার্কড মুভমেন্টসের বৈশিষ্ট্য হলো নমনীয়তা, বিকেন্দ্রীভূত নেতৃত্ব এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ। প্রথাগত কাঠামোর পরিবর্তে, এগুলো স্বতঃস্ফূর্ত সংযোগ ও যৌথ কর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। তবে, এর দীর্ঘস্থায়িত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে চ্যালেঞ্জ আছে।
বাংলাদেশে ম্যানুয়েল কাস্টেলসের নেটওয়ার্ক সমাজ তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ দেশটি দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের ব্যবহার অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে, যা শহর থেকে গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই প্রযুক্তিগত বিস্তার বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশে ডিজিটালাইজেশন উদ্যোগ এই প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্যোগের লক্ষ্য তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা, যার আওতায় ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, অনলাইন শিক্ষা ও অন্যান্য ডিজিটাল সেবার প্রসার ঘটছে। এর ফলে সরকারি সেবা জনগণের কাছে সহজে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে, ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে, অবকাঠামোগত দুর্বলতা, ডিজিটাল বিভাজন ও প্রযুক্তি ব্যবহারের সচেতনতার অভাবের মতো চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করতে হবে।
ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স এবং অনলাইন শিক্ষা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। ই-গভর্নেন্স সরকারি প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত ও জনবান্ধব করার চেষ্টা করছে। অনলাইনে বিভিন্ন সেবা গ্রহণ এখন সহজ হয়েছে। ই-কমার্স নতুন ব্যবসায়িক মডেল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য। অনলাইন শিক্ষা দূরবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়িয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলোতে গুণগত মান বজায় রাখা, সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সাইবার নিরাপত্তা রক্ষা এখনও গুরুত্বপূর্ণ। তথ্যপ্রযুক্তির বিস্তার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ উদ্যোগ কাস্টেলসের তত্ত্বের মূল ধারণাগুলোর বাস্তব প্রতিফলন ঘটায় এবং বাংলাদেশে একটি তথ্যনির্ভর সমাজের উত্থানকে স্পষ্ট করে।
তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। আউটসোর্সিং বা ফ্রিল্যান্সিং তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি সম্ভাবনাময় খাত হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ ও দক্ষ জনশক্তির কারণে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আউটসোর্সিং বাজারে স্থান করে নিয়েছে। রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান স্তম্ভগুলোর একটি, যা মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরাপদে প্রবাসীদের পরিবারের কাছে পৌঁছাচ্ছে। এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো অর্থ লেনদেন সহজ করেছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ডিজিটাল অর্থনীতি বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল ক্ষেত্র। ই-কমার্স, অনলাইন মার্কেটপ্লেস ও ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেমের ব্যবহার বাড়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। ছোট উদ্যোক্তারা অনলাইনে পণ্য বিক্রি করে বাজার সম্প্রসারিত করছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও অন্যান্য সেক্টরেও প্রযুক্তির ব্যবহার দক্ষতা বাড়াচ্ছে।
তবে, প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার সত্ত্বেও বাংলাদেশে বৈষম্য ও ডিজিটাল বিভাজন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ডিজিটাল বিভাজন হলো প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ ও দক্ষতার ক্ষেত্রে বৈষম্য, যা শহর ও গ্রামের মানুষ, ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্পষ্ট। অবকাঠামোগত দুর্বলতা, উচ্চ ইন্টারনেট মূল্য ও প্রযুক্তি ব্যবহারের জ্ঞানের অভাব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ডিজিটাল সুযোগ গ্রহণ কঠিন করে তোলে। এই বিভাজন অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছাতে বাধা দেয় এবং বিদ্যমান বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর উন্নয়ন, ইন্টারনেট মূল্য হ্রাস এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি জরুরি।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বাংলাদেশের রাজনীতি ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনেছে। এই প্ল্যাটফর্মগুলো রাজনৈতিক আলোচনা, জনমত গঠন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ। ফেসবুক, টুইটার সাধারণ মানুষকে মতামত প্রকাশ, রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যুক্ত হওয়া এবং সমমনাদের সাথে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোও প্রচারণা ও বার্তা ছড়াতে এটি ব্যবহার করছে। তবে, ভুয়া খবর ও অপপ্রচারের বিস্তার একটি বড় সমস্যা, যা জনমতকে বিভ্রান্ত ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন ও নাগরিক সমাজের সংগঠনও অনলাইনে দ্রুত সংগঠিত হচ্ছে। অধিকার আদায়, পরিবেশ রক্ষা বা দুর্নীতিবিরোধী ইস্যুতে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শক্তিশালী হাতিয়ার। তবে, গুজব ও ভুল তথ্যের বিস্তার উদ্বেগজনক, যা বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে পারে। এটি মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য যাচাই এবং আইনি পদক্ষেপ জরুরি।
তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন এনেছে। বিনোদন, যোগাযোগ, কেনাকাটা সবকিছুর সাথে প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সহজে দেখা যাচ্ছে। সামাজিক রীতিনীতিতেও পরিবর্তন আসছে, যেমন ভার্চুয়াল মাধ্যমে শুভেচ্ছা বিনিময়। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নতুন সামাজিক পরিচয় ও যোগাযোগের ধরণ তৈরি হয়েছে। তারা অনলাইন কমিউনিটি ও সামাজিক মাধ্যমে ভার্চুয়াল জগৎ তৈরি করেছে, যেখানে তারা সমমনাদের সাথে যুক্ত হয়। ভাষা, ফ্যাশন ও জীবনযাত্রায় ভার্চুয়াল জগতের প্রভাব দেখা যায়। তারা স্থানীয় ও বৈশ্বিক সংস্কৃতির সাথে মিশছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে তারা ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করছে। বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশের স্থানীয় সংস্কৃতির উপর মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। জনপ্রিয় বৈশ্বিক সংস্কৃতি সহজে প্রবেশ করছে, যা আন্তর্জাতিকীকরণ ঘটাচ্ছে। তবে, স্থানীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য হুমকির মুখে পড়তে পারে। তবে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে স্থানীয় সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার সুযোগও তৈরি হচ্ছে। স্থানীয় সংস্কৃতি টিকিয়ে রাখতে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সমন্বয় জরুরি।
বাংলাদেশে নেটওয়ার্ক সমাজের প্রয়োগে অপার সম্ভাবনা থাকলেও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অবকাঠামোগত দুর্বলতা একটি বড় সমস্যা; দ্রুতগতির ইন্টারনেটের অভাব, বিশেষ করে গ্রামে, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের অনিয়মিততা ডিজিটাল সেবায় বাধা সৃষ্টি করে। ডিজিটাল বিভাজন ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম, নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান, যা সুযোগের অসমতা তৈরি করে। সাইবার নিরাপত্তা ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ; অনলাইন ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে তথ্য চুরি, হ্যাকিং ও সাইবার অপরাধের ঝুঁকি বাড়ছে। দুর্বল সাইবার নিরাপত্তা ডিজিটাল লেনদেন ও অনলাইন কার্যকলাপের উপর আস্থা কমাতে পারে। গুজব ও ভুল তথ্যের বিস্তার এবং তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে নেটওয়ার্ক সমাজের সম্ভাবনা কাজে লাগানো সম্ভব।
সমন্বিত ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ জরুরি। অবকাঠামোগত উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়িয়ে স্থিতিশীল ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল বিভাজন কমাতে প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসার, সুলভ ইন্টারনেট ও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সাইবার নিরাপত্তা জোরদারে প্রযুক্তি, দক্ষ জনবল ও আইন প্রয়োগের পাশাপাশি জনসচেতনতা জরুরি। গুজব রোধে তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। নীতি নির্ধারণে একটি সমন্বিত জাতীয় ডিজিটাল কৌশল প্রণয়ন করা উচিত, যেখানে অবকাঠামো, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি, সাইবার নিরাপত্তা ও ডেটা সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষা কারিকুলামে ডিজিটাল সাক্ষরতা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ডিজিটাল অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করাও জরুরি। এই পদক্ষেপগুলো বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নেটওয়ার্ক সমাজ গড়তে সাহায্য করবে।
ম্যানুয়েল কাস্টেলসের নেটওয়ার্ক সমাজতত্ত্ব সমসাময়িক সমাজের গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে, যেখানে প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক, ক্ষমতা ও স্থান-কালের পরিবর্তন সমাজের সর্বস্তরে প্রভাব ফেলে। এই তত্ত্বের মূল কথা হলো, আমরা বিশ্বব্যাপী আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক দ্বারা গঠিত সমাজে বাস করছি, যেখানে তথ্য ও জ্ঞানের প্রবাহ ক্ষমতার নতুন উৎস। বাংলাদেশে প্রযুক্তির বিস্তার এই তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট। অর্থনীতি, রাজনীতি, সামাজিক আন্দোলন, সংস্কৃতি ও পরিচয়ে প্রযুক্তির প্রভাব দৃশ্যমান। তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সমাজের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য অপার সম্ভাবনা বহন করে। ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, অনলাইন শিক্ষা ও আউটসোর্সিং অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে পারে । সামাজিক মাধ্যম নাগরিক সমাজের ক্ষমতায়ন বাড়াতে পারে ।
তবে, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে অবকাঠামো, ডিজিটাল বিভাজন ও সাইবার নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নিরাপদ ডিজিটাল সমাজ গড়তে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে মনোযোগ প্রয়োজন । ভবিষ্যতের গবেষণার জন্য নেটওয়ার্ক সমাজের প্রভাব, ডিজিটাল বিভাজন, সাইবার নিরাপত্তা, গুজব বিস্তার ও স্থানীয় সংস্কৃতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ইত্যাদি দিক গুরুত্বপূর্ণ । নীতি নির্ধারকদের জন্য গবেষণালব্ধ সুপারিশ প্রণয়ন করা জরুরি, যাতে প্রযুক্তির সুফল সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছায় এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ডিজিটাল সমাজ গঠিত হয়।
লেখক: সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা