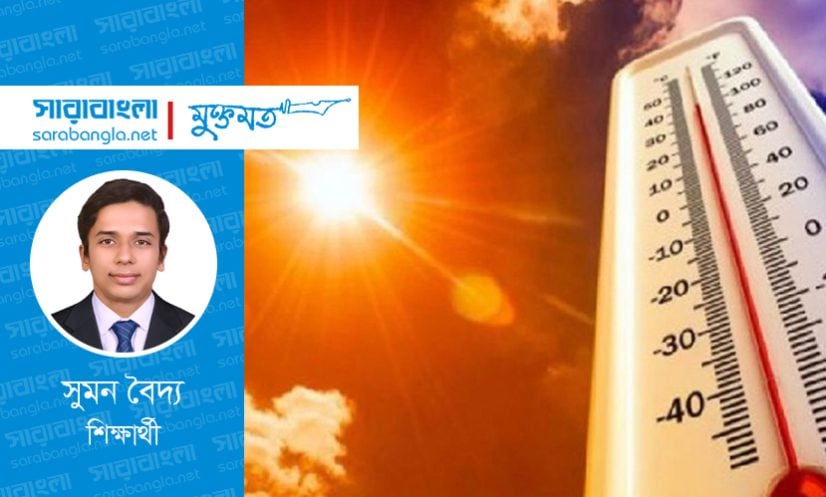এবারের গ্রীষ্মে প্রকৃতি যেন রুদ্র রূপে ধরা দিয়েছে। গ্রীষ্মের তীব্র একটানা দাবদাহে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মানুষের জীবন যেনো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। রাস্তায় পথচারীদের অবস্থা যেনো একটু ছায়ায় আশায় ছুটে বেড়ায়। প্রতিবছর পাল্লা দিয়ে গরমের তীব্রতা যেনো বেড়েই চলেছে। যার ফলে ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষদের।
আর গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং সমস্যা যেনো প্রতিবছরের নিয়মিত কর্মকান্ডে পরিণত হয়েছে। আর এই প্রচণ্ড গরমে শিশুদের সবচেয়ে বেশি কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। একই সঙ্গে নগরীতে দেখা দিচ্ছে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব।প্রশ্ন জাগে, এই অবস্থা কি প্রাকৃতিক? নাকি এটি মানুষের সৃষ্টি?
এই প্রশ্নের উত্তরে নিষ্ঠুরতার ভাব প্রকাশ পেলেও সত্যি যে, আজকের এই তীব্র তাপদাহের পিছনের মূল কারণ হলো পরিবেশের প্রতি মানুষের অবহেলা এবং নির্বিচারের নগরায়নের শেষ করার ফলেই আজ সবাই জলবায়ু সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। তাই মানুষের এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বলা যেতেই পারে –
গরমের ঘামে ভিজে বুক,
পুড়ে যায় পথ, পুড়ে যায় সুখ।
আকাশ যেন আগুন বোনে,
প্রাণ কাঁদে, ধরা শুধু ক্রন্দন শোনে।
নদী শুকায়, ডাল মরে যায়,
পাতা ছুঁয়ে আশ্বাসও হারায়।
একফোঁটা বৃষ্টি যেন স্বর্গদান,
জীবন হয়ে যায় তপ্ত চুল্লির সন্ধান।
এ গরম শুধু ঋতু নয়,
এ এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ—
মানুষের অপরাধে প্রকৃতির প্রতিঘাত।
অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাভূমি ভরাট, নির্বিচারে গাছপালা কেটে ফেলা, শহরের সবুজ মাঠ, খোলা জায়গা ও পুকুর খাল ধ্বংসের কারণেই প্রতিবছরই মানুষের এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ভোগ করতে হয় আমাদের নগরবাসীকে। যার ফলে প্রকৃত তাপমাত্রার চেয়ে গরমের অনুভূতি কয়েক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি অনুভূত হচ্ছে।
তাপমাত্রা বৃদ্ধির পেছনে বৈশ্বিক উষ্ণতার পাশাপাশি স্থানীয় অনেক কারণও আছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে তাপমাত্রা ভিন্ন অনুভূত হয়। এর কারণ হলো সবুজের অভাব এবং ঘরের ছাদে টিন ব্যবহারের কারণে দরিদ্রতম এলাকাগুলোয় বেশি গরম। যার ফলে দিনের বেলা সূর্যের তাপ ধরে রাখে এবং রাতে খুব দ্রুত তাপ ছাড়ে না। তাছাড়াও অঞ্চলগুলোতে দেখা যায় বেশিরভাগ উঁচু ভবনবেষ্টিত। তাই সহজেই বাতাস প্রবাহিত হয় না, এতে করে গরম বাতাস আটকে থাকে।
অন্যদিকে শহরাঞ্চলের মধ্যে জলাভূমিগুলো ধ্বংস হয়ে যাবার কারণে এখন শহরে ভবনের ভেতর শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বা এসি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে তাপমাত্রা কমানো যাচ্ছে না। অন্যদিকে মাত্রারিক্ত এসি ব্যবহারের কারণে জলবায়ুতে ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলছে। কারণ এসি যখন ঘরের গরম বাতাস বাইরে বের করে দেয়, তখন সেই তাপ বাইরের পরিবেশকে আরও গরম করে তোলে। এটি শহরাঞ্চলে ‘urban heat island effect’ তৈরি করে, যেখানে শহরের তাপমাত্রা আশপাশের গ্রামীণ এলাকার চেয়ে অনেক বেশি হয়।
এসির ব্যবহার বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে দেয়। এই বিদ্যুৎ যদি জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে তা কার্বন নিঃসরণ বৃদ্ধি করে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নে ভূমিকা রাখে। অনেক এসি যন্ত্রে ব্যবহৃত রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস যেমন HFC (Hydrofluorocarbons), যা কার্বন ডাই অক্সাইডের তুলনায় অনেক গুণ বেশি তাপ ধরে রাখতে পারে, পরিবেশে নিঃসৃত হলে তা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিপজ্জনক।
মানুষের এই নেতিবাচক কর্মে যেমন নগরবাসী যেমন অতিষ্ঠ ঠিক তেমনি বাদ যাচ্ছে না শহরাঞ্চলের উন্মুক্ত স্থানগুলো। বিভিন্ন শহরাঞ্চলের উন্মুক্ত স্থানগুলোতে কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নগরায়ণের নামে জায়গা ভরাট করেই চলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতবাদ অনুসারে, নগরে ৩০ ভাগ জলাশয় ও সবুজ এলাকা বাড়ানো উচিত। কিন্তু সেই জায়গায় মানুষরা নির্বিচারে তা ক্ষতিসাধন করেই যাচ্ছে।
এই তীব্র তাপমাত্রার গরমের ফলে অতিরিক্ত গরম ডিহাইড্রেশন, হিটস্ট্রোক, রক্তচাপের সমস্যা দেখা দেয়। আর এই গরমের কারণেই মানুষের কাজের স্পৃহা কমে যায়, বিরক্তি ও অবসাদ বাড়ে।
অসহ্য গরমে জনজীবনের যখন হাঁসফাঁস, ঠিক অন্যদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়তি বিড়ম্বনা হিসেবে বেড়েই চলেছে দিয়েছে বায়ুদূষণ। গরমে রাস্তায় ধুলাবালি ও যানবাহনের ধোঁয়া মিলে বায়ুদূষণ বেড়ে যায়, যা শ্বাসকষ্টের কারণ হয়। আর এই বায়ুদূষণ ও অসহনীয় তাপমাত্রার দিকে প্রথম দিকে অবস্থান করছে বাংলাদেশের প্রধান রাজধানী ঢাকা। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যাড্রিয়েন আরশট-রকফেলার ফাউন্ডেশন রিজিলিয়ান্স সেন্টারের ‘হট সিটিজ, চিল্ড ইকোনমিক: ইমপ্যাক্টস অব এক্সট্রিম হিট অন গ্লোবাল সিটিজ’ শীর্ষক গবেষণায় উল্লেখিত হয়েছে যে, ঢাকায় উচ্চ তাপমাত্রার কারণে প্রতি বছর ৬০০ কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ এই ক্ষতির পরিমাণ ৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।
অন্যদিকে উচ্চ তাপমাত্রার ফলে ঢাকার মানুষের শ্রম উৎপাদনশীলতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঢাকায় উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিমাণ ৬০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে চলেছে। আবহাওয়াবিদদের মতবাদ অনুযায়ী, সাধারণত এপ্রিলে ঢাকার গড় তাপমাত্রা থাকে ৩৩ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০২৩ সালের ১৬ এপ্রিল ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে ৪০ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা বিগত ৫৮ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১৯৬৫ সালে এপ্রিল মাসে ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ১৯৬০ সালে ঢাকায় পারদ উঠেছিল রেকর্ড ৪২ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।
সম্প্রতি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, গাছ ও জলাশয় আছে এমন এলাকার চেয়ে ঢাকার তাপমাত্রা গড়ে ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি।
তাছাড়াও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের ব্যবহার যতই বাড়ছে, ভবনের বাইরের এলাকার তাপমাত্রা ততই বাড়ছে। আবহাওয়া বিভাগের হিসাবে গত ১০০ বছরে দেশের অন্যান্য স্থানের তুলনায় রাজধানীর তাপমাত্রা দেড় গুণের বেশি বেড়েছে।
গত বছরের কথাই ধরা যাক। গত বছর দেশে তাপমাত্রা যা ছিল, তা ৭৬ বছরের মধ্যে ছিল সর্বোচ্চ। এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত টানা ৩৫ দিন তাপপ্রবাহ ছিল। শুধু বাংলাদেশ নয়, গত বছর ইতিহাসের সর্বোচ্চ উষ্ণ বছর ছিল। চলতি বছরের জানুয়ারি মাস যতটা উষ্ণ ছিল, তাও বিশ্বের ইতিহাসে অনেকটাই বিরল।
আশ্চর্যের বিষয় হলো এবার দেশে শীত তেমন পড়েনি। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে শূন্য দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি ছিল। আর সদ্য বিদায়ী ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা বেশি ছিল ১ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দেখা যাচ্ছে, ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা অনেকটাই বেড়ে গেছে।
এ বছরের জানুয়ারি মাস ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে উষ্ণতম মাস। ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোপার্নিকাস ক্লাইমেট চেঞ্জ সার্ভিস এ পরিসংখ্যান দিয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জানুয়ারির তাপমাত্রা প্রায় শূন্য দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ নিয়ে গত বছরের (২০২৪) জানুয়ারির রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।
স্বাভাবিকভাবেই তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৭ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত থাকলে তাকে মৃদু তাপপ্রবাহ বলা হয়। তাপমাত্রা ৩৮ থেকে ৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তা মাঝারি তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে তীব্র তাপপ্রবাহ ধরা হয়। তাপমাত্রা ৪২-এর বেশি হলে তা অতি তীব্র তাপপ্রবাহ বলে গণ্য হয়।
কিন্তু এইবারের গরমের তেজ যেনো রেকর্ড গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। গেলো ১০ই মার্চ দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা বিভাগের চুয়াডাঙ্গা। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়িয়ে গরমের তীব্র তান্ডব নগরবাসীকে অতীষ্ঠ করে রেখেছে। এরপরই অবস্থান করছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা, ৪০ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে চুয়াডাঙ্গার পর ঢাকার মানুষও তীব্র গরমের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে আছে। এর আগে ২৮ মার্চ রাজধানীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সিলেটে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এইতো গেলো মানবসৃষ্টের অনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা। অন্যদিকে আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যেও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উদাসীনতার ভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক তরুণ-তরুণীরা মনে করে জলবায়ু পরিবর্তন দূরবর্তী ভবিষ্যতের সমস্যা, যা এখনই তাদের জীবনে বড় প্রভাব ফেলছে না। তাই তারা বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না।
স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কার্যকর শিক্ষা ও আলোচনা কম হয়। ফলে তরুণদের মধ্যে বিষয়টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান তৈরি হয় না। সোশ্যাল মিডিয়া, বিনোদন ও ব্যক্তিগত চাহিদার ভিড়ে জলবায়ু ইস্যুগুলো অনেকের কাছে গুরুত্ব হারায়। অনেকেই ভাবে সরকার বা বড় কোম্পানিগুলোই এই সমস্যার সমাধান করবে, ব্যক্তিগত সচেতনতা বা উদ্যোগের প্রয়োজন নেই। কিছু তরুণ জানলেও ভাবে ‘আমার একার কিছু করার নেই’, তাই তারা নিজেদের অসহায় মনে করে উদাসীন হয়ে পড়ে।
তাই শুধু ঢাকায় নয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলের এই ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বপ্রথম যে পদক্ষেপ নিতে হবে তা হলো, শহরের প্রতিটি ফাঁকা স্থানে গাছ লাগানো। সড়ক বিভাজকে শোভাবর্ধক রাখতে গাছ ছাড়াও ভূমির ধরনের ভিত্তিতে বিভিন্ন রকম উপকারী বৃক্ষ যেমন ফলের গাছ, ঔষধি গাছ, কাষ্ঠল গাছও রোপণ করতে হবে। ছাদবাগান বাড়াতে হবে। তাই সরকারি, বেসরকারি স্থানীয় প্রশাসনদের দায়িত্বের সাথে এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে।দখলকৃত জলাভূমি উদ্ধার করতে হবে এবং সেইসাথে এসব কারণ বিবেচনায় রেখে রাজধানী-সংক্রান্ত যাবতীয় জননীতি ঢেলে সাজাতে হবে। সরকারি -বেসরকারী সংস্থাগুলোতে বেশি বেশি বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ বাড়াতে হবে এবং বৃক্ষরোপণের প্রতি জনগণের উৎসাহ বাড়াতে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা প্রয়োজন।
গরমের এই অসহনীয় তাপমাত্রা রোধে ও আগামী দিনে জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবিলায় তরুণ প্রজন্ম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, স্কুল-কলেজে ও স্থানীয় পর্যায়ে তরুণ প্রজন্মদের জলবায়ু বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালাতে হবে। প্লাস্টিক কম ব্যবহার, বাইসাইকেল/পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার, বিদ্যুৎ ও পানির অপচয় রোধে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক পোষ্ট যেমন: ইনফোগ্রাফিক ডকুমেন্টারি, ব্লগ, ছোট ভিডিও, রিলস, বা কার্টুনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, এসির ক্ষতি, এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির গুরুত্ব বোঝানো যেতে পারে।
শহরের বা এলাকার গরম পরিস্থিতি, গাছ কাটা, পানির সংকট ইত্যাদি বিষয়ে ফেসবুক লাইভ, টুইটার থ্রেড বা ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে প্রশাসনের নজর আনা যায়। সচেতন তরুণরা অনলাইনে পিটিশন চালু করে, ভাইরাল ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে, এবং জলবায়ু নীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে পারে।
তাছাড়াও তরুণদের সংগঠনগুলো আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংগঠন (যেমন Fridays for Future, 350.org) এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৈশ্বিক প্ল্যাটফর্মে নিজেদের কণ্ঠ তুলে ধরতে পারে এবং বিদেশি ফান্ডিং বা ট্রেইনিং-এর সুযোগ নিতে পারে।
যৌথভাবে তরুণ সংগঠনগুলো নীতিনির্ধারকদের কাছে দাবি জানাতে পারে। যেমন: টেকসই শহর পরিকল্পনা, সবুজ এলাকা সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম। তরুণদের নেতৃত্বে গঠিত অর্গানাইজেশনগুলো নিজেদের এলাকায় নির্দিষ্ট সমস্যা (যেমন গাছ কাটা, জলাবদ্ধতা, অতিরিক্ত কংক্রিট) চিহ্নিত করে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। তারা ছোট ছোট প্রকল্প (urban gardening, ছাদে গাছ লাগানো, রেইনওয়াটার হারভেস্টিং) শুরু করে বাস্তব সমাধান করতে পারে। এতে করে এই অ্যাডভোকেসি কাজগুলোর মাধ্যমে সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব।
তাছাড়াও যেসব তরুণ প্রজন্মরা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে সোচ্চার নয় তাদেরকে বিভিন্ন উপায়ে কাজে লাগাতে হবে। যেমন: জনপ্রিয় ইউটিউবার, সেলিব্রেটি ও ইনফ্লুয়েন্সারদের যুক্ত করে সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করা।স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবেশ ক্লাব গঠন করে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া।
ছোট ছোট ‘গ্রীন প্রজেক্ট’ (গাছ লাগানো, প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সৌরশক্তির ব্যবহার) হাতে নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।
পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা (ইনোভেটিভ আইডিয়া, পোস্টার ডিজাইন, ব্লগ লেখা) আয়োজন করা। সফল তরুণদের পুরস্কৃত ও প্রচার করা। এতে করে কাজ করার ও সচেতনতার স্পৃহা বাড়বে।
স্বল্পপরিসরে হলেও তাদের জীবনযাত্রায় পরিবেশবান্ধব আচরণ (প্লাস্টিক কমানো, রিসাইক্লিং, সাইকেল ব্যবহার) অন্তর্ভুক্ত করতে উৎসাহিত করা। কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু ন্যায়বিচারের জন্য সোচ্চার হওয়ার সুযোগ তৈরি করা। সফল উদাহরণ ও গল্প শোনানো। যেমন: তরুণদের প্রচেষ্টায় পরিবেশগত কি কি উন্নতি হয়েছে, তারা কী কী বিষয় শিখতে পেরেছে, কিরকম ছোট উদ্যোগ নিলেও পরিবর্তন সম্ভব! এবং তাদের আগামীতে পরিবেশ নিয়ে কি ভাবনা এবং এইটা নিয়ে তাদের বিভিন্ন গবেষণামূলক ও বিভিন্ন অর্গানাইজেশন ভিত্তিক ফোরামে যুক্ত হয়ে আরো কীভাবে কাজ করা যায় তা নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা।
এরপরই রয়েছে সাংবাদিকতা। পরিবেশগত সাংবাদিকতার উপর ভিত্তি করে ইনভেস্টিগেটিভ সাংবাদিকতা গরমের তীব্রতা ও জলবায়ুর আকস্মিক পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র, কারণ ও সমাধান তুলে ধরার শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। এটি শুধু সমস্যা চিহ্নিত করে না, বরং জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের সচেতন করতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
জলবায়ু পরিবর্তন ও উষ্ণায়নের নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, যেমন: IPCC রিপোর্ট, স্থানীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর, গবেষণা সংস্থার উপর বৈজ্ঞানিক উপাত্ত ও গবেষণা রিপোর্ট তৈরি। সরকারি দপ্তর বা পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রাসঙ্গিক নীতি, অনুমতি, শিল্প-কারখানার নির্গমন তথ্য সংগ্রহ করা।
খরা, জলাবদ্ধতা, অতিরিক্ত তাপদাহ বা ঘূর্ণিঝড়পীড়িত প্রভাবিত এলাকায় সরেজমিন পরিদর্শন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ। কৃষিকাজ, মৎস চাষ, বনাঞ্চল, নদীর গতিপথ ইত্যাদিতে জলবায়ুর পরিবর্তনের সরাসরি প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা।
স্থানীয় শিল্পকারখানা, ইটভাটা, গাড়ির ধোঁয়া, অবৈধ বন উজাড় — এসবের কারণে কীভাবে গরমের তীব্রতা বাড়ছে, তা অনুসন্ধান করা। সেইসাথে নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ফাঁকফোকর খোঁজা। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের নির্ধারিত নীতিমালাগুলো স্থানীয় প্রশাসনগুলো কতটুকু কার্যকর করতে পারছে এবং পরিবেশ আইন কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে তা বিশ্লেষণ ও তদারকি করা।
অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, জেলে, দিনমজুর, নারী ও শিশুদের জীবনযাত্রা ও স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে মানবিক গল্প উপস্থাপন করা। ডেটা জার্নালিজম ও ভিজ্যুয়াল রিপ্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা বোঝানোর জন্য ইন্টার্যাক্টিভ ভিজ্যুয়াল টুল ব্যবহার করা।
তাছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু সংকটের সাথে বাংলাদেশের স্থানীয় বাস্তবতার যোগসূত্র তুলে ধরা এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি (যেমন প্যারিস চুক্তি) দেশের অঙ্গীকারের মধ্যে বাস্তবতা তুলনা করা। সম্ভাব্য সমাধান ও নীতির সুপারিশ করা। যেমন: পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু অভিযোজনের জন্য বিশেষজ্ঞ মতামত ও কমিউনিটি-ভিত্তিক সমাধানের উপস্থাপন। প্রশাসন, নাগরিক সমাজ, ব্যবসায়ী মহলের দায়িত্ববোধ নিয়ে প্রশ্ন উপস্থাপন।
সর্বোপরি, গরম বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট কাজকর্মই বেশি দায়ী। তাই পরিবেশ রক্ষা কোনো একক দায়িত্ব নয়—এটি সবার সম্মিলিত কর্তব্য। তাই সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম ও নাগরিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একত্রে কাজ করলেই টেকসই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব। আরে এতে করে সবুজায়ন, সচেতনতা ও পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের মাধ্যমেই আমরা একটি শীতল ও স্বস্তিদায়ক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।
লেখক: শিক্ষার্থী, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা