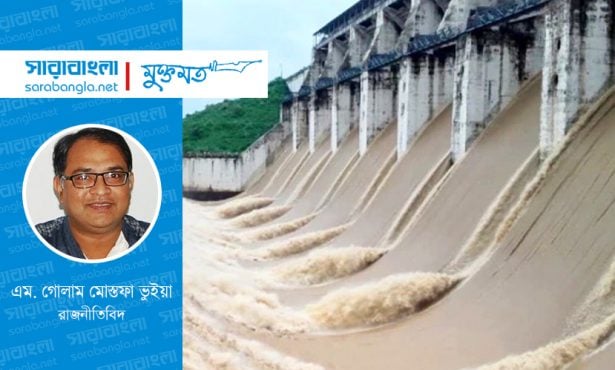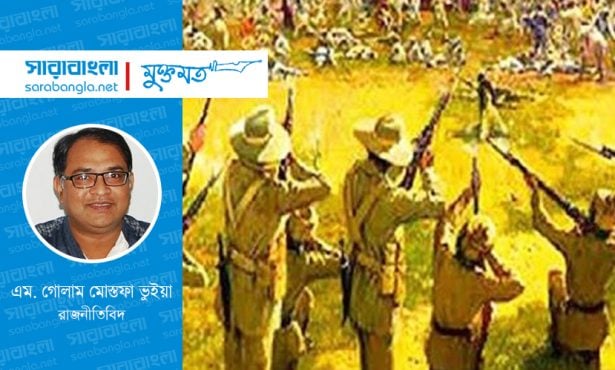বাংলাদেশ ব্যাপকভাবে ভারতীয় পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ যখন গঙ্গার পানির ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তখন নতুন করে আবার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তিস্তায় পানি না পাওয়া এবং টিঁপাইমুখ বাঁধ নিয়ে। পানির অন্যতম প্রধান উৎস পদ্মা নদী এখন শুধু বালুচর। কোথাও কোথাও হচ্ছে শস্য চাষ। চরছে গবাদি পশু। ১৯৯৬ সালের পানি চুক্তি অনুযায়ী ভারত ফারাক্কা পয়েন্ট দিয়ে প্রয়োজনীয় পানি ছাড় না করায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রংপুরে তিস্তার পানি বন্টন নিয়ে প্রতিবেশী ভারতের অনৈতিক ঢিলেমি, হঠকারিতা ও একগুয়েমির ফলে এ নদীর বাংলাদেশ অংশ জুড়ে এখন মরুভূমির প্রতিচ্ছবি। একই সাথে টিঁপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বাংলাদেশের জন্য সৃষ্টি করেছে অশনি সংক্ষেত। নদীমাতৃক এই বাংলাদেশ আজ প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। ভারতের অব্যাহত পানি আগ্রাসনের কারণে বাংলাদেশ আজ তার স্বাধীন অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকবে কিনা সে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।
ফারাক্কা বাঁধ
ফারাক্কা বাঁধ গঙ্গা নদীর উপর অবস্থিত একটি বাঁধ। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এই বাঁধটি অবস্থিত। ১৯৬১ সালে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়। শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। সেই বছর ২১ এপ্রিল থেকে বাঁধ চালু হয়। ফারাক্কা বাঁধ ২,২৪০ মিটার (৭,৩৫০ ফুট) লম্বা যেটা প্রায় এক বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় বানানো হয়েছিল। বাংলাদেশের রাজশাহী সীমান্তের ১৬.৫ কিলোমিটার উজানে গঙ্গা নদীতে এ বাধ নির্মান করা হয়। কলকাতা বন্দরের নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে ভারত ১৯৫৬ সালে এই প্রকল্প হাতে নেয়।
১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে গঙ্গা প্রশ্নে জরুরি আন্তরিক আলোচনা শুরু করে। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন (JRC)। ১৯৭৫ সালে ভারত বাংলাদেশকে জানায় যে, ফারাক্কা বাঁধের ফিডার ক্যানাল পরীক্ষা করা তাদের প্রয়োজন। সে সময় ভারত ১৯৭৫ সালের ২১ এপ্রিল থেকে ৩১ মে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১০ দিন ফারাক্কা থেকে ৩১০-৪৫০ কিউবিক মিটার/সেকেন্ড গঙ্গার প্রবাহ প্রত্যাহার করার ব্যাপারে বাংলাদেশের অনুমতি প্রার্থনা করে। বাংলাদেশ সরল বিশ্বাসে এতে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ভারত বাঁধ চালু করে দেয় এবং নির্ধারিত সময়ের পরেও একতরফাভাবে গঙ্গার গতি পরিবর্তন করতে থাকে যা ১৯৭৬ সালের পুরা শুষ্ক মৌসুম পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বন্দরের নাব্যতা উন্নয়নে পলি ধুয়ে নিতে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গানদী থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভাগিরথী-হুগলী নদীতে ১১৩০ কিউবিক মিটারের বেশি পানি পৌঁছে দেওয়া।
ভারতকে এ কাজ থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হয়ে বাংলাদেশ এ ব্যাপারে জাতিসংঘের শরণাপন্ন হয়। ১৯৭৬ সালের ২৬ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি সর্বসম্মত বিবৃতি গৃহীত হয় যাতে অন্যান্যের মধ্যে ভারতকে সমস্যার একটি ন্যায্য ও দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনায় বসার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরিশেষে ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বণ্টন সংক্রান্ত ৩০ বছরের একটি চুক্তিতে উপনীত হতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ফারাক্কা চুক্তি সাক্ষরিত হলেও ভারত কখনোই বাংলাদেশকে তার পানির ন্যয্য হিস্যা দেয় নাই।
শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার পানি অপসারণের ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ বাধ চালুর পর দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরুকরণ শুরু হয়। গঙ্গার প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে ফলে বর্ষা কালে এ দেশের উত্তরাঞ্চলে তিব্র বন্যা দেখা দিচ্ছে। এতে বাংলাদেশকে কৃষি, মৎস্য, বনজ, শিল্প, নৌ পরিবহন, পানি সরবরাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়। ফারাক্কার আগে এক সময় রাজশাহী পদ্মা অবধি ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। এখন আরিচাতেই এ মাছ পাওয়া যায় না। ফারাক্কা বিদ্যমান থাকলে আশংকা করা হয় পদ্মা এবং তার কমান্ড অঞ্চলে ইলিশ মাছ আদৌ পাওয়া যাবে না।
তিস্তা বা গজলডোবা বাঁধ
সিকিম হিমালয়ের ৭,২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত চিতামু হ্রদ থেকে এই নদীটি সৃষ্টি হয়েছে। নদীটি নিলফামারী জেলার কালীগঞ্জ সীমান্ত এলাকা দিয়ে। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দের অতিবৃষ্টি একটি ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করেছিল এবং সেই সময় নদীটি গতিপথ পরিবর্তন করে লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম এবং গাইবান্ধা জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে চিলমারী নদীবন্দরের দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হয়। তিস্তা নদীর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ৩০৯ কিমি, তার মধ্যে ১১৫ কিমি বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত। তিস্তা একসময় করতোয়া নদীর মাধ্যমে গঙ্গার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং এর অংশবিশেষ এখনও বুড়ি তিস্তা নদী নামে পরিচিত।
গজলডোবা (তিস্তা) বাঁধ ২২১ দশমিক ৫৩ মিটার দীর্ঘ, ৪৪ গেটবিশিষ্ট গজলডোবা বাধের রয়েছে ৩ টি পর্যায়। প্রথম পর্যায় সেচ প্রকল্প, দ্বিতীয় পর্যায় পানি বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং তৃতীয় পর্যায় গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল খনন করে নৌপথ তৈরী। সিকিম এন্ডারসন সেতুটি দার্জিলিং কালিংপং সড়কে অবস্থিত, যার ২৫ কিলোমিটার ভাটিতে করনেশন সেতু। এরই ভাটিতে সিভক শহরের কাছে তিস্তা নদী ডুয়ার্সের সমতলে প্রবেশ করেছে। তারও ১৫ কিলোমিটার ভাটিতে গজলডোবায় এ ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়েছে। গজলডোবার ৭০ কিলোমিটার ভাটিতে তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। গজলডোবার এই বাঁধে ফটক রয়েছে ৪৪ টি, যা বন্ধ করে তিস্তার মূলপ্রবাহ থেকে পানি বিভিন্ন খাতে পুনর্বাহিত করা হয়। নদী বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন, তিস্তার পানি তিস্তা-মহানন্দা খালে পুনর্বাহিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এ বাঁধ স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সরকার তিস্তায় গজলডোবা বাঁধের মাধ্যমে উজানে জলাধার থেকে পানি সরাসরি ফারাক্কা বাঁধের উজানে গঙ্গা নদীতে নিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারত তিস্তা বেসিনের পানি মহানন্দা বেসিনেও সরিয়ে নিচ্ছে। গঙ্গা থেকে আরেকটি সংযোগ খালের মাধ্যমে তিস্তার পানি দক্ষিণাত্যেও সরিয়ে নেয়ার পরিকল্পনা ভারতের রয়েছে।
তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে লালমনিরহাট জেলার ডালিয়া পয়েন্টে। এই নদী বাংলাদেশের প্রায় ১২ টি জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদে এসে মিলেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল এবং এই ১২ টি জেলার অর্থনীতি প্রত্যক্ষভাবে তিস্তা নদীর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৪ % মানুষের জীবিকা তাই এই নদীর ওপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পানি-ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত বলেন যে, ‘তিস্তার মূল প্রবাহ ভারত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তিস্তায় ডালিয়া ব্যারাজে উজান থেকে আসা পানিপ্রবাহ প্রায় শূন্য। এখন যে ৬০০-৭০০ কিউসেক পানি যা আসছে তা, ধারণা করি, ভারতের গজলডোবা ব্যারাজের ভাটির উপনদী থেকে’। বাংলাদেশ অনেক দর কশাকশি করেও তিস্তা চুক্তিতে অগ্রসর হতেক পারে নাই। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তিস্তা চুক্তি চাইলেও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অনিচ্ছার কারনে এই চুক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। ভারত বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য হিস্যা দিচ্ছে না। যার সরাসরি ফলাফল হিসেবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল এবং বৃহৎ জনঙ্গষ্ঠি হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মরুকরণ দেখা দিচ্ছে।
আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প
গঙ্গার তথাকথিত পানি চুক্তি যখন বাংলাদেশকে তার পানি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে, ঠিক তখনই ভারত আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের করতে চাচ্ছে। এই প্রকল্প খোদ ভারতেই বির্তকের সৃষ্টি করেছে। এই বিশাল নদী সংযোগ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে ভারতের অভ্যন্তরে ৩৭টি নদীকে ৯ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ ৩১টি খালের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করে ১৫০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করার জন্য। প্রকল্পটির মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্রের পানি নিয়ে যাওয়া হবে গঙ্গায়। সেখান থেকে তা নিয়ে যাওয়া হবে মহানন্দ এবং গোদাবরিতে। গোদাবরির পানি নিয়ে যাওয়া হবে কৃষ্ণায় এবং সেখানে থেকে পেনার এবং কাবেরীতে। নর্মদার পানি নিয়ে যাওয়া হবে সবরমতিতে। এই বিশাল আন্তঅববাহিকা পানি প্রত্যাহার প্রকল্প সম্পূর্ণ করা হবে ২০০৬ সালের মধ্যে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষ হলে বাংলাদেশের ওপর মারাত্মক আর্থসামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া এ প্রকল্পের কারণে বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থায় ভয়াবহ প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।
টিঁপাইমুখ বাঁধ
বাংলাদেশের জন্য আরেকটি দুঃখজনক খবর হচ্ছে টিপাইমুখ বাঁধ। বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বড় ধরনের আতঙ্কের। ভারতের টিপাইমুখ হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টে যে হাই ড্যাম নির্মাণ করা হবে তার উচ্চতা ১৬২ দশমিক ৮ মিটার। এর পানি ধারণ ক্ষমতা ১৫ দশমিক ৫ বিলিয়ন কিউবিক মিটার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৫০০ মেগাওয়াট। এটি নির্মিত হবে প্রায় বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষে, আসামের করিমগঞ্জে বরাক নদীর ওপর। এ বরাক নদী হচ্ছে সুরমা ও কুশিয়ারার মূল ধারা। সুরমা ও কুশিয়ারা পরে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করেছে আমাদের বিশাল মেঘনা। ইতোমধ্যে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করায় মরে যাচ্ছে প্রমত্তা সুরমা। গণমাধ্যমের বিশ্লেষন অনুযায়ী উজানে পানি প্রত্যাহারের ফলে বাংলাদেশের সুরমা নদীর পানি প্রবাহ গত ১০ বছরে শতকরা ৮০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। ভারতের বরাক নদী বাংলাদেশের সুরমা, কুশিয়ারা অমলশীদে এসে মিলিত হয়েছে। বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা এ তিন নদীর মিলনস্থল অমলশীদ এক সময় অনেক গভীর ছিল। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বর্ষা মৌসুমে ভাঙ্গন রোধে বরাক নদীর দুই তীরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ধীরে ধীরে সুরমা নদীর প্রধান প্রবাহ কুশিয়ারার দিকে ঘুরে গেছে। এতে বলা হয়, সুরমার ভাটিতে কমপক্ষে তিন কিলোমিটার মরে গেছে।
আন্তর্জাতিক পানি ব্যবহারের আইনগত দিক
আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে একটি নদী যদি ২/৩ টি দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাহলে ঐ নদীর পানি সম্পদের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। যে কোন আন্তর্জাতিক নদীর উপর তীরবর্তী রাষ্ট্রের অধিকার সমঅংশীদারিত্বের নীতির উপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক নদী সম্পদের তীরবর্তী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সুষম বন্টনের নীতি আজ স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক নদীর ব্যাবহার সম্পর্কে ১৮১৫ সালে ভিয়েনা সম্মেলন ও ১৯২১ সালে আন্তর্জাতিক দানিযুব নদী কমিশন কর্তৃক প্রণীত আইনে এই নীতির উল্লেখ রয়েছে। পৃথিবীতে প্রায় ২১৪টি নদী রয়েছে যে নদীগুলো একাধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। মোট ৯টি নদীর কথা জানা যায়, যা ৬টি বা ততোধিক দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। এসব নদী হচ্ছে- দানিয়ুব, নাইজার, নীল, জায়ার, রাইন, জাম্বেজী, আমাজান, লেকচাদ ও মেকং। এক্ষেত্রে কোন একটি একক দেশই এ পানি সম্পদ ভোগ করে নাই।
আন্তর্জাতিক নদীর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত ১৯৬৬ সালে আন্তর্জাতিক আইন সমিতির হেলসিংকি নীতিমালার ৪ ও ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি অববাহিকাভূক্ত রাষ্ট্র, অভিন্ন নদীসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্য রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনকে বিবেচনায় নেবে। এবং তা অব্যশ্যই অন্য রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি না করে করেই হতে হবে। ১৯৯২ সালের ডাবলিন নীতিমালার ২ নং নীতিতে বলা হয়েছে, পানি উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা অবশ্যই সবার অংশগ্রহণমূলক হতে হবে। আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহ কনভেনশনের ৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহে পানি তার নিজের ভৌগোলিক এলাকায় যুক্তি ও ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে ব্যবহার করবে।
বাংলাদেশের ক্ষতি
ভারতের ‘পানি রাজনীতি’ তথা বাংলাদেশকে তার ন্যায্য ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে গঙ্গা থেকে পানি প্রত্যাহার ও টিঁপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করায় বাংলাদেশ এক বড় ধরনের পরিবেশ ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখেন হয়েছে। নদী ব্যবস্থায় এসেছে বড় ধরনের পরিবর্তন। পলি পড়ে উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং উজানে পানি প্রত্যাহারের কারণে দেশের ২০টি নদী ইতোমধ্য অস্তিত্ব হারিযে ফেলেছে। এর মধ্যে ১৩টি মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছে। কার্যত এগুলো এখন মৃত নদীতে পরিণত হয়েছে।
বাংলাদেশের করণীয়
ভারতে নিকট থেকে অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায় কোনো দলীয় সমস্যা নয়। এই সমস্যা দেশের এবং সমগ্র জাতির। কারণ, এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। এই অবস্থায় পানির অধিকার আদায়ে দ্বীপাক্ষিক, আন্তর্জাতিক ফোরামে আলোচনা করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। পানির অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কিংবা বুদ্ধিজীবীরা কী ভাবছেন বা বলছেন এটি কোনো বিষয় নয়। জনগণকেই লড়াই চালাতে হবে। টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের একটিমাত্র সমঝোতা হতে পারে আর তা হচ্ছে কোনো প্রকারেই টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করা যাবে না। এ আন্দোলনে আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারেন ভাসানী।
দীর্ঘ সময়েও ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও বাংলাদেশের পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে ব্যর্থতা হচ্ছে বাংলাদেরশর নতজানু পররাষ্ট্রনীতি। এই বিষয়ে শাসকগোষ্টির কূটনীতিকদের চরম ব্যর্থতা প্রকাশ পেয়েছে বার বার। আমাদের দেশের নীতি নির্ধারকরা ও কূটনীতিকরা তাদের কূটনৈতিক সাফল্য দেখাতে চরম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের শাসকগোষ্টিকে মাজা সোজা করে দাড়াতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা পানির অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলকে ন্যুনতম ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। ২০৩০ সালকে সামনে রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি পানি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন এখনই। সেই সাথে আন্তর্জাতিক নদীর পানির সুষ্ঠ ব্যবহারের স্বার্থে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও চীনের পানি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পানি ফোরাম গঠনেরও সময় এখন। একই সাথে সার্ক সনদে পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনা বিষয়টি সংযুক্ত করা দাবি করছি। মনে রাখাতে হবে পানি আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। এ নিরাপত্তা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে সরকারকে।
দলমত সকলকে মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ ভারতের দানবীয়, উন্মাদীয়, উদ্ভট নদীসংযোগ পরিকল্পনায় পুরোপুরি ধ্বংসের মুখোমুখী। এই মুহুর্তে আমাদের নিজস্ব রাজনৈতিক বিভাজন ও মতপার্থক্যের মধ্যেও বাংলাদেশ বাঁচানোর স্বার্থে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে চিৎকার করতে হবে। যাতে এই চিৎকার শুধু সার্ক মঞ্চে নয়, জাতিসংঘ এবং বিশ্ব ব্যাংকের কানেও পৌঁছাতে হবে। জাতিসংঘকে বুঝাতে হবে, বাধ্য করতে হবে – তোমরা একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় পরিকল্পনা ঠেকাও। বিশ্ব ব্যাংকে বলতে হবে-তোমরা এই মহাবিপর্যয় সৃষ্টিকারী নদী সংযোগ পরিকল্পনায় অর্থ দিও না। ইউনেস্কো ঘোষিত ‘হেরিটেজ অঞ্চল’ বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে নদী সংযোগ পরিকল্পনায়। ইউনেস্কোকে বলতে হবে তোমরা ভারতের নদী সংযোগ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হও। এমনভাবে চিৎকার করতে হবে, যেন এই চিৎকার জাতিসংঘে পৌঁছাতে বাধ্য হয়। বিশ্ব ব্যাংক, ইউনেস্কোতে পৌঁছাতে বাধ্য হয়। এই চিৎকার যেন বিশ্ববাসীর কাছে পৌছায়। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, হোক্কাইডো থেকে হনুলুলু, হংকং থেকে হাম্বুর্ক যে যেখানেই আছেন বা থাকবেন সেখানেই এই চিৎকার দিতে হবে। ভারতের পানি ডাকাতির বিরুদ্ধে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে, গড়ে তুলতে হবে আন্দোলন।
স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, ভারতের পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদী জননায়ক মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর ১৬ মে ঐতিহাসিক ফারাক্কা লংমার্চ দিবসে এই হোক আমাদের শপথ।
লেখক: কলাম লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক