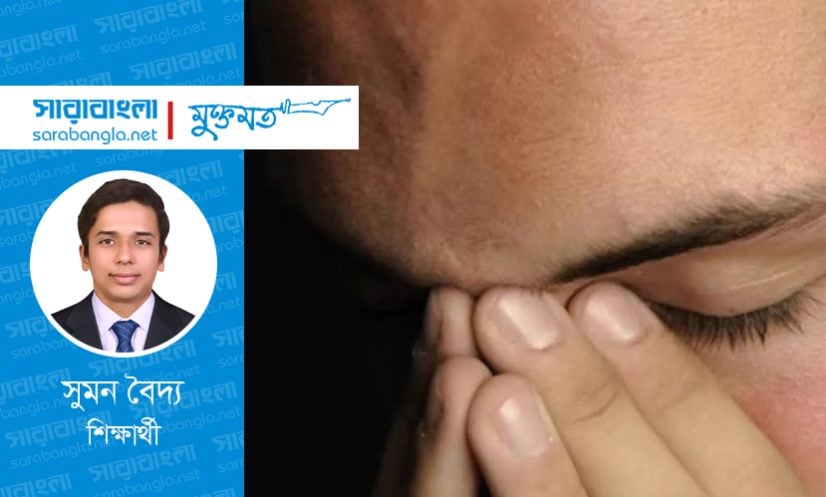বর্তমান তরুণ প্রজন্মেদের বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের কাঁধেই ভবিষ্যতের সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার ভার। কিন্তু আমাদের সমাজে এই তরুণরাই আজ দিশাহারা, হতাশ এবং অনেক সময় জীবনের প্রতি অনীহা নিয়ে আত্মহননের মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিচ্ছে। পড়াশোনার দীর্ঘ ধাপ অতিক্রম করে যখন কোনো তরুণ কর্মসংস্থানের সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা খুঁজে পায় না, তখন সে একটি গভীর মানসিক সংকটে নিপতিত হয়। এই সংকট শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং এটি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতার একটি বহিঃপ্রকাশ।
নম্বরভিত্তিক পড়াশোনার যাঁতাকলে পিষ্ট তরুণেরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনো সৃজনশীলতা ও দক্ষতা গড়ে তোলার পরিবর্তে পরীক্ষার নম্বর অর্জনে সীমাবদ্ধ। শিক্ষার্থীরা শেখে না—তারা মুখস্থ করে, তারা প্রশ্নের উত্তর দেয় কিন্তু জীবনের প্রশ্নের উত্তর জানে না। এই ব্যবস্থায় একটি কৃতকার্য সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, কিন্তু বাস্তব জীবনের জন্য যে প্রয়োজনীয় মানসিক দৃঢ়তা, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কিংবা আত্মবিশ্বাস—সেগুলো তৈরি হয় না। দুঃখজনকভাবে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা সৃজনশীল চর্চার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রোগ্রামিং, শিল্পচর্চা, সাহিত্য, বক্তৃতা, বা উদ্যোক্তা-চিন্তা—এসব দক্ষতার চর্চা করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীরা দিনশেষে প্রাইভেট, কোচিং ও গাইড বই নির্ভর পড়াশোনার মধ্যেই আটকে যায়। যে শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বেশি নম্বর পায়, তাকেই আমরা ‘সেরা” বলে মূল্যায়ন করি। এর ফলে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী যারা অন্য ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিভাবান, তারা নিজেকে ‘ব্যর্থ’ ভাবতে শেখে।
বর্তমান সমাজে শিক্ষা গ্রহণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো মাধ্যমিক পরবর্তী শ্রেণি বিভাজন — বিজ্ঞান, ব্যবসা (কমার্স), ও মানবিক (আর্টস)। এই শাখাগুলোর মধ্যে একটি নির্বাচন যেন শুধু একাডেমিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং সমাজে একজন শিক্ষার্থীর ‘মর্যাদা’ নির্ধারণের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে অভিভাবক ও কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা যেভাবে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দ শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন, তা উদ্বেগজনক এবং অযাচিত।
বিজ্ঞান ও কর্মাস শাখাকে দীর্ঘদিন ধরে ‘সেরা’ ধরা হয়। একে যেন উচ্চমেধার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়, যেখানে আর্টস বা মানবিক শাখাকে অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলা করা হয় —‘পড়া পারেনি বলেই আর্টসে গেছে’ এমন মন্তব্য কানে পড়ে হরহামেশা। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একধরনের মানসিক বিভ্রান্তি তৈরি হয়। অনেক সময় নিজের ইচ্ছা ও দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও সমাজ বা পরিবারের চাপে পড়ে বিজ্ঞান বা কমার্সে ভর্তি হতে হয়। ফলস্বরূপ, অনেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব, হতাশা ও পড়াশোনায় অনাগ্রহ জন্মায়। এই অনাকাঙ্ক্ষিত চাপ ছাত্রজীবনে নয়, বরং পরবর্তীতে কর্মজীবনেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
শিক্ষকদের ভূমিকাও এখানে প্রশ্নবিদ্ধ। অনেক শিক্ষক নিজ নিজ বিভাগের প্রচার করতে গিয়ে অন্য বিভাগের অবমূল্যায়ন করেন। তারা যদি বরং শিক্ষার্থীদের প্রতিভা, আগ্রহ ও মনোবিজ্ঞান বুঝে পরামর্শ দেন, তবে ছাত্রছাত্রীরা আরও সুস্থ ও আত্মবিশ্বাসী সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
একটি গণতান্ত্রিক ও মানবিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিটি শাখাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। আর্টস মানেই শুধুমাত্র ইতিহাস-ভূগোল নয়; এখানে সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি— এমন বহু ক্ষেত্র আছে যেখানে একজন মানুষ অসাধারণ অবদান রাখতে পারেন। একইভাবে কমার্স ও বিজ্ঞানও গুরুত্বপূর্ণ — তবে কারও পছন্দ বা যোগ্যতাকে নিচু করে দেখা একধরনের সামাজিক বৈষম্যই।
একদিকে যেমন শিক্ষাথীরা নম্বরভিত্তিক পড়াশোনার যাঁতাকলে পিষ্ট, অন্যদিকে বেকারত্বও যেনো দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা একটি পুঞ্জীভূত সামাজিক ব্যর্থতা।
বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসা একজন তরুণ যদি বছরের পর বছর চাকরির পরীক্ষায় বসেও কোথাও ঠাঁই না পান, তখন তার মধ্যে চরম হতাশা জন্ম নেয়। বেকারত্ব শুধু আর্থিক অসচ্ছলতা সৃষ্টি করে না, এটি আত্মমর্যাদাহানির বোধ, পরিবার-সমাজের উপেক্ষা ও আত্মবিশ্বাস ভেঙে ফেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বহু তরুণ মনে করে—এই সমাজে তার কোনো প্রয়োজন নেই, তার অস্তিত্ব মূল্যহীন। পরিবার বা সমাজে মন খুলে বলার সুযোগ না পেয়ে কিংবা মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার পরিবেশ না থাকায়, অনেকেই আত্মহননের পথ বেছে নেয়। এটি কোনো দুর্বলতা নয়—বরং দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা বঞ্চনা, অপমান, অনিশ্চয়তা ও দিকহীনতার ফল। যা এখনকার তরুণ সমাজের নীরব কান্না।
তরুণ সমাজের বেকারত্ব বা পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়ার পরেও শুধু নম্বরের ভিত্তিতে তাকে অযোগ্য গড়ে তোলার কারিগর হলো পরিবার ও শিক্ষকদের নোংরা মন মানসিকতা। বছরের পর বছর তাদের চাপিয়ে দেওয়া মনোভাব ও অসৃজনশীলতা তৈরি করার ফলে একদিকে নতুন এই তরুণ প্রজন্মের ছাত্র ছাত্রীরা মুখস্থ বিদ্যার বাইরে যেতে পারছে না, অন্যদিকে একজন তরুণ যুবক বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে শুধুমাত্র সিজিপিএর জন্য রাতদিন পড়াশোনা করছে।
তাদের মতে সমাজে ‘ভালো নম্বর’ বা ‘সরকারি চাকরি’ কে সফলতার একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে কেউ যদি সফলভাবে পরীক্ষায় পাশ করেও উচ্চ নম্বর না পায়, তখন তাকেই অযোগ্য মনে করা হয়। কিন্তু তারা এইটা বোঝার চেষ্টা করে তার ভেতরে অন্য অনেক গুণ বা দক্ষতা থাকতে পারে।
অনেক মা-বাবা বা শিক্ষক নিজের জীবনে যা হতে পারেননি, সেটাই সন্তানের মাধ্যমে পূরণ করতে চান। যদি সেই মানদণ্ডে সন্তানের ফলাফল বা ক্যারিয়ার না মেলে, তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ে এবং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান। এছাড়াও অভিভাবক ও শিক্ষকরা প্রায়শই অন্যদের সঙ্গে তুলনা করেন — ‘অমুকের ছেলে এত নম্বর পেয়েছে’, ‘তোর বন্ধু তো ক্যাডার হয়েছে’ ইত্যাদি।
অনেকে বুঝেই না যে চাকরি পাওয়া বা নম্বর পাওয়া সবসময় ব্যক্তির সামর্থ্যের একমাত্র প্রমাণ নয়। পরীক্ষার নম্বর, চাকরির সুযোগ—সবই বহু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। এই বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থেকেই তরুণদের দোষারোপ করা হয়।
অনেকে সন্তান বা শিক্ষার্থীর নম্বর বা চাকরিকে নিজের পরিবারের ‘সম্মান’ বা ‘মর্যাদা’র সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে কোনো ব্যর্থতা হলে তারা একে ব্যক্তিগত অপমান বলে ধরে নেন এবং সেটার প্রতিক্রিয়ায় রাগ বা গালমন্দ করেন।
সন্তান কী পড়বে, কোথায় ভর্তি হবে, কোন বিষয়ে আগ্রহ—তা না জেনে বা না বুঝে অভিভাবক নিজের পছন্দ চাপিয়ে দেন।এতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও উৎসাহ নষ্ট হয় এবং তার ভেতরে এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।
বর্তমান যুগ যতোটা না পড়াশোনা ভিত্তিক তার থেকেও বড় বিষয় হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট। কিন্তু বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের থেকেও বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সিজিপিএ প্রতি নোংরা চিন্তা ভাবনা। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রজন্মরা সিজিপিএ ছাড়া সৃজনশীলতার কাজ পছন্দ করে না বা জানেই না। এরও বেশকিছু কারণ রয়েছে।
সিজিপিএ বা একাডেমিক রেজাল্টকে এখনো অনেক পরিবার ও সমাজ ‘সফলতার একমাত্র মাপকাঠি’ হিসেবে দেখে। এতে শিক্ষার্থীরা চাপের মধ্যে পড়ে যায় এবং সৃজনশীল চর্চাকে সময় দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয় না।
বাংলাদেশসহ অনেক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখনো মূলত পরীক্ষাভিত্তিক মূল্যায়নের দিকে ঝুঁকে থাকে। এতে শেখার চেয়ে নম্বর পাওয়াটা বেশি গুরুত্ব পায়। এই কারণে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতা বা উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে গুরুত্ব দিতে শেখে না।
সৃজনশীল কাজের জন্য যেমন—ল্যাব, ওয়ার্কশপ, থিঙ্কিং ক্লাব, ওপেন প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি দরকার, সেগুলোর অনেক সময় অভাব থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা জানেই না যে তারা কীভাবে তাদের ধারণাগুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।
অনেকেই সৃজনশীল হতে চায়, কিন্তু কিভাবে শুরু করতে হয় বা কীভাবে একটি প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে হয়—এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা না থাকায় তারা দ্বিধায় পড়ে যায় এবং শেষে শুধু পড়াশোনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
ভুল করার ভয় বা ব্যর্থতার আতঙ্ক অনেক তরুণকে সৃজনশীল পথে হাঁটতে নিরুৎসাহিত করে। তারা ভাবে— ‘সবাই যখন CGPA-তেই মনোযোগ দিচ্ছে, আমি যদি অন্য কিছু করি আর ব্যর্থ হই, তাহলে কী হবে?’
তাছাড়া যখন সবাই একই বিষয় পড়ে, একইভাবে পড়াশোনা করে, তখন তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে পড়ে। কোনো বিশেষ দক্ষতা বা আলাদা কিছু না থাকলে বেকার থেকে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়।
তাছাড়াও দেশের চাকরি বাজারে সীমিত সুযোগ হয়ে পড়েছে, সেইসাথে রয়েছে পেশাভিত্তিক শিক্ষার ঘাটতি। আর সেইসাথে রয়েছে সরকারি-বেসরকারি সেক্টরের মাঝে সমন্বয়ের অভাব।
বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের আত্মহত্যার প্রবণতা দিনকে দিন বাড়ছে। শিক্ষার্থীদের হতাশার নীরব প্রতিবাদ আত্মহত্যার পরিসংখ্যানের দিকে তাকালেই এর ভয়াবহতার চিত্রের প্রতিফলন ফুটে উঠবে।
সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আঁচল ফাউন্ডেশনের সমীক্ষায় অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার কারণগুলোর মধ্যে অ্যাকাডেমিক চাপ উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৪ দশমিক দুই শতাংশ অ্যাকাডেমিক চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন।
এর মধ্যে স্কুলশিক্ষার্থী ৫৯ দশমিক শূন্য নয় শতাংশ, কলেজ শিক্ষার্থী ২৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী নয় দশমিক শূন্য নয় শতাংশ।
২০২৪ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ মানসিক অস্থিরতার কারণে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন।
বাড়ছে স্কুলপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা _
গত বছর ৪৯ দশমিক চার শতাংশ স্কুলশিক্ষার্থী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। এই পরিসংখ্যান অল্প বয়সী শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ এবং তাদের জীবনে চলমান সংকটের ভয়াবহ বাস্তবতাকে সামনে এনেছে।এছাড়া, ২৩ দশমিক দুই শতাংশ কলেজশিক্ষার্থীর অকাল প্রাণ ঝরেছে।
আর এই আত্মহত্যার দিকে ঢাকায় আত্মহত্যার পরিমাণ বেশি। আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে, ২৯ শতাংশ। এরপর রয়েছে খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগ, যথাক্রমে ১৭ দশমিক সাত এবং ১৫ দশমিক আট শতাংশ।
রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে আত্মহত্যার হার ছিল ১০ দশমিক সাত শতাংশ করে। এছাড়া, রংপুরে সাত দশমিক সাত শতাংশ, ময়মনসিংহে পাঁচ দশমিক পাঁচ শতাংশ এবং সিলেটে আত্মহত্যার হার দুই দশমিক নয় শতাংশ।
অন্যদিকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের হার ছিল ছয় দশমিক আট শতাংশ। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১২ বছর বয়সী পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ছিল সবচেয়ে বেশি, ৪৭ দশমিক ছয় শতাংশ।
এর পরে ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই হার ছিল ৪৭ দশমিক ছয় শতাংশ এবং ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের মধ্যে এটি কমে চার দশমিক আট শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
লিঙ্গভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পুরুষ মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ৫৭ দশমিক ১৪ শতাংশ এবং নারীদের ৪২ দশমিক নয় শতাংশ।
এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও আত্মহত্যার উচ্চহার সমীক্ষায় দেখা গেছে, আত্মহত্যাকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১৭ দশমিক ৭৪ শতাংশই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থী। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর হার ৬৫ দশমিক ৪৬ শতাংশ এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদের ৩৪ দশমিক ৫৪ শতাংশ। পাশাপাশি ডিপ্লোমা শূন্য দশমিক ছয় শতাংশ এবং সদ্য পড়াশোনা শেষ করা শিক্ষিত বেকার শূন্য দশমিক ছয় শতাংশ।
এইবার আসা যাক বেকারত্বের হারের দিকে। আমাদের দেশের যেসব শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র স্কিলবিহীন পড়াশোনা করে শুধুমাত্র সিজিপিএ বাড়ানোর লক্ষ্যেই পড়তে চায় তারা জানেই না দেশে বেকারত্বের হার কত পরিমাণে বাড়ছে। আর অন্যদিকে নেই পড়াশোনার বিষয় অনুযায়ী চাকরির সুব্যবস্থা।
দেশে বেকারত্ব আরও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)প্রকাশিত ত্রৈমাসিক শ্রমশক্তি জরিপে চলতি অর্থবছরের অক্টোবর-ডিসেম্বর প্রান্তিকে বেকারত্বের হার বেড়ে ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশে পৌঁছেছে। বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ২৭ লাখ ৩০ হাজার।
শ্রমশক্তি জরিপের (অক্টোবর-ডিসেম্বর) প্রান্তিকের তথ্য বলছে, ১৯তম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব লেবার স্টাটিসটিসিয়ানস (আইসিএলএস) অনুযায়ী দেশে বর্তমানে বেকারত্বের হার ৪ দশমিক ৬৩ শতাংশ। ২০২৩ এর একই সময়ে এ হার ছিল ৩ দশমিক ৯৫ শতাংশ। ১৩তম আইসিএলএসে ডিসেম্বর শেষে দেশের বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। ডিসেম্বর শেষে ১৯তম আইসিএলএস অনুযায়ী দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বেড়ে ২৭ লাখ ৩০ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ২০২৩ এ একই সময়ে ছিল ২৪ লাখ।
বাংলাদেশ দেশে বেকারত্ব আরও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)এর হিসাব অনুযায়ী, ১৩তম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব লেবার স্টাটিসটিসিয়ানস (আইসিএলএস)এ ডিসেম্বর শেষে বেকারত্বের হার ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। আগের বছরের একই সময়ে এ হার ছিল ৩ দশমিক ২০ শতাংশ। এই পুরোনো হিসাবে দেশে বেকারের সংখ্যা বর্তমানে ২৬ লাখ ১০ হাজার। আগের বছরের একই সময়ে এ হার ছিল ২৩ লাখ ৫০ হাজার।
বিবিএসের সংজ্ঞা মোতাবেক,বাংলাদেশে বেকার জনগোষ্ঠী মূলত তারাই, যারা গত সাত দিনে কমপক্ষে এক ঘণ্টাও কোনো কাজ করেনি, কিন্তু কাজ করার জন্য গত সাতদিন ও আগামী দুই সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত ছিলেন এবং গত ৩০ দিনে বেতন বা মজুরি বা মুনাফার বিনিময়ে কোনো না কোনো কাজ খুঁজেছেন। তাছাড়াও উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বিনিয়োগ পরিবেশ না থাকা ও ব্যাংক ঋণের সুদহার বেশি হওয়ায় বেকারত্ব বেড়েছে।
এছাড়াও আরো বেশকিছু কারণ লক্ষ্য করা যায়।বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখনো তাত্ত্বিক জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষার অভাব, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা এবং বাস্তবমুখী দক্ষতার ঘাটতির কারণে শিক্ষার্থীরা শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতা করতে পারছেন না। ফলে তারা চাকরির জন্য যোগ্য হলেও কার্যকর কর্মী হিসেবে বিবেচিত হয় না।
প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক তরুণ কর্মবাজারে প্রবেশ করছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হচ্ছে না। ম্যানুফ্যাকচারিং, আইটি বা হাইটেক খাতে কর্মসংস্থান বাড়লেও তা প্রয়োজনীয় হারে নয়। অনেক তরুণ শুধু সরকারি চাকরির পেছনে ছুটে, ফলে প্রাইভেট সেক্টর বা উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ কম।
নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশের অভাব এবং সামাজিক বাধার কারণে অনেক নারী কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে না। অনেক কর্মসংস্থানই অস্থায়ী বা অনানুষ্ঠানিক, যেখানে চাকরির নিরাপত্তা নেই এবং দীর্ঘমেয়াদি ক্যারিয়ার গড়া যায় না।অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারণে কিছু চাকরি কমে যাচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী অটোমেশনের কারণে অনেক কর্মক্ষেত্রেই মানুষের প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে। যেমন: ব্যাংকিং, ম্যানুফ্যাকচারিং ও রিটেইল সেক্টরে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কম দক্ষ কর্মীদের চাহিদা কমেছে।
যথোপযুক্ত অবকাঠামো, দীর্ঘসূত্রতা, সার্বিক পরিস্থিতি অস্থিতিশীলতার কারণে অনেক দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হন না। ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না।
দেশের অনেক তরুণ এখনো শুধুমাত্র সরকারি চাকরির আশায় বসে থাকেন। তবে সরকারি চাকরির সংখ্যা সীমিত, অথচ প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বেশি। ফলে এই মানসিকতা বেকারত্ব বাড়াচ্ছে।
দেশের শিল্প খাত এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্প্রসারিত হয়নি। বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তিনির্ভর কোম্পানি, আন্তর্জাতিক মানের সেবা খাত এখনো পর্যাপ্ত হারে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। যে গুটিকয়টি খাত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে, সেগুলোও তুলনায় অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক এবং সীমিত সুযোগসম্পন্ন।
নেতৃত্ব, টিমওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন, ডিজিটাল লিটারেসি, প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন বা ভাষাজ্ঞান—এসব স্কিল না থাকায় তরুণরা আধুনিক চাকরির বাজারে টিকে থাকতে পারছেন না।
আর তাই তরুণ প্রজন্মের শিক্ষাথীদের নম্বর বন্টনের ভয় থেকে বের করে নিয়ে আসতে হলে অভিভাবক এবং শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং সময়োপযোগী দায়িত্ব নিতে হবে।
প্রথমত, নম্বরকে নয়, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে একটি শিশুর মেধা, সামর্থ্য বা ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা কখনোই যৌক্তিক নয়। অভিভাবক ও শিক্ষকরা যদি শেখার প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেন, তাহলে শিক্ষার্থীরাও বুঝবে যে তারা শেখার জন্য পড়ছে, নম্বরের জন্য নয়। এতে শেখার প্রতি আগ্রহ বাড়বে এবং মানসিক চাপ কমবে।
দ্বিতীয়ত, ভুলকে শেখার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। অনেক সময় শিক্ষক ও অভিভাবকরা পরীক্ষায় ভুল হলে কঠোর সমালোচনা করে থাকেন। এতে শিক্ষার্থীরা ভয় পায়, লুকিয়ে ফেলে নিজের অক্ষমতাকে। অথচ ভুল থেকে শেখার সুযোগ তৈরি করলে শিক্ষার্থীরা নির্ভয়ে প্রশ্ন করতে পারবে, বুঝতে পারবে কোন ক্ষেত্রে উন্নতি প্রয়োজন।
তৃতীয়ত, তুলনামূলক মানসিকতা ত্যাগ করা জরুরি। ‘তোমার বন্ধু ৯০ পেয়েছে, তুমি কেন ৮০ পেলে?’—এই ধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। প্রতিটি শিশুই আলাদা; তাদের শেখার ধরন ও গতিও আলাদা। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল নিজের আগের ফলাফলের সঙ্গে বর্তমানটিকে তুলনা করে উন্নয়নের চেষ্টা করা।শিক্ষার্থীদের শুধু পরীক্ষার ফলাফলের ওপর মনোনিবেশ না করে সার্বিক বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এটি ক্রীড়া, কলা ও সংস্কৃতি এবং অন্যান্য সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে করা যেতে পারে।
চতুর্থত, খোলা মন ও ইতিবাচক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অভিভাবক ও শিক্ষক উভয়ের উচিত শিক্ষার্থীর সঙ্গে নিয়মিত কথা বলা, তার চিন্তা-ভাবনা শোনা, এবং তাকে বোঝানো যে সে যেমন আছে, তেমন করেই ভালোবাসা ও সমর্থন পাবে।
সেইসাথে স্কুল কলেজে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। মা–বাবার সন্তানদের মানসিক সহায়তা কীভাবে দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে জানানোর জন্য স্কুলভিত্তিক কর্মশালা বা সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে। প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সদস্যরাও শিক্ষার্থীদের মানসিক সহায়তায় ভূমিকা রাখতে পারে। এ সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে সচেতনতামূলক কর্মশালা করা যেতে পারে, যাতে তারা পরীক্ষার সময় ও ফলাফলের পরে শিক্ষার্থীদের কীভাবে সমর্থন করতে পারে, তা শিখতে পারে।
স্কুলগুলো বিদ্যমান হেল্পলাইন ও শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের জন্য উপলব্ধ মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদারদের তথ্য প্রচার করতে পারে। এটি শিক্ষার্থীদের জানাবে যে তাদের প্রয়োজনে সহায়তা পাওয়া যায়।
ফলাফল প্রকাশের আগের সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্বেগ হয়। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টিকে সঠিকভাবে পার করানোর সহজ উপায় হলো খোলাখুলি আলোচনা। এতে করে তাদের মধ্যে থেকে ভয়ের ভিত্তি সড়ে দাঁড়ায় এবং ইতিবাচক প্রত্যাশা স্থাপন হয়। শিক্ষাবর্ষজুড়ে শিক্ষকদের পরীক্ষা, বিশেষ করে শুধু ফলাফল নয়, সে সম্পর্কে আলোচনা স্বাভাবিক করা উচিত। শুধু সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার ওপর জোর না দিয়ে, ফলাফলকে শিক্ষার্থীর যাত্রার মাত্র একটি দিক হিসেবে তুলে ধরুন। এটি শিক্ষার্থীদের বুঝতে সাহায্য করে যে তাদের মূল্যায়ন শুধু পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হয় না, ফলে যেকোনো মূল্যে সেরা ফলাফল করার চাপ কমে।
শিক্ষার্থীদের আগের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বা নমুনা প্রশ্ন সরবরাহ করুন। এটি তাদের পরীক্ষার ফরম্যাটের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সাহায্য করে, উদ্বেগ কমায় এবং তাদের জ্ঞানের ওপর মনোযোগ দিতে দেয়। সম্ভাব্য প্রশ্ন নিয়ে খোলা আলোচনা করতে উৎসাহিত করুন, এটি প্রস্তুতির অনুভূতি এবং সহযোগী শিক্ষাকে উন্নীত করে।
পরীক্ষার চাপ মোকাবিলায় অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপযুক্ত কৌশল দিয়ে শিক্ষার্থীদের সজ্জিত করতে হবে। বিক্ষিপ্ত কৌশলগুলো অত্যন্ত উপকারী হতে পারে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা, হালকা ব্যায়াম বা হাতে–কলমে শিক্ষামূলক কাজ করার মতো কার্যক্রমের মাধ্যমে মানসিকভাবে উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্বস্ত প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা, যেমন শিক্ষক, কাউন্সিলর বা অভিভাবক, এটিও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রাপ্তবয়স্করা মূল্যবান নির্দেশনা দিতে পারে এবং উদ্বেগ বা চাপের সঙ্গে লড়াই করা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সমর্থন ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে।
অনেক অভিভাবকেরই হয়তো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা নেই। পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষার সময় তাদের সন্তানদের সমর্থন করার কৌশলগুলোর ওপরও মনোযোগ দিন। এ সভাগুলো অভিভাবকদের সন্তানদের উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে এবং মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য কার্যকর সরঞ্জাম সরবরাহ করতে পারে।
অভিভাবকদের বুঝতে সাহায্য করুন যে তাদের সন্তানের অর্জিত দক্ষতা পরীক্ষার ফলাফলের চেয়ে বেশি মূল্যবান। পরীক্ষাগুলো একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রমের মূল্যায়ন করতে পারে, তবে পড়াশোনার প্রক্রিয়া সমস্যা সমাধান, সমালোচনা চিন্তাধারা এবং সময় ব্যবস্থাপনা করার মতো মূল্যবান দক্ষতা গড়ে তোলে। এ স্থানান্তরযোগ্য দক্ষতাগুলো যেকোনো ক্ষেত্রে বা এমনকি দৈনন্দিন জীবনে সফলতার জন্য জরুরি। এ বৃহত্তর সুবিধাগুলো তুলে ধরা অভিভাবকদের তাদের সন্তানের পারফরম্যান্স সম্পর্কে উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করতে পারে।
বিদ্যালয়জুড়ে একটি সমন্বিত পদ্ধতি জরুরি। ফলাফলের আগের সময়টিতে জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীরা যখন তরুণদের পরামর্শ দেয়, তখন সহপাঠী সমর্থন কর্যক্রম গড়ে তোলার পক্ষে কাজ করুন। এটি একটি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগত অনুভূতি দেয় এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সহানুভূতি এবং নেতৃত্ব দক্ষতা অনুশীলন করার অনুমতি দেয়। স্কুল কাউন্সিলররা শিক্ষার্থী এবং অভিভাবককদের উদ্বেগগুলো মোকাবিলা করার জন্য সহজলভাবে উপলব্ধ আছে, তা নিশ্চিত করতে হবে। উদ্বেগ বা চাপের সঙ্গে লড়াই করা শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের উপস্থিতি সান্ত্বনা এবং নির্দেশনার উৎস হতে পারে।
স্কুল সম্প্রদায় কেবল তার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অভিভাবকদের জন্য কর্মশালাগুলো সংগঠিত করতে হবে, যাতে নিজেদের উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষার্থীর চাপ বোঝা এবং মানসিক সুস্থতা উন্নীত করার কৌশলগুলোয় মনোযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উভয়ের জন্য উপলব্ধ বিদ্যমান হেল্পলাইন বা সহায়তা গ্রুপগুলো প্রচার করার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে উপকরণগুলো সহজে উপলব্ধ করা যাবে, প্রয়োজনে সহায়তা পাওয়া যাবে এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা এবং যোগাযোগ করার গুরুত্ব, সহানুভূতি এবং অন্যদের কথা শোনার দক্ষতা শেখাতে হবে। এতে করে নিঃসাহায্য বোধ করা শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস এবং বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পাবে।
শিক্ষার গণ্ডির বাইরেও জ্ঞান ও সৃজনশীলতার বিকাশ করাতে হবে। কারণ আজকের তরুণ প্রজন্ম আগামী দিনের নেতৃত্ব দিবে। কিন্তু যদি তাদের শিক্ষা কেবল পাঠ্যবই ও পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তারা হয়তো সার্টিফিকেটধারী হবে, কিন্তু বাস্তবজ্ঞান ও সৃজনশীলতার দিক থেকে পিছিয়ে পড়বে। তাই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়াশোনার বাইরেও বাহ্যিক জ্ঞান এবং সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো এখন সময়ের দাবি।
প্রথমত, সহশিক্ষা কার্যক্রমে গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, বিজ্ঞান মেলা বা রোবটিকস ক্লাবের মতো কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনার পরিধি বাড়ায়। এসব চর্চার মাধ্যমে তারা বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা, আত্মবিশ্বাস এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন করে।
দ্বিতীয়ত, বাস্তবমুখী শিক্ষা এবং জীবনদক্ষতা শেখানো প্রয়োজন। অর্থব্যবস্থা, পরিবেশ সচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধি, নাগরিক দায়িত্ব বা ডিজিটাল নিরাপত্তা—এই বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের শেখানো হলে তারা হবে আরও পরিপক্ব ও সচেতন। একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি এই বাহ্যিক জ্ঞানই তাদের জীবনে কাজে লাগবে।
তৃতীয়ত, গ্রন্থাগার ও পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় ও কলেজে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ পাঠাগার তৈরি করে শিক্ষার্থীদের বই পড়ার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে। ক্লাসের বাইরেও সাহিত্যের, ইতিহাসের বা বিজ্ঞানের নানা বিষয় পড়ে তারা চিন্তার গভীরতা অর্জন করতে পারে।
চতুর্থত, উন্মুক্ত আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দিলে তারা ভাবতে শেখে, প্রশ্ন তুলতে শেখে। শিক্ষকদের উচিত হবে শ্রেণিকক্ষে কেবল পাঠ না দিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার ও নিজের মত প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া।
পঞ্চমত, প্রযুক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো জরুরি। ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের কনটেন্ট দেখতে পারে, অনলাইন কোর্স করতে পারে, এমনকি গবেষণাও করতে পারে। তবে প্রযুক্তি যেন শুধুই বিনোদনের মাধ্যম না হয়ে জ্ঞানের হাতিয়ার হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী স্নাতক সম্পন্ন করছে। কিন্তু চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতা এতটাই তীব্র যে, ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী কর্মসংস্থানের বাইরে থেকে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো — শিক্ষাজীবনের সঙ্গে কর্মজীবনের সংযোগের অভাব। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি দক্ষতা অর্জন এবং উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার প্রস্তুতি নেওয়া এখন সময়ের দাবি।
প্রথমত, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী স্কিল ডেভেলপমেন্টে মনোযোগ দিতে হবে। বিশ্ব এখন দক্ষতার যুগ। শুধুমাত্র পাঠ্যবই মুখস্থ করে ডিগ্রি অর্জন করলে চলবে না। তরুণদের শেখা উচিতডিজিটাল স্কিল। যেমন গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট, কনটেন্ট ক্রিয়েশন, সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ডেটা অ্যানালাইসিস। কমিউনিকেশন স্কিল। যেমন: বাংলা ও ইংরেজিতে স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ, ইমেইল লেখা, পাবলিক স্পিকিং। প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ও টিমওয়ার্ক, যেমন: বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাব বা ইভেন্টের মাধ্যমে এ দক্ষতা অর্জন সম্ভব। সমস্যা সমাধান ও ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, যেমন: নানা সমস্যার বিশ্লেষণ করে নিজের মতামত গঠন করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
দ্বিতীয়ত, বাস্তবমুখী অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। ইন্টার্নশিপ, পার্ট-টাইম কাজ, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম কিংবা ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। এতে কেবল আত্মবিশ্বাসই বাড়ে না, ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের ভিত্তিও তৈরি হয়। এতে একদিকে কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ে, অন্যদিকে চাকরির ক্ষেত্রে রেফারেন্স তৈরি হয়।
তৃতীয়ত, উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। চাকরি খোঁজার পাশাপাশি ‘চাকরি দেওয়ার’ মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনেই ছোট উদ্যোগ শুরু করা যেতে পারে—যেমন অনলাইন ব্যবসা, কোচিং সেবা, হস্তশিল্প তৈরি, অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট, ই-কমার্স ইত্যাদি।
উদ্যোক্তা হতে হলে শিখে রাখতে হবে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (Business Plan) তৈরি,বাজার বিশ্লেষণ ও কাস্টমার চাহিদা বোঝা, ডিজিটাল মার্কেটিং ও ব্র্যান্ডিং,ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রাথমিক জ্ঞান, আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও বাজেটিং।
চতুর্থত, নেটওয়ার্ক গড়ে তুলুন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নানা সেমিনার, ওয়ার্কশপ, কনফারেন্স ও অনলাইন কমিউনিটিতে যুক্ত থেকে নিজেকে পরিচিত করে তুলুন। এই নেটওয়ার্কই ভবিষ্যতে কাজ বা উদ্যোগে সহযোগী হতে পারে।
পঞ্চমত, ব্যর্থতাকে ভয় নয়, শিক্ষা হিসেবে নিন।ছাত্রজীবনে উদ্যোগ শুরু করে সফল না হলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। প্রতিটি ভুল ও ব্যর্থতা ভবিষ্যতের জন্য শিক্ষণীয়। যারা সাহস করে ঝুঁকি নেয়, তারাই একদিন সফল উদ্যোক্তা হয়ে ওঠে। সেইসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে ক্যারিয়ার বিষয়ক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ক্যারিয়ার ফেয়ারের আয়োজন হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের সিভি লেখার কৌশল, ইন্টারভিউ প্রস্তুতি শেখানো দরকার।সফল তরুণ উদ্যোক্তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এনে বক্তব্য রাখা, তাদের অভিজ্ঞতা শোনানো।এতে অনুপ্রেরণা জন্মায় এবং উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি আগ্রহ জন্মায়।
ষষ্ঠত তরুণদের জন্য সরকার ও বেসরকারি খাতের তরফে স্টার্টআপ ফান্ড, প্রশিক্ষণ ও মেন্টরশিপ প্রদান করা উচিত।শিক্ষার আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন। বাজারমুখী শিক্ষা চালু করতে হবে (যেমন: আইটি, সফট স্কিল, কারিগরি শিক্ষা)। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইন্ডাস্ট্রি-সংযুক্ত কোর্স অন্তর্ভুক্তি স্কুল পর্যায় থেকেই ভোকেশনাল ও স্কিল-ভিত্তিক শিক্ষা চালু।
প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। বেকারদের জন্য ফ্রি বা ভর্তুকিযুক্ত প্রশিক্ষণ। ডিজিটাল স্কিল যেমন: প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক ডিজাইন, ফ্রিল্যান্সিং শেখানো। স্টার্টআপদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ ও ভর্তুকি প্রদান। ইনকিউবেশন সেন্টার ও ব্যবসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং কর-ছাড় ও প্রণোদনার ব্যবস্থা। সেইসাথে সরকারী ও বেসরকারী চাকরিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত করা। এবং লোভী স্বার্থান্বেষী মহলরা অঘটন ঘটাতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সরকারি চাকরির সংখ্যা বাড়ানো নয়, বরং দক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ বাড়ানো।
বর্তমান প্রজন্ম এখন ডিজিটাল প্রযুক্তিতে আগ্রহী। তাই যারা গার্মেন্টস ও কৃষিভিত্তিক চাকরির কাজে আগ্রহী তাদের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংযোজন ঘটানো। এতে করে তরুণ প্রজন্মরা সফট স্কিল কাজও শিখবে। গার্মেন্টস শিল্পে যেমন: ডিজিটাল মেশিনারিজ, অটোমেটেড কাটিং ও সেলাই প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টের কাজ শিখবে ঠিক তেমনি অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক চাকরিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয়, সারের পরিমাণ, কীটনাশক ব্যবহার এবং বাজারমূল্য সংক্রান্ত তথ্য মোবাইল অ্যাপ বা এসএমএস-এর ব্যবহার করে কৃষকদের কীভাবে সচেতন করা যায় শিখবে।
কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে CSR এর অংশ হিসেবে তরুণদের স্কিল ট্রেনিং চালু করতে উৎসাহিত করা। ইন্টার্নশিপ ও অন-জব ট্রেনিংয়ের সংখ্যা বাড়ানো। নতুন ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহীদের জন্য মেন্টরশিপ, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্ক সরবরাহ। সফল উদ্যোক্তাদের প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে অভিজ্ঞতা বিনিময় ও উদ্ভাবনী ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া। আইটি, এড-টেক, হেলথটেক, ই-কমার্স খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো। গ্রামাঞ্চলেও প্রযুক্তি ভিত্তিক কাজের সুযোগ সৃষ্টি। কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মীদের জন্য নিরাপত্তা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, ডে-কেয়ার সুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিত করা। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ ফান্ড ও প্রশিক্ষণ চালু করা।
বেকারত্ব একটি একক সমস্যা নয়—এটি অর্থনীতি, শিক্ষা, সমাজ ও প্রযুক্তির সমন্বিত এক প্রতিফলন। তাই এর সমাধানও হতে হবে সমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী। তাই সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নীতিগত সহায়তা ও পরিবেশ তৈরি করতে হবে, আর নিতে হবে কর্মসংস্থানের ভার। তাহলেই গড়ে উঠবে একটি কর্মমুখর, দক্ষ ও আত্মনির্ভর বাংলাদেশ।
পরিশেষে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হতে হবে যেখানে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে চিন্তা করার সুযোগ থাকে, বাহ্যিক জ্ঞানের অন্বেষণ থাকে, এবং সৃজনশীলতা বিকাশের পথ খোলা থাকে। শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো একজন সচেতন, চিন্তাশীল ও মানবিক নাগরিক গড়ে তোলা—এটা ভুলে গেলে চলবে না। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুধু ডিগ্রির জন্য নয়, বরং নিজেকে কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করার শ্রেষ্ঠ সময়। এখনকার যুগে শুধু ভালো রেজাল্ট নয়, বরং ‘কোন কোন স্কিল জানো’ এবং ‘সেই স্কিল দিয়ে কী করো’ — সেটাই মূল বিষয়। চাকরি পাওয়া না-পাওয়ার মধ্যে জীবন আটকে থাকা উচিত নয়। উদ্যোক্তা হওয়া, স্বাধীনভাবে কাজ করা, কিংবা নতুন কিছু তৈরি করাও সফলতার পথ।
তরুণদের শুধু দিক দেখানো নয়—তাদের সম্ভাবনা চিনতে শেখানো, সুযোগ তৈরি করা, এবং ব্যর্থ হলেও পাশে দাঁড়ানোর মতো সমাজ ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার সময় এখনই। তরুণরা যদি এই সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগায়, তবে বেকারত্বের অভিশাপকে রূপান্তর করা যাবে সম্ভাবনার সোনালী পথে। এভাবেই যদি গটবাধা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যদি আসতে আসতে পরিবর্তন আনা যায়, তাহলে আর কোনো স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হতাশাগ্রস্থ হয়ে নীরব প্রতিবাদ হিসেবে আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিতে হবে না।
লেখক: শিক্ষার্থী, সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম অধ্যয়ন বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা