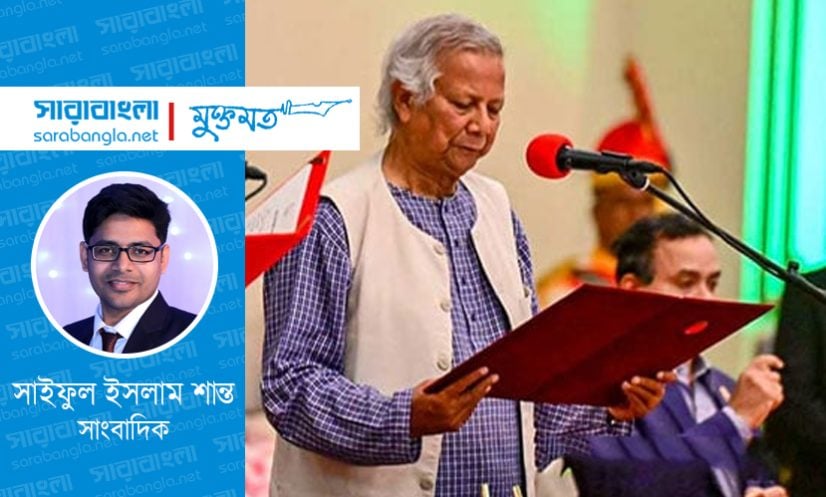২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ‘ছাত্র-জনতার গণআন্দোলন’ নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। দীর্ঘ ১৫ বছরের টানা শাসনের অবসান ঘটিয়ে ক্ষমতায় আসে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যার নেতৃত্ব দেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ে সরকার কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে, আবার কিছু সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জও সামনে এসেছে।
ছাত্র–জনতার আন্দোলনের পটভূমিতে গঠিত ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার জনগণের কাছে নতুন আশা ও প্রত্যাশার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিনের দমনপীড়ন, গণতন্ত্রহীনতা ও প্রশাসনিক জটিলতার পর মানুষ ভেবেছিল এবার হয়তো পরিবর্তনের সূচনা হবে। প্রথম দিকের সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো রাজনৈতিক পরিবেশে কিছুটা মুক্তি ফিরিয়ে আনা। সমাবেশের সুযোগ আগের তুলনায় বেড়েছে। প্রশাসনিক কাঠামোতে সংস্কারের প্রাথমিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য নতুন পে কমিশন ও প্রণোদনা ঘোষণা হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের উপস্থিতি জোরালো করার চেষ্টা চলছে। এসব উদ্যোগ জনমনে আশার আলো জাগিয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ঘোষণা বা প্রাথমিক পদক্ষেপে জনগণের চাহিদা পূরণ হয় না। বিনিয়োগে চলছে মন্দা, এর সাথে বেড়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়। একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্যও তৈরি করা যায়নি। এ কারণে আস্থার সংকট কাটেনি। জনগণ চায় নিরপেক্ষ নির্বাচন, অর্থনীতিতে স্বস্তি, বিচারব্যবস্থায় ন্যায়বিচার এবং মৌলিক খাতে দৃশ্যমান উন্নতি।
সাফল্যের খতিয়ান
প্রথমেই বলতে হয় রাষ্ট্রযন্ত্র পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার কথা। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রভাব ও দলীয়করণের জটিলতা কাটিয়ে প্রশাসনকে নিরপেক্ষ করার সরকারের উদ্যোগ প্রশংসিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন কিছু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, যদিও সেগুলোর প্রভাব এখনো পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়।
অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ থাকলেও সরকার তুলনামূলক স্থিতিশীলতা আনতে পেরেছে। অর্থাৎ রেমিটেন্স বেড়েছে, রপ্তানি চালু আছে, আমদানি কম হওয়ার ফলে বৈদেশিক লেনদেনে একটা ভারসাম্য এসেছে এবং সরকার অনেক পুরোনো বিদেশি ঋণ পরিশোধ করেছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সহায়তায় আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানিমুখী নীতি কার্যকর হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষাকৃত ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে—এটি একটি বড় সাফল্য।
সবচেয়ে বড় অর্জন সম্ভবত রাজনৈতিক রূপান্তরের আশ্বাস। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের ঘোষণা শুধু জনগণের মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আশার সঞ্চার করেছে। এছাড়া কূটনীতিতে নতুন ভারসাম্য লক্ষ্য করা গেছে। একক কোনো দেশের ওপর নির্ভরতা থেকে সরে এসে বহুমাত্রিক ও ভারসাম্যপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি গড়ে তোলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, চিকিৎসা সহায়তা ও সংকট মোকাবিলায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা ‘সার্ক’কে পুনরুজ্জীবন ও আসিয়ান সদস্যপদ অর্জনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিসরে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে কূটনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশকে নতুনভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।
সবশেষে, বিচার ব্যবস্থায় কিছু আলোচনাযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার, গুম-খুন ইত্যাদি বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। যদিও সেগুলোর ফলাফল সামনে আসতে সময় লাগবে, তবুও এই প্রক্রিয়া জনগণকে কিছুটা আশা জাগাচ্ছে।
রাজনীতিবিদরা মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্জন হলো—রাষ্ট্রীয় সংস্কারের বিষয়ে ডান-বাম সব রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারা। অনেকগুলো সংস্কার বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। যদিও কিছু দল আপত্তি জানালেও সরকার ইতোমধ্যে ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’ প্রকাশ করেছে এবং ‘জুলাই সনদ’ তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। তবে এই দুটি প্রস্তাবের বাস্তবায়ন ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও মতভেদ রয়ে গেছে।
সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণ কাজ
অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ হলো স্বচ্ছ, অংশগ্রহণমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন আয়োজন। একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক ঐক্যমত গড়ে তোলা যায়নি। একই সঙ্গে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক হিংসা ও ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার মতো মৌলিক খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ এর প্রত্যক্ষ সুফল পায়।
অনেক সংস্কার এখনও কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। জনগণ দ্রুত পরিবর্তন চেয়েছিল কিন্তু বাস্তবে অনেক পদক্ষেপে গড়িমসি করা হয়েছে। সংবিধান সংস্কারের আলোচনা আটকে আছে বিশেষজ্ঞ মহল ও রাজনৈতিক দলগুলোর টানাপোড়েনে।
রাস্তায় ছিনতাই, সন্ত্রাস এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ কমেনি। মব সৃষ্টি করে আতঙ্ক ছড়ানোয় জনগণের নিরাপত্তাবোধ পুরোপুরি ফিরে আসেনি, যা সরকারের জন্য অশনিসঙ্কেত।
অর্থনীতি বিশেষভাবে চাপে রয়েছে—বিনিয়োগ কমেছে, সরকারি হিসাবে মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তেমন দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। শিল্পোন্নয়ন ও প্রযুক্তি খাতে সরকারের প্রতিশ্রুতি এখনো কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ।
আগামী পথচলা
এখানে সরকারকে দুটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, আস্থা তৈরি করা। জনগণের আস্থা ফিরে পেলে রাজনৈতিক সংস্কার টেকসই হবে। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও গ্রহণযোগ্য করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক বাস্তবায়ন। শুধু আন্তর্জাতিক সহায়তার উপর নির্ভর করলে চলবে না, স্থানীয় উৎপাদন, কৃষি ও প্রযুক্তি খাতে বিপ্লবী উদ্যোগ প্রয়োজন। তরুণ সমাজকে সৃজনশীল কাজে সম্পৃক্ত করা না গেলে ভবিষ্যৎ অচলাবস্থার দিকে যাবে।
এক বছরে ইউনূস সরকারের অর্জন ও সীমাবদ্ধতা আমাদের সামনে দুটি ভিন্ন দিক তুলে ধরেছে। একদিকে দেখা গেছে সংস্কার ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা, অন্যদিকে রয়ে গেছে পুরোনো সমস্যার ছায়া। জনগণের প্রত্যাশা এখন আর শুধু প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ নয়, তারা চায় দৃশ্যমান অগ্রগতি ও এর বাস্তবায়ন। আগামী পথচলায় সরকারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে আস্থা পুনর্গঠন এবং গণতান্ত্রিক সংস্কারকে টেকসই করা। যদি এ কাজে সফল হওয়া যায়, তবে এই অধ্যায় ইতিহাসে লেখা হবে “পুনর্জাগরণের সময়” হিসেবে। আর যদি ব্যর্থতা এসে যায়, তবে সেটি কেবল আরেকটি হারানো সম্ভাবনার গল্প হয়ে থাকবে।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট