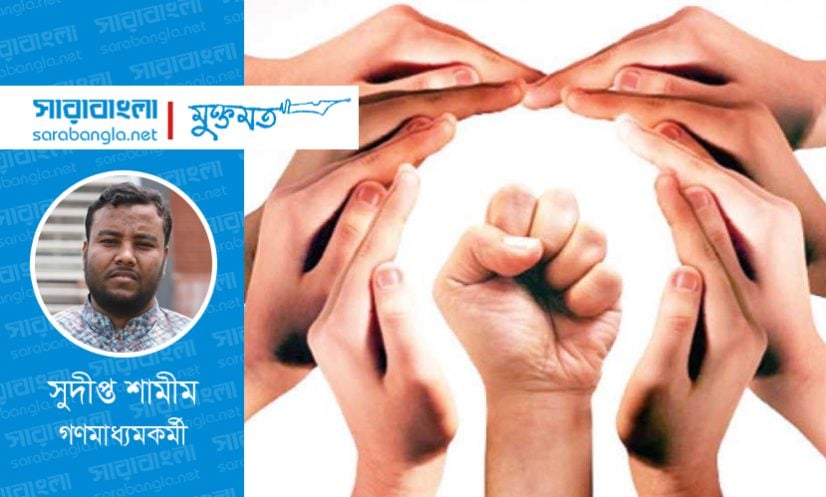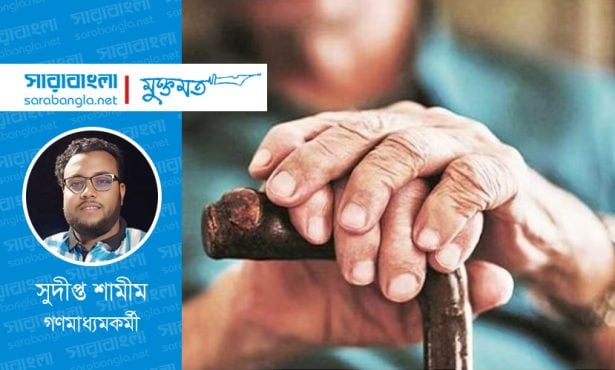মানবসভ্যতার ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—ঐক্যবদ্ধ মানুষের শক্তি অদম্য, আর বিভক্ত মানুষের পরিণতি সবসময় করুণ। যে জাতি ভেতরে ভেঙে পড়ে, বাইরের শত্রুরা তাকে সহজেই দমন করতে পারে। আমরা যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখতে ব্যর্থ হই, তবে বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, নিজেদের অস্তিত্বই টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যাবে। বিশ্ব ইতিহাসে রোমান সাম্রাজ্যের পতন, মুসলিম উম্মাহর দুর্বলতা কিংবা উপমহাদেশে বিদেশি শক্তির আগ্রাসন—সব ক্ষেত্রেই ভেতরের অনৈক্য বড় কারণ হিসেবে কাজ করেছে। আবার ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমরা দেখেছি, বাঙালিরা ঐক্যবদ্ধ ছিল বলেই পাকিস্তানি সেনাদের পরাজিত করতে পেরেছিল। আজকের বিশ্ব প্রতিনিয়ত ষড়যন্ত্র, প্রতিযোগিতা ও আধিপত্য বিস্তারের খেলায় ব্যস্ত। যে জাতি ভেতরে ঐক্যহীন, তাদের নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে সহজ। তাই বর্তমান বাস্তবতায় টিকে থাকতে চাইলে ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।
ইতিহাস থেকে শিক্ষা
মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা বহন করে। সপ্তম শতকে নবী করিম (সা.)-এর নেতৃত্বে যখন আরবরা ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়বিচার ও ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তখন মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই তারা দুনিয়ার এক-তৃতীয়াংশ শাসন করেছে। মরুভূমির অসংগঠিত জনগোষ্ঠী এক বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জ্ঞান, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সভ্যতার দিক থেকে পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু সেই শক্তিই ভেঙে পড়ে যখন খিলাফতের ভেতরে বিভক্তি শুরু হয়। মতপার্থক্য, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লোভ ও বিদেশি প্রভাব মুসলিম উম্মাহকে টুকরো টুকরো করে দেয়। ফলে যাদের একসময় দেখে পৃথিবীর পরাশক্তিরা ভয়ে কাঁপত, তারাই ধীরে ধীরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইউরোপের ইতিহাসও একই শিক্ষা দেয়। মধ্যযুগে ইউরোপীয় রাজ্যগুলো ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত ছিল। একেকজন রাজা, একেকজন ডিউক নিজের ক্ষমতার লড়াইয়ে মত্ত ছিল। এ কারণে তারা বাইরের আক্রমণের সহজ শিকার হয়েছিল। মঙ্গোল আক্রমণ কিংবা পরবর্তীতে অটোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার ইউরোপের সেই বিভক্তিরই সুযোগ নিয়েছিল। কিন্তু একই ইউরোপ যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর শিক্ষা নেয়, তখন তারা ‘ইউরোপীয় ইউনিয়ন’-এর পতাকার নিচে একত্রিত হয়। ফলাফল—আজ তারা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি।
বাংলার ইতিহাসও আমাদের শেখায়, ঐক্য হারালে শক্তি বৃথা যায়। পাল ও সেন রাজাদের সময় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার লড়াই ও গোষ্ঠীবাজির কারণে বিদেশি আক্রমণকারীরা সহজেই আধিপত্য বিস্তার করেছে। দিল্লি সালতানাত ও মোগলরা বাংলাকে জয় করতে পেরেছিল প্রধানত এখানকার বিভক্তির সুযোগ নিয়ে। এমনকি ঔপনিবেশিক শক্তি ব্রিটিশরাও একক শক্তিতে ভারত দখল করতে পারেনি; তারা স্থানীয় মহাজন, জমিদার ও বিশ্বাসঘাতকদের কাজে লাগিয়েছে। অর্থাৎ ভেতরের অনৈক্য বাইরের শত্রুর শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এর উল্টো শিক্ষাও আমরা পেয়েছি মুক্তিযুদ্ধ থেকে। ১৯৭১ সালে রাজনীতির ভিন্নতা, মতের পার্থক্য, ব্যক্তিগত স্বার্থ—সবকিছু ভুলে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-যুবক থেকে শুরু করে নারী ও শিশু পর্যন্ত সবাই একটি পতাকার নিচে দাঁড়িয়েছিল। সেই ঐক্যের শক্তিই পাকিস্তানি সেনাদের পরাজিত করে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। ঠিক তেমনি ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে যে গণ-আন্দোলন, যে বিপ্লব বাংলাদেশ দেখেছে, সেটিও ঐক্যের শক্তির আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ। নানা মত-পার্থক্য ও দলীয় বিভাজন সত্ত্বেও জনগণ তখন গণতন্ত্র ও অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে এক কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিল। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী—সবাই একই স্রোতে মিশে গিয়েছিল। সেই ঐক্যের কারণে শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন, গ্রেপ্তার, এমনকি হত্যাযজ্ঞও মানুষকে থামাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত জনতার ঐক্যের চাপেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বড় পরিবর্তন আসে।
অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিটি শিক্ষা একই সত্যকে প্রমাণ করে—ঐক্যই আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, আর বিভক্তিই আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা।
বর্তমান বাস্তবতা
দুঃখজনক হলেও সত্য, আজকের বাংলাদেশে আমরা প্রতিদিন বিভাজনের নতুন নতুন রূপের মুখোমুখি হচ্ছি। রাজনীতি থেকে শুরু করে সমাজ, শিক্ষা থেকে সংস্কৃতি, এমনকি ব্যক্তিজীবনেও বিভক্তির রেখা ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। এই বিভাজন কেবল পারিবারিক বা সামাজিক সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি করছে না, বরং রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজনীতিতে দলীয় বিভক্তি এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের দাবি প্রায়ই দলীয় হিসাব-নিকাশে ঢাকা পড়ে যায়। শাসক দল হোক বা বিরোধী দল—পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণের কারণে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুতেও ঐক্যমতের ভিত্তি তৈরি হয় না। ফলে বড় বড় উন্নয়ন পরিকল্পনা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার, কিংবা অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের মতো মৌলিক বিষয়ও দলীয় স্বার্থের কারণে ব্যাহত হয়।
সমাজের দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখা যায়। ধনী-গরিবের বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। শহরাঞ্চলের মানুষ উন্নত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে, অথচ গ্রামের মানুষ এখনো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। চিকিৎসা, শিক্ষা, এমনকি বিশুদ্ধ পানি বা নিরাপদ বাসস্থানের ক্ষেত্রেও এ বৈষম্য স্পষ্ট। এর ফলে সমাজে শ্রেণিভেদ আরও প্রকট হয়ে উঠছে, যা মানুষকে কাছাকাছি আনার বদলে আলাদা করে রাখছে। শিক্ষাক্ষেত্রও এই বিভাজনের শিকার। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনেক সময় ইতিবাচক দিকের বদলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। ঐক্য, সহমর্মিতা বা সহযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠার পরিবর্তে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, হিংসা কিংবা বিভাজনই প্রাধান্য পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক প্রভাব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভক্তি আরও বাড়িয়ে তুলছে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেও মতভেদের কারণে সহমর্মিতার জায়গা সংকুচিত হচ্ছে। ধর্মীয় পরিচয়, ভাষা বা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে একে অপরকে ছোট করে দেখার প্রবণতা সমাজে বেড়েছে। অথচ ইতিহাস বলছে—যখনই আমরা ভ্রাতৃত্ব ও সহনশীলতা দেখিয়েছি, তখনই জাতি হিসেবে শক্তিশালী হয়েছি।
সবচেয়ে বড় আশঙ্কা হলো, এই ভাঙনের ফাঁকেই বাইরের শক্তিগুলো প্রবেশের সুযোগ পায়। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বড় শক্তিধর দেশগুলো সবসময় দুর্বলদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এমন উদাহরণ অসংখ্যবার ঘটেছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা কিংবা নেপাল—সব দেশই ভেতরের বিভাজন ও রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাইরের শক্তির প্রভাবের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ভেতরে ঐক্য না থাকলে বড় শক্তিগুলো সহজেই আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক ইস্যু নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবে। অতএব, বর্তমান বাস্তবতায় আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি শিক্ষা হলো—ঐক্য ছাড়া টিকে থাকা সম্ভব নয়। রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভাজনের দেয়াল ভেঙে আমাদেরকে সহমর্মিতা, সমঝোতা ও ভ্রাতৃত্বের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। নইলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেরি হবে না।
অন্য দেশের উদাহরণ
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য বড় শিক্ষার ভাণ্ডার। দেখা যায়, যেখানে জনগণ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে দ্রুত অগ্রগতি ও শক্তিশালী অবস্থান তৈরি হয়েছে। চীন উদাহরণস্বরূপ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। দেশটিতে বহু জাতিগোষ্ঠী, ভাষা ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা রয়েছে। তাও তারা জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রেখেছে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো থেকে নানা হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেও চীন অভ্যন্তরীণ শক্তি ও শৃঙ্খলাকে কাজে লাগিয়ে অল্প কয়েক দশকের মধ্যে অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে বিশ্বশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের শিক্ষা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনী প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ সবই ঐক্যের ওপর নির্ভরশীল।
জাপানের উদাহরণও চমকপ্রদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। টোকিও, হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের ধ্বংসাবশেষ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোকে ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে—শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম ও জাতীয় উদ্দেশ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে। ফলে জাপান অল্প সময়ের মধ্যেই প্রযুক্তি, শিল্প ও অর্থনীতিতে বিশ্বশক্তি হিসেবে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। সিঙ্গাপুরও অনন্য উদাহরণ। ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র, যেখানে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মানুষ বসবাস করে। তবু তারা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বজায় রেখেছে এবং দেশকে বিশ্বের অর্থনৈতিক মডেল হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। তাদের পরিকল্পিত শহর উন্নয়ন, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ এবং সামাজিক শৃঙ্খলা একে শক্তিশালী করেছে।
এই উদাহরণগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, বৈচিত্র্য বা ভিন্ন মত থাকা কোনো সমস্যা নয়; সমস্যা আসে তখন, যখন সেই ভিন্নতা বিভাজনে রূপ নেয়। আমরা কেন পারবো না? আমরা পারবো, যদি নিজেদের ভেতরের বিভাজনের সব দেয়াল ভেঙে ফেলতে পারি। যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা এবং জাতীয় স্বার্থকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপরে রাখতে পারি। ইতিহাস ও সমসাময়িক বিশ্বের উদাহরণগুলো দেখাচ্ছে, ঐক্য ছাড়া কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। অতএব, আমাদের প্রথম ধাপ হওয়া উচিত নিজেরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা, ছোটখাটো বিভাজন ও কলহ ভুলে গিয়ে জাতীয় লক্ষ্যকে এক কণ্ঠে গ্রহণ করা। তখনই আমরা চীনের, জাপানের বা সিঙ্গাপুরের মতো শক্তিশালী জাতি হিসেবে উঠে দাঁড়াতে পারব।
সমাধানের পথ
ঐক্য বজায় রাখা শুধুই স্লোগান নয়; এটি একটি সচেতন সামাজিক চর্চা, যা প্রতিটি স্তরে আমাদের জীবনে কার্যকর হতে হবে। একে কেবল মৌখিকভাবে প্রচার করলে চলবে না, বরং বাস্তব অভ্যাস ও সামাজিক সংস্কৃতির অংশ করতে হবে।
সহনশীলতা গড়ে তোলা: ভিন্ন মত, দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত থাকা স্বাভাবিক। তবে সহমর্মিতা থাকলে এই ভিন্নতাগুলো সমস্যা হিসেবে গড়ে ওঠে না। আমাদের সমাজে সহনশীলতার অভাবই নানা কলহ ও বিভাজনের মূল কারণ। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে ছোটবেলা থেকেই সহনশীলতার চর্চা গড়ে তুললে বড় বিভাজন কমানো সম্ভব।
আলোচনার সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনা: মতের অমিলকে সংঘাত বা শত্রুতায় রূপ দেওয়া মানে সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায়, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে সমালোচনা আর বিতর্ককে সহিংসতায় রূপান্তর করা হয়। সঠিক পথ হলো—মতবিরোধ থাকলেও আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করা। স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে কমিউনিটি মিটিং পর্যন্ত এই সংস্কৃতিকে প্রচলিত করতে হবে।
জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া: দলের স্বার্থ, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ওপরে রাখা বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির জন্য হুমকি। আমাদের দেশে ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ঘটনা দেখিয়েছে, যে জায়গায় দলীয় স্বার্থ জাতীয় স্বার্থের চেয়ে প্রাধান্য পায়, সেখানে উন্নয়ন ও সামাজিক ঐক্য ব্যাহত হয়। তাই রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংগঠন এবং নাগরিকরা সর্বদা দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
শিক্ষায় ঐক্যের পাঠ: শিশু-কিশোরদের শুরু থেকেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। স্কুল ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কেবল পাঠ্যবই বা পরীক্ষার জন্য নয়; শিশুদের মধ্যে সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং দলগত সহযোগিতার মানসিকতা তৈরি করা উচিত। এটি ভবিষ্যৎ সমাজকে সংহত ও শক্তিশালী করে।
ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিবাচক ব্যবহার: ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিভাজনের হাতিয়ার নয়, বরং মিলনের সেতু হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এটি শুধু সমাজকে সংহত রাখে না, বরং জাতীয় ঐক্যের শক্তিকে আরও দৃঢ় করে।
সত্যিকারের ঐক্য মানে কেবল বাহ্যিক দৃঢ়তা নয়; এটি হলো সমাজের প্রতিটি স্তরে সহমর্মিতা, সমঝোতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার অভ্যাস। এই চর্চা ছাড়া আমরা কেবল শ্লোগান দিতে পারব, কিন্তু বাস্তবে শক্তিশালী ও একত্রিত সমাজ গড়ে তুলতে পারব না।
ঐক্যের বিজয়: একসাথে থাকার শক্তি
আজ আমাদের সামনে দুটি পথ খোলা। আমরা চাইলে নিজেদের মধ্যে বিভাজন, স্বার্থের লোভ ও ক্ষুদ্র কলহকে টিকিয়ে রেখে ধ্বংসের দিকে যাত্রা করতে পারি, অথবা ঐক্যের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দাঁড়াতে পারি, শক্তিশালী হয়ে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু রাখতে পারি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে—ঐক্যবদ্ধ জাতিকে কোনো শত্রু সহজে পরাজিত করতে পারে না। যুগে যুগে আমরা দেখেছি, যেখানে মানুষ বিভক্ত হয়েছিল, সেখানে বাইরের শক্তি সহজেই প্রভাব বিস্তার করেছে; যেখানে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, সেখানে বিপদ যত বড়ই হোক, সেটি জয় সম্ভব হয়েছে। আমাদের এখন প্রয়োজন প্রতিজ্ঞা; স্বার্থের ছোটখাটো দেয়াল ভেঙে ফেলব, পারস্পরিক বিশ্বাসের সেতু গড়ব। একে অপরের কষ্ট বুঝব, পরস্পরের শক্তি কাজে লাগাব। দেশের উন্নয়ন, সমাজের শান্তি এবং প্রজন্মের ভবিষ্যৎ শুধুমাত্র তখনই সম্ভব, যখন আমরা ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেব। ঐক্য মানে কেবল বাহ্যিক দৃঢ়তা নয়; এটি হলো পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার শক্তি। যখন আমরা সবাই একসাথে থাকব—বিভাজনের অন্ধকার নেই, শত্রুর ভয় নেই, আর আমাদের বিজয় নিঃসন্দেহে স্থায়ী হবে। তাই আজই শুরু করতে হবে ঐক্যের চর্চা, ইতিহাস থেকে শেখা শিক্ষা প্রয়োগ করা, এবং সমাজকে একটি শক্তিশালী, সমন্বিত ও দায়িত্ববান জাতিতে পরিণত করা। কারণ সত্যিকারের বিজয় আসে তখনই, যখন আমরা সবাই একসাথে, এক হৃদয়ে, এক লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাই।
লেখক: কলামিস্ট, গণমাধ্যমকর্মী ও সংগঠক