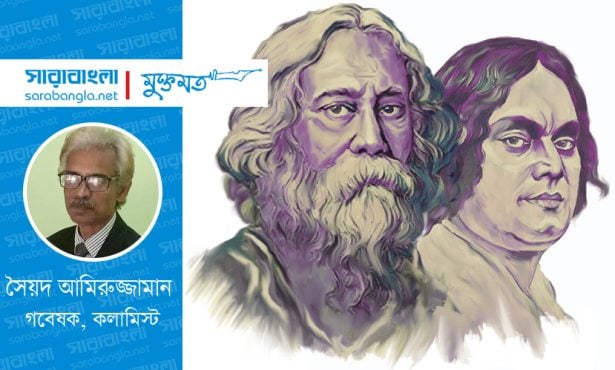স্বপ্ন, সংগ্রাম ও ইলার উত্তরাধিকার
বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এমন কিছু নাম আছে, যাদের জীবন কেবল ব্যক্তিগত কাহিনি নয়—বরং এক জাতির মুক্তির পথের প্রতীক। তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী কমরেড ইলা মিত্র তাদেরই অন্যতম। তার নেতৃত্ব, ত্যাগ ও নির্যাতনের ইতিহাস আমাদের জাতিসত্তায় অনুরণিত হয়, যেন সংগ্রাম ও মানবিক মর্যাদার এক অবিচল প্রতীক।
আজ, তার ২৩তম প্রয়াণ দিবসে তাকে স্মরণ করা মানে কেবল এক নারীর বীরত্ব নয়, বরং বঞ্চিত কৃষক, শ্রমিক ও নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা।
জন্ম, পরিবার ও শিক্ষা: সম্ভ্রান্ত বংশে বিপ্লবের বীজ
ইলা মিত্র (জন্মনাম ইলা সেন) ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের বাংলার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল। সম্ভ্রান্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা এই মেয়েটির জীবনের পথচলা শুরু হয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে— বেথুন স্কুল ও কলেজে পড়াশোনা করে তিনি হয়ে ওঠেন তৎকালীন বাংলার ক্রীড়া জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র।
অ্যাথলেটিকস, বাস্কেটবল, ব্যাডমিন্টন, টেনিকোয়েট— সবক্ষেত্রেই ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। এমনকি ১৯৪০ সালে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকের জন্য নির্বাচিত প্রথম বাঙালি নারী হিসেবে তিনি ইতিহাসে স্থান করে নেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিক স্থগিত হয়— তবু তার লড়াই থামেনি। রাজনীতি তখন তাকে টানছিল অন্য এক ময়দানে— মানুষের মুক্তির লড়াইয়ে।
রাজনীতিতে প্রবেশ ও কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাস
কলেজজীবনে ইলা সেন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়ো আন্দোলন’-এ তিনি আত্মগোপনে থেকে কাজ করেন, সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করেন। ১৯৪৩ সালে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে, এবং একই বছরে ‘মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি’-তে যুক্ত হয়ে নারীর রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃত্বে আসেন।
এই সময়েই তার পরিচয় হয় মালদহের তরুণ কৃষক নেতা রমেন মিত্রের সঙ্গে; ১৯৪৫ সালে তাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর ইলা চলে যান মালদহ জেলার নবাবগঞ্জের রামচন্দ্রপুরহাট গ্রামে, যেখানে পরবর্তীকালে তার নেতৃত্বে ইতিহাস সৃষ্টি হয়।
পটভূমি: ভূমি ব্যবস্থার শোষণ ও তেভাগা আন্দোলনের আবির্ভাব
বাংলার কৃষক সমাজের ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জমিদারি ও জোতদারি প্রথা ছিল শোষণের মূল ভিত্তি।
ব্রিটিশ শাসনামলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হলে কৃষকের মালিকানা হারিয়ে যায়; জমিদারদের অধীনে জন্ম নেয় জোতদার নামে নতুন মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণি। কৃষককে বাধ্য করা হতো উৎপাদিত ফসলের অর্ধেক—আধিয়ারি প্রথা—জোতদারকে দিতে। অর্থনৈতিক দুরবস্থা, ঋণের বোঝা ও ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ মন্বন্তর এই শোষণকে তীব্রতর করে তোলে।
এই প্রেক্ষাপটে, ১৯৪৬ সালে কমিউনিস্ট পার্টি ও সর্বভারতীয় কৃষক সমিতি তিনভাগের দুইভাগ ফসল কৃষকের দাবি তোলে—এটাই ছিল তেভাগা আন্দোলনের সূত্রপাত। দিনাজপুরে কমরেড হাজী দানেশের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, নাচোল ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চলে।
নাচোলের রাণী: মাঠে-মাঠে কৃষকের পাশে
দেশভাগের পর ১৯৪৭ সালে ইলা মিত্রের শ্বশুরবাড়ি এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সময় মুসলিম কৃষক, আদিবাসী সাঁওতাল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি হয়ে ওঠেন ‘রাণীমা’—তাদের অভিভাবক, সংগঠক ও প্রেরণা। তার নেতৃত্বে নাচোলের কৃষক আন্দোলন রূপ নেয় এক গণঅভ্যুত্থানে। কৃষকেরা নিজেদের ফসলের ন্যায্য অংশ আদায়ের দাবিতে ফসল ঘরে তোলার সময় জোতদারদের প্রভাব অগ্রাহ্য করতে শুরু করে। এতে প্রশাসনের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।
১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় অসংখ্য সাঁওতাল কৃষক। পাল্টা জনরোষে নিহত হয় কয়েকজন পুলিশ। এই সংঘর্ষ ইতিহাসে স্থান পায় ‘নাচোল বিদ্রোহ’ নামে—যার কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিলেন ইলা মিত্র।
গ্রেফতার, নির্যাতন ও মানবিক প্রতিরোধের ইতিহাস
১৯৫০ সালের জানুয়ারিতেই পুলিশ ইলা মিত্রকে গ্রেফতার করে। এরপর শুরু হয় মানবসভ্যতার ইতিহাসের এক ভয়াবহ অধ্যায়—তার ওপর চালানো হয় অকথ্য শারীরিক ও যৌন নির্যাতন।
তিনি পরে আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে বিস্তারিতভাবে সেই নির্যাতনের বর্ণনা দেন— কীভাবে তাকে উলঙ্গ করে মারধর করা হয়, গরম ডিম ও লোহার পেরেক দিয়ে নির্যাতন করা হয়, এমনকি ধর্ষণের শিকার হতে হয়— কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছু স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। এই জবানবন্দি আজও ন্যায়ের লড়াইয়ে নিপীড়িত নারীর সংগ্রামের এক অনন্য দলিল।
আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, ভারত ও পাকিস্তানের প্রগতিশীল জনগণ ইলা মিত্রের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড থেকে তিনি রক্ষা পান; পরে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
জেল, মুক্তি ও নতুন জীবনযুদ্ধ
চার বছর কারাবাসের পর ১৯৫৪ সালে ইলা মিত্রের শারীরিক অবস্থা মারাত্মকভাবে অবনতি ঘটলে তাকে প্যারোলে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তিনি আবার লেখাপড়ায় ফিরে আসেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. সম্পন্ন করেন এবং ১৯৫৮ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন।
রাজনীতিতেও তিনি সক্রিয় থাকেন— ১৯৭২ সাল থেকে পরপর চারবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটি, মহিলা ফেডারেশন, স্পোর্টস কাউন্সিল ও বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠনে তিনি নেতৃত্ব দেন।
সাহিত্য, অনুবাদ ও সাংস্কৃতিক কর্ম
ইলা মিত্র শুধু বিপ্লবী বা রাজনীতিক নন— তিনি ছিলেন এক সুলেখিকা ও অনুবাদক। তার অনূদিত গ্রন্থ ‘হিরোশিমার মেয়ে’ তাকে এনে দেয় সোভিয়েত ল্যান্ড নেহেরু পুরস্কার। এছাড়া ‘জেলখানার চিঠি’, ‘মনেপ্রাণে’ (দুই খণ্ড), ‘লেনিনের জীবনী’ ও ‘রাশিয়ার ছোটগল্প’— এগুলো তার সাহিত্যিক গভীরতা ও সমাজবোধের পরিচায়ক। তার লেখার ভাষা ছিল সংযত, যুক্তিনিষ্ঠ, কিন্তু হৃদয়ের গভীর মানবিক স্পন্দনে ভরপুর।
ইলা মিত্র ও নারীমুক্তি: প্রতিরোধের প্রতীক
ইলা মিত্র কেবল শ্রেণি-সংগ্রামের নেত্রী নন, তিনি নারীমুক্তিরও অগ্রদূত। তার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ নারী দেহের ওপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে উঠেছে। যখন সমাজ নারীকে নিছক আবেগ বা গৃহস্থালির সীমায় দেখতে অভ্যস্ত, তখন তিনি রাজনীতি, আন্দোলন, শিক্ষা, সাহিত্য— সবক্ষেত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। আজকের সমাজে নারী নির্যাতন, ভূমি বঞ্চনা, বৈষম্য ও শ্রমশোষণের বিরুদ্ধে প্রতিটি প্রতিবাদের অনুপ্রেরণা হয়ে আছেন তিনি।
সমাজতান্ত্রিক চেতনা ও রাজনৈতিক দর্শন
ইলা মিত্রের পুরো রাজনৈতিক জীবন সমাজতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবিক সমতার দর্শনের ওপর দাঁড়িয়ে। তিনি বিশ্বাস করতেন— ‘শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি ছাড়া কোনো রাষ্ট্র প্রকৃত স্বাধীন হতে পারে না।’
এই চিন্তাধারা কেবল অর্থনৈতিক প্রস্তাব নয়, বরং এক নৈতিক-রাজনৈতিক অঙ্গীকার। তেভাগা আন্দোলনের মূল দর্শন—ফসলের দুইভাগ কৃষকের অধিকার—ছিল উৎপাদন সম্পর্কের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। আজও বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার, কৃষকের অধিকার, নারীর সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নে ইলা মিত্রের চিন্তা প্রাসঙ্গিক।
উত্তরাধিকার ও প্রাসঙ্গিকতা
২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর, কলকাতায় ৭৭ বছর বয়সে ইলা মিত্রের মৃত্যু হয়। তবে, তার মৃত্যু তার আন্দোলনের সমাপ্তি নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের প্রগতিশীল আন্দোলন, কৃষক সংগঠন ও নারীমুক্তি চেতনায় তার নাম আজও উচ্চারিত হয় সম্মানের সঙ্গে।
আজ যখন কৃষি ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর বৈষম্য, কর্পোরেট দখল ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন অব্যাহত, তখন ইলা মিত্রের সংগ্রামের ইতিহাস নতুন করে মনে করিয়ে দেয়— ন্যায়বিচারের লড়াই কখনো বৃথা যায় না।
উপসংহার: রাণীমা থেকে বিপ্লবের চেতনা
ইলা মিত্র শুধু একজন নেত্রী নন, তিনি এক যুগের প্রতিচ্ছবি। তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়—খেলোয়াড় থেকে বিপ্লবী, নির্যাতিতা থেকে শিক্ষিকা—মানুষের মর্যাদা ও সমতার চিরন্তন বার্তা বহন করে। তেভাগা আন্দোলনের ‘রাণীমা’ আজও আমাদের বলে যান— ‘ন্যায় ও স্বাধীনতার লড়াই কোনো দেশের, কোনো ধর্মের নয়—এ লড়াই মানুষের।’
পরিশেষে, সমাজতন্ত্র অভিমুখী অসাম্প্রদায়িক জনগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যহীন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সমতা-ন্যায্যতার প্রশ্নে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনেই বিশ্বজনীন মহান এই গুণীর রাজনীতি, আত্মোৎসর্গ, জীবন সংগ্রাম, কীর্তি, ইতিহাস, তত্ত্ব ও অনুশীলন সম্পর্কে পাঠ প্রাসঙ্গিক ও জরুরী।
আজ তার প্রয়াণ দিবসে তাকে স্মরণ মানে আমাদের সমাজে ন্যায়বিচার, সমতা ও মানবিকতার চেতনা পুনঃস্থাপন করা।
জয়তু ইলা মিত্র। জয়তু তেভাগার রাণী।
লেখক: মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট