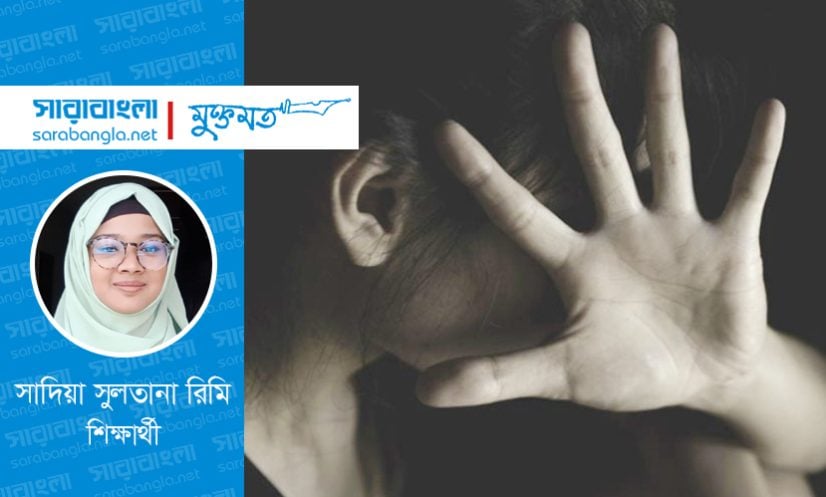যৌন হয়রানি কেবল একটি ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়, এটি একটি সামাজিক ব্যাধি। সমাজ, কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সর্বত্র এর বিষাক্ত ছোবল বিস্তৃত। কিন্তু এর চেয়েও ভয়ংকর হলো এই অপরাধকে ঘিরে থাকা এক গভীর নীরবতার সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিই নিপীড়কদের সুরক্ষা দেয় এবং শিকারকে বাধ্য করে অপমান আর কষ্ট নীরবে সয়ে যেতে। প্রশ্ন হলো এই নীরবতার অভেদ্য দেয়াল ভাঙবে কে? উত্তরটা জটিল, কারণ এর সাথে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা, ভয়, সামাজিক কলঙ্ক আর বিচারহীনতার এক দীর্ঘ ইতিহাস।
যৌন হয়রানির সংজ্ঞা শুধু শারীরিক আক্রমণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অবাঞ্ছিত স্পর্শ, ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, যৌন সুবিধা লাভের জন্য চাপ দেওয়া, অশ্লীল ছবি বা বার্তা পাঠানো এ সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এর শিকার হন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষ, তবে নারীরাই এর প্রধান শিকার। হয়রানির শিকার ব্যক্তি সমাজে লজ্জিত হন, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হন, কর্মক্ষেত্র বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, এমনকি অনেক সময় নিজের দোষ না থাকা সত্ত্বেও কাজ বা পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন।
যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিরা কেন চুপ থাকেন? এর পেছনে কাজ করে একাধিক শক্তিশালী সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণ। প্রথমত, রয়েছে ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা। হয়রানিকারী প্রায়শই ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী অবস্থানে থাকেন সেটা হতে পারে অফিসের বস, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা বা পরিবারের কোনো সদস্য। অভিযোগ করলে চাকরি হারানোর, একাডেমিক জীবন নষ্ট হওয়ার, বা আরও গুরুতর প্রতিশোধের শিকার হওয়ার ভয় থাকে। অনেক সময়, অভিযুক্ত ব্যক্তি এতটাই প্রভাবশালী হন যে তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস অধিকাংশেরই থাকে না।
দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজে ভুক্তভোগীকে দায়ী করার বা ‘ভিক্টিম ব্লেমিং’-এর এক ভয়াবহ সংস্কৃতি বিদ্যমান। হয়রানির শিকার হলেই সমাজ উল্টো প্রশ্ন তোলে ‘পোশাক কেন এমন ছিল?’, ‘রাতে একা কেন বেরিয়েছিল?’, ‘বিরোধিতা করেনি কেন?’। ফলে ভুক্তভোগী নিজেই নিজেকে দোষী ভাবতে শুরু করেন এবং সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে চুপ থাকেন। এই মানসিক চাপ একটি গভীর ক্ষত তৈরি করে।
তৃতীয়ত, বিচারহীনতার সংস্কৃতি এই নীরবতাকে আরও পাকাপোক্ত করে। অভিযোগ জানানোর পরও যদি যথাযথ তদন্ত না হয়, অভিযুক্ত ব্যক্তি পার পেয়ে যান, বা উল্টো ভুক্তভোগীর জীবন আরও কঠিন হয়ে ওঠে, তখন অন্যরা অভিযোগ করতে নিরুৎসাহিত হন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থলের অভ্যন্তরীণ কমিটিগুলোর নিষ্ক্রিয়তা, দীর্ঘসূত্রিতা, অথবা অভিযুক্তকে রক্ষার প্রবণতা বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা কমিয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে আইনি প্রক্রিয়াও দীর্ঘ ও জটিল হওয়ায় ভুক্তভোগীরা হয়রানিকে সয়ে যাওয়াকেই সহজ মনে করেন।
চতুর্থত, পারিবারিক ও সামাজিক চাপ। অনেক অভিভাবক বা পরিবারের সদস্যরা ভুক্তভোগীকে ‘সম্মান রক্ষার্থে’ বিষয়টি চেপে যেতে পরামর্শ দেন। কারণ, ‘কেলেঙ্কারি’ রটে গেলে সমাজে তাদের সম্মানহানি হবে বলে মনে করা হয়। ভুক্তভোগীর ব্যক্তিগত ট্রমা ছাপিয়ে তখন গুরুত্ব পায় সামাজিক মান-সম্মান।
নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙার দায়িত্ব কার?
এই বিষাক্ত নীরবতার জাল ছিন্ন করার দায়িত্ব এককভাবে কারো নয়, বরং সমাজ, রাষ্ট্র, প্রতিষ্ঠান ও প্রতিটি ব্যক্তির সম্মিলিত দায়িত্ব।
১. আইনের সঠিক প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংবেদনশীলতা:
প্রথমেই প্রয়োজন বিদ্যমান আইন ও আদালতের রায়গুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সেই নির্দেশ মেনে একটি শক্তিশালী ও সংবেদনশীল ‘যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি’ গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা বেশি হওয়া এবং বাইরের স্বাধীন সদস্য থাকা আবশ্যক। কমিটিগুলোর তদন্ত প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ, দ্রুত ও নিরপেক্ষ। অভিযুক্ত যত প্রভাবশালীই হোক না কেন, তার শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। একইসাথে, মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে, যাতে প্রকৃত ভুক্তভোগীরা সাহস হারান না।
২. ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে অবস্থান:
কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অপব্যবহারের সুযোগ কমাতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই নিজেদের আচরণের মাধ্যমে নজির স্থাপন করতে হবে। ক্ষমতার বলয়ে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা হয়রানির ঘটনা ঘটলে তা ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে মোকাবিলা করতে হবে। প্রতিষ্ঠানের সংস্কৃতি হতে হবে এমন, যেখানে কর্মীদের এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সম্মান সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়।
৩. জনসচেতনতা ও শিক্ষার বিস্তার:
প্রাথমিক শিক্ষাস্তর থেকেই যৌন হয়রানি কী, কেন এটি অপরাধ এবং এর পরিণতি কী—এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হবে। সচেতনতা সৃষ্টিতে পরিবার, গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। ‘না’ বলার অধিকার এবং নিজের শরীরের ওপর নিজের অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে। এই অপরাধের শিকার যে কেউ হতে পারে এবং এক্ষেত্রে ভুক্তভোগী কোনোভাবেই দায়ী নয়—এই বার্তাটি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছে দিতে হবে।
৪. মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমের দায়িত্বশীলতা:
গণমাধ্যম এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হতে পারে। তারা পারে নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙতে, ভুক্তভোগীর সাহস যোগাতে এবং বিচারহীনতার ঘটনাগুলোকে সামনে আনতে। তবে, খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর পরিচয় সুরক্ষায় এবং সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে হবে। সামাজিক মাধ্যমে অযথা ট্রল বা ভিক্টিম ব্লেমিং-এর বিরুদ্ধেও সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
৫. সাক্ষী ও সহকর্মীদের ভূমিকা:
যৌন হয়রানি শুধুমাত্র ভুক্তভোগী আর অভিযুক্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অনেক সময় নীরব সাক্ষীরাও এই অপরাধকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করেন। যখন কোনো হয়রানির ঘটনা ঘটে, তখন পাশে থাকা সহকর্মী বা বন্ধুর প্রতিবাদ, সমর্থন ও আইনি সহায়তা প্রদানে এগিয়ে আসা অত্যন্ত জরুরি। একজন সরব সাক্ষী নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে যুদ্ধটা দীর্ঘ এবং জটিল। এই নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙা মানে শুধু কয়েকটি অভিযোগের বিচার করা নয়, বরং আমাদের সামাজিক কাঠামোর গোড়ায় জমে থাকা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা, ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা এবং ভুক্তভোগীকে দোষারোপ করার প্রথাকে উপড়ে ফেলা। এই দেয়াল ভাঙতে এগিয়ে আসতে হবে ভুক্তভোগী, তার পরিবার, বন্ধু, সহকর্মী, প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রকে। নীরবতার সংস্কৃতি যদি নিপীড়ককে সাহস যোগায়, তবে সরবতার সংস্কৃতিই পারে ভুক্তভোগীকে মুক্তি দিতে। নীরবতার সংস্কৃতি ভাঙার দায়িত্ব আমাদের সকলের যে যার অবস্থান থেকে সাহস করে ‘না’ বলা এবং বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়ার মাধ্যমেই সমাজে পরিবর্তন আনা সম্ভব। যতদিন না পর্যন্ত প্রতিটি ভুক্তভোগী নির্ভয়ে অভিযোগ জানাতে পারছেন এবং ন্যায়বিচার পাচ্ছেন, ততদিন এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। নীরবতার সংস্কৃতির সমাপ্তি ঘটাতে সম্মিলিত কণ্ঠস্বরই একমাত্র পথ।
লেখক: শিক্ষার্থী, গণিত বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়