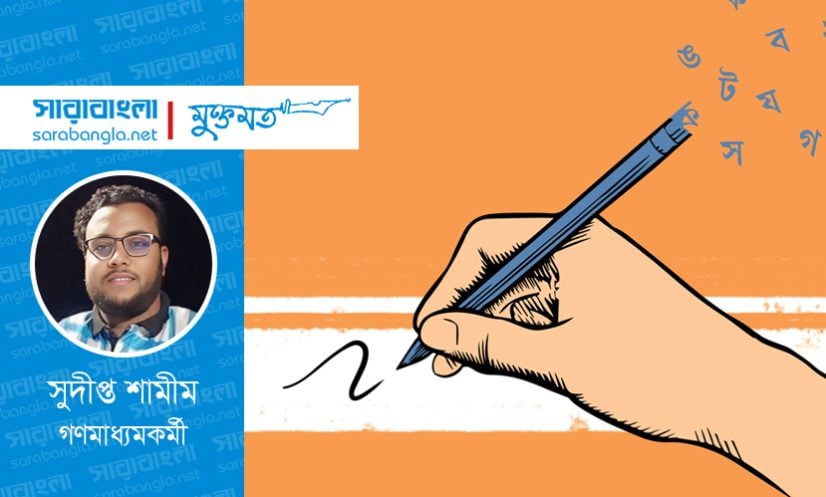আজকাল যে কারও হাতে স্মার্টফোন থাকলেই সে যেন সাংবাদিক। কেউ ভিডিও তুলছে, কেউ লাইভ দিচ্ছে, কেউ ঘটনার বিবরণ লিখে ফেসবুকে পোস্ট দিচ্ছে। যে কোনো দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, রাজনৈতিক সংঘাত কিংবা সামাজিক ঘটনার প্রথম খবর এখন অনেক সময় আসে কোনো সাধারণ পথচারীর মোবাইল থেকে। অনেকেই গর্বভরে বলেন, ‘আমরা সবাই সাংবাদিক!’ কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে খবর দেয়, সে কি সত্যিই সাংবাদিক?
এই প্রশ্নটাই আজ জরুরি। কারণ আমরা এমন এক সময়ের মধ্যে আছি, যখন তথ্যের বন্যা বইছে, কিন্তু সত্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই খবর দিচ্ছে, কিন্তু খুব কম মানুষই খবর যাচাই করছে। এক ক্লিকেই ছড়িয়ে পড়ছে অর্ধসত্য, গুজব আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তথ্য। সমাজে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে, মানুষ বিভক্ত হচ্ছে, আর সাংবাদিকতার প্রতি আস্থা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। এই তথ্য-অরাজক পরিস্থিতিতে মানুষ সহজেই প্রভাবিত হচ্ছে সামাজিক মিডিয়ার ট্রেন্ড ও জনপ্রিয়তার দৌড়ে, আর সত্য ও ন্যায্যতার মতো মূল্যবোধ পিছনে পড়ে যাচ্ছে।
নাগরিক সাংবাদিকতার উত্থান: আশীর্বাদ না অভিশাপ?
নাগরিক সাংবাদিকতা আসলে তথ্যের গণতন্ত্রীকরণ। আগে যেখানে সংবাদমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ ছিল কিছু পেশাদার প্রতিষ্ঠানের হাতে, সেখানে এখন সাধারণ মানুষও ঘটনার অংশ হতে পারছে। কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভিডিও করছে, কেউ দুর্নীতির প্রমাণ দিচ্ছে, কেউ সরকারি বা সামাজিক অনিয়ম তুলে ধরছে। এতে নির্যাতিত মানুষের কণ্ঠস্বর কিছুটা হলেও জোরালো হয়েছে, প্রান্তিক মানুষের কথা শহরের মানুষের কানে পৌঁছাচ্ছে। এ দিক থেকে এটি নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পরিবর্তন।
কিন্তু সমস্যা হলো, এই পরিবর্তনের মধ্যেই ঢুকে পড়েছে বিশৃঙ্খলা, অপেশাদারিত্ব আর উদ্দেশ্যপ্রণোদিততা। নাগরিক সাংবাদিকদের অনেকেই জানেন না, তথ্য যাচাই কীভাবে করতে হয়, কোনো ঘটনার ছবি প্রকাশ করা নৈতিক কি না, কারও মুখ দেখানো আইনসম্মত কি না। ফলাফল—সংবেদনশীল ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়, ভিকটিমের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। আরও বড় সমস্যা হলো, অনেকে এখন খবর দেয় ‘লাইক’, ‘ভিউ’ আর ‘ফলোয়ার’ বাড়ানোর জন্য। সাংবাদিকতা নয়, বরং বিনোদনই হয়ে দাঁড়িয়েছে মূল লক্ষ্য। একটি দুর্ঘটনার সময় কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, বরং ক্যামেরা নিয়ে দৌড়ে যায় ‘এক্সক্লুসিভ’ ফুটেজ নিতে। মানবতা হারিয়ে গেছে ভিউয়ের অন্ধ দৌড়ে।
পেশাদার সাংবাদিকতার সংকট: ভিতরে ঘুণ, বাইরে ঝড়
পেশাদার সাংবাদিকতার অবস্থাও খুব সুখকর নয়। অনেক সংবাদমাধ্যম এখন মালিকানার চাপ, রাজনৈতিক প্রভাব ও ব্যবসায়িক স্বার্থে জর্জরিত। সত্য প্রকাশের আগে চিন্তা করতে হয়—এতে কার ক্ষতি হবে? বিজ্ঞাপন কমে যাবে না তো? মালিক রাজি কি না? এই ভয়ের সংস্কৃতি পেশাদার সাংবাদিকতার বিশ্বাসযোগ্যতাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সংবাদকর্মীদের ওপর তৈরি হয়েছে আত্মনিয়ন্ত্রণের চাপ, ফলে অনেকেই আর সত্য উচ্চারণের সাহস পান না। কেউ কেউ পেশার মর্যাদা রক্ষা করতে চান, কিন্তু উপরের নির্দেশ আর অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের কাছে তাঁদের বিবেক বন্দি হয়ে যায়। অনেকেই বাধ্য হয়ে আপস করেন, কেউ চাকরি হারান, আবার কেউ নীরবে আত্মসমর্পণ করেন পেশার অমানবিক বাস্তবতার কাছে। তবু পার্থক্য এখানেই—একজন পেশাদার সাংবাদিক জানেন, ভুল করলে তার দায় আছে, আইনি ও নৈতিক জবাবদিহি আছে। তিনি জানেন, কোনো খবর প্রকাশের আগে তা যাচাই-বাছাই করা আবশ্যক, অপর পক্ষের বক্তব্য নেওয়া দায়িত্বের অংশ। এই জবাবদিহির মানসিকতাই একজন সাংবাদিককে আলাদা করে। কিন্তু নাগরিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এই জবাবদিহির জায়গাটা প্রায় শূন্য।
যখন সবাই সাংবাদিক, তখন কে শ্রোতা?
এখন সবাই ভিডিও করছে, সবাই মন্তব্য দিচ্ছে, সবাই বিশ্লেষণ করছে। ফলে প্রশ্ন দাঁড়ায়—তাহলে শ্রোতা বা পাঠক কে? যদি সবাই খবরের নির্মাতা হয়ে যায়, তাহলে খবরের গ্রহণকারী কোথায়? সমাজে তখন গড়ে ওঠে এক ধরনের ‘তথ্য-অরাজকতা’, যেখানে সবাই চিৎকার করছে, কিন্তু কেউ শুনছে না। প্রত্যেকে নিজেকে কেন্দ্র করে একেকটা ছোট ‘মিডিয়া দ্বীপ’ বানিয়ে ফেলেছে, যেখানে সত্যের চেয়ে মতামতই বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিতর্কের জায়গা হারিয়ে যাচ্ছে বিশ্লেষণের গভীরতা, আর জনমত গড়ে উঠছে আবেগ ও পক্ষপাতের ওপর ভিত্তি করে। এই অবস্থায় পেশাদার সাংবাদিকতাই হতে পারে সংবাদের শৃঙ্খলা ফেরানোর একমাত্র আশ্রয়। কারণ সাংবাদিকতা কেবল তথ্য পরিবেশন নয়, বরং তা হচ্ছে তথ্যের প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করা, সত্যের বিশ্লেষণ করা, সমাজে দায়বদ্ধ বার্তা পৌঁছে দেওয়া।
ভিউয়ের দৌড়ে হারিয়ে যাওয়া বিবেক
আজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভিউ মানেই প্রভাব, আর প্রভাব মানেই অর্থ। ফলে সত্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে জনপ্রিয়তা। কেউ গুজব ছড়ালেও তাতে ভিউ হলে সেটিই ‘সফল’ কনটেন্ট। এই সংস্কৃতি সাংবাদিকতাকে পরিণত করছে বাজারে বিক্রির পণ্য হিসেবে। সাংবাদিকতার নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, বস্তুনিষ্ঠতা—সবই হারাচ্ছে ‘অ্যালগরিদমের’ ভেতর।
আরও ভয়াবহ হলো, এই প্রতিযোগিতায় এখন অনেক পেশাদার সাংবাদিকও ‘ক্লিকবেইট’ শিরোনামে ঝুঁকছেন, যাচাই-বাছাই বাদ দিয়ে দ্রুত খবর প্রকাশে আগ্রহী হচ্ছেন। সংবাদ হয়ে উঠছে বিনোদন, আর পাঠক পরিণত হচ্ছে ভোক্তায়। ফলে মানুষ সংবাদমাধ্যমে নয়, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। এই পরিস্থিতিতে সত্য আর বিশ্লেষণ অনেকাংশে হারিয়ে যাচ্ছে, এবং জনমত প্রভাবিত হচ্ছে আবেগ, পক্ষপাত ও অতিরিক্ত সরলীকরণের ভিত্তিতে। সংবাদকের দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্ব এখন আগে কখনও যেমন প্রয়োজন, তেমনি চরম জরুরি হয়ে উঠেছে।
তবে নাগরিক সাংবাদিকতা অপ্রয়োজনীয় নয়
নাগরিক সাংবাদিকতাকে একেবারে বাতিল করা যায় না। বরং এটি মূলধারার সাংবাদিকতার জন্য একটি সহায়ক মাধ্যম হতে পারে। কারণ মাঠের প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে যা ধরা পড়ে, সেটি অনেক সময় মিডিয়ার ক্যামেরায় আসে না। একজন সাধারণ মানুষ ঘটনার সূত্র দিতে পারেন, প্রমাণ হাজির করতে পারেন, সমস্যার দিক নির্দেশ করতে পারেন। কিন্তু সেই তথ্য যাচাই, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার কাজটি করতে হবে পেশাদার সাংবাদিকদের। নাগরিক সাংবাদিকতা যদি দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা ও যাচাই-বাছাইয়ের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে এটি সংবাদজগতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে। তখন সাংবাদিকতা হবে এক যৌথ প্রয়াস—মানুষের হাতে তথ্য, সাংবাদিকের হাতে সত্য প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব, এবং সমাজের কাছে পৌঁছাবে নির্ভরযোগ্য, প্রমাণভিত্তিক সংবাদ যা কেবল দেখানো নয়, বরং বোঝাতে সক্ষম। একই সঙ্গে এটি জনগণকে সচেতন করতে, সামাজিক অনিয়ম তুলে ধরতে এবং সরকারের নীতি-প্রয়োগে তদারকি করতে কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।
শুধু ক্যামেরা নয়, কলমই ইতিহাসের শক্তি
যে সমাজে সবাই খবর দেয়, কিন্তু কেউ সত্য যাচাই করে না—সেই সমাজ ধীরে ধীরে বিশ্বাস হারায়। সাংবাদিকতা তখন ‘পেশা’ নয়, ‘অরাজকতা’ হয়ে দাঁড়ায়। আর যে সমাজে সাংবাদিকতার বিশ্বাস হারায়, সেখানে সত্যও একসময় পরাজিত হয়। তথ্যের এই বিশৃঙ্খলায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়, জনমত প্রভাবিত হয়, এবং সমাজের নৈতিক ভিত্তি কমজোরি হয়ে পড়ে।
সুতরাং নাগরিক সাংবাদিকতা যেমন দরকার, তেমনি পেশাদার সাংবাদিকতার গুরুত্বও অস্বীকার করার নয়। তথ্যের এই অরাজক সময়েও সত্যের পথ তৈরি করতে পারে কেবল পেশাদার সাংবাদিকতাই। যেখানে দায়িত্ব আছে, নীতি আছে, যাচাই-বাছাই আছে এবং সবচেয়ে বড় কথা- সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে।
যে ফোনের ক্যামেরা খবর ধরে, সেটি শক্তিশালী; কিন্তু যে কলম সত্য লিখে, সেটিই ইতিহাস বদলায়, সমাজের মান বজায় রাখে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার গড়ে তোলে।
লেখক: গণমাধ্যমকর্মী, কলামিস্ট ও সংগঠক