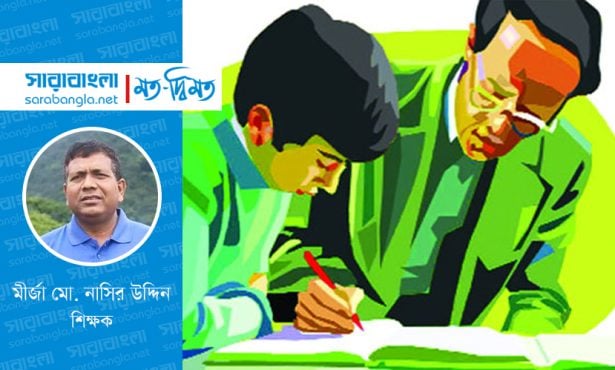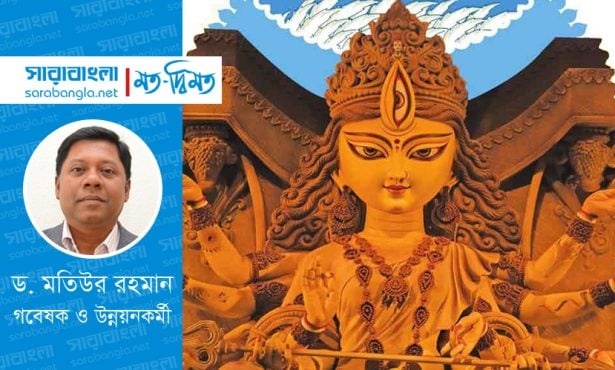সমাজবিজ্ঞান মানুষের আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক এবং সমষ্টিগত জীবনের জটিলতা বোঝার এক অন্তহীন প্রচেষ্টা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই শাস্ত্রের গবেষণার পদ্ধতি ও উপকরণ পরিবর্তিত হয়েছে, এবং বিস্তৃতও হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যেখানে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার এবং জরিপ ছিল মূল ভরসা, সেখানে আজকের যুগে যোগ হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিংয়ের মতো আধুনিক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি সমাজবিজ্ঞানের বিশ্লেষণকে কেবল গতিশীলই করছে না, বরং এক নতুন পদ্ধতিগত বিপ্লবের সূচনা করছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিপুল তথ্যভাণ্ডার থেকে শুরু করে জটিল সামাজিক নেটওয়ার্কের মডেলিং কিংবা ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়া—এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অভূতপূর্ব সম্ভাবনা তৈরি করছে। তবে এর পাশাপাশি রয়েছে নৈতিকতা, গোপনীয়তা ও বৈষম্যের মতো জটিল চ্যালেঞ্জ, বিশেষত বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে সামাজিক রূপান্তর দ্রুত ঘটছে কিন্তু তথ্যনিরাপত্তা ও ডেটা গভর্নেন্স এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী নয়।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বর্তমানে কাঁচা সামাজিক তথ্যকে অর্থবহ সমাজতাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টিতে রূপান্তর করার এক শক্তিশালী মাধ্যম। যেখানে প্রচলিত জরিপ বা সাক্ষাৎকার সামাজিক বাস্তবতার আংশিক চিত্র দেয়, সেখানে এআই বিভিন্ন উৎস থেকে ক্রমাগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে সক্ষম। এই প্রযুক্তি গবেষকদের এমন এক গভীরতা এবং ব্যাপকতা এনে দেয় যা আগে সম্ভব ছিল না।
১. ডেটা-চালিত অন্তর্দৃষ্টি: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োগ অসাধারণ হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষানীতি সংস্কার বা সুশাসন নিয়ে জনগণের মনোভাব জানতে চাইলে প্রচলিত জরিপে হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছানো কঠিন। কিন্তু এআই ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের লক্ষ লক্ষ পোস্ট, সংবাদ প্রতিবেদন ও অনলাইন আলোচনাকে একত্র করে মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। এই প্রক্রিয়া নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন সংস্থা ও গবেষকদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে, বিশেষত নগর পরিকল্পনা, জনস্বাস্থ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়।
২. সামাজিক নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণ: দীর্ঘদিন ধরে সমাজবিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংযোগের ধরন এবং এর প্রভাব বোঝার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে শ্রমবাজারের পরিবর্তন, শহরমুখী অভিবাসন এবং ডিজিটাল যোগাযোগের বিস্তার বাংলাদেশের সামাজিক নেটওয়ার্ককে দ্রুত রূপান্তরিত করছে। এই জটিল নেটওয়ার্কগুলোতে তথ্য প্রবাহ, প্রভাব বিস্তার কিংবা বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রসার কীভাবে ঘটে তা বোঝার জন্য ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বা জনস্বাস্থ্য সংকটের সময় মিথ্যা তথ্য কীভাবে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তা শনাক্ত করতে এআই-ভিত্তিক মডেল কার্যকর হতে পারে, যা সঠিক সময়ে জনসচেতনতা প্রচার বা প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে সহায়ক।
৩. ভবিষ্যৎ প্রবণতা পূর্বাভাস: ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়াতেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যাগত রূপান্তর, জলবায়ু-প্রসূত অভিবাসন এবং অটোমেশন-প্রভাবিত শ্রমবাজারের পরিবর্তন নিয়ে মেশিন লার্নিং-ভিত্তিক পূর্বাভাস নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আগামী দশকে গ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষের ঢল কীভাবে পরিবর্তিত হবে, উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু বাস্তুচ্যুতি সামাজিক বন্ধনকে কীভাবে প্রভাবিত করবে বা যুব বেকারত্ব কীভাবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে প্রভাব ফেলবে—এসব বিষয়ে এআই-চালিত পূর্বাভাস সমাজবিজ্ঞানী এবং সরকার উভয়ের জন্যই মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
প্রযুক্তিগত এই অগ্রগতির পাশাপাশি রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক চ্যালেঞ্জ, যা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।
১. তথ্যের গোপনীয়তা ও সম্মতি: তথ্যের গোপনীয়তা অন্যতম বড় উদ্বেগ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা মোবাইল নেটওয়ার্ক থেকে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রায়শই মানুষের সম্মতি ছাড়া হয়, যা নৈতিকতা ও মানবাধিকারের জন্য বড় হুমকি। বাংলাদেশে যেখানে ডিজিটাল সাক্ষরতা সমানভাবে বিস্তৃত নয় এবং ডেটা সুরক্ষার আইনগত কাঠামো এখনো শক্তিশালী নয়, সেখানে এই ঝুঁকি আরও বাড়তে পারে। সুতরাং, সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় এআই ব্যবহার করতে হলে স্বচ্ছ সম্মতি, ডেটা সুরক্ষা ও ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
২. অ্যালগরিদমিক পক্ষপাত: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেসব তথ্যের উপর প্রশিক্ষিত হয় তা যদি সামাজিক বৈষম্য বা ঐতিহাসিক পক্ষপাত বহন করে, তবে ফলাফলও সেই পক্ষপাতকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে শ্রেণি, লিঙ্গ ও ভৌগোলিক বৈষম্য সুস্পষ্ট, সেখানে পক্ষপাতদুষ্ট ডেটাসেট ব্যবহার করলে গবেষণার ফলাফল সমাজের দুর্বল গোষ্ঠীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, পক্ষপাতপূর্ণ অপরাধতথ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত প্রেডিক্টিভ পুলিশিং টুল কোনো কোনো এলাকা বা সম্প্রদায়কে অন্যায্যভাবে টার্গেট করতে পারে। তাই সমাজবিজ্ঞানীদের উচিত এআই-ভিত্তিক বিশ্লেষণের ফলাফলকে সমালোচনামূলকভাবে যাচাই করা ও ন্যায্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা।
এআই সমাজবিজ্ঞানকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করছে এবং পদ্ধতিগত দিক থেকেও চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে।
১. গুণগত গবেষণার গুরুত্ব: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তথ্যের বিপুল ভাণ্ডার বিশ্লেষণে দক্ষ হলেও এটি প্রায়শই গুণগত (qualitative) গবেষণার সূক্ষ্মতা ধরতে পারে না। বাংলাদেশে অনেক ক্ষেত্রেই সামাজিক আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনানুষ্ঠানিক কাঠামো ও সামাজিক রীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে শুধুমাত্র ডেটা-নির্ভর বিশ্লেষণ প্রায়শই প্রকৃত সামাজিক বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করতে পারে না। তাই ভবিষ্যতের সমাজবিজ্ঞান হবে একধরনের সমন্বিত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে, যেখানে এআই-চালিত বিশ্লেষণকে গুণগত পদ্ধতির সঙ্গে একত্রিত করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, নারী নির্যাতন নিয়ে অনলাইন আলোচনার এআই-ভিত্তিক বিশ্লেষণ যদি ভুক্তভোগীদের জীবনকথা ও মানবাধিকার কর্মীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তবে ফলাফল হবে অনেক বেশি গভীর ও কার্যকর।
২. অবকাঠামোগত এবং দক্ষতাগত চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশে এআই-চালিত সমাজ গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, দক্ষতা ও নির্ভরযোগ্য ডেটা এখনো সমানভাবে বিতরণ হয়নি। স্থানীয় সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য এটি একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে তেমনি সুযোগও। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব, স্থানীয় ডেটা সায়েন্স প্রোগ্রাম এবং উন্মুক্ত ডেটা প্ল্যাটফর্মের বিকাশ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সঠিক নীতি সহায়তা ও গবেষণা তহবিল থাকলে বাংলাদেশ সামাজিক উন্নয়নের জন্য এআই ব্যবহারে এক অগ্রণী দেশ হতে পারে।
এআই সমাজ বিশ্লেষণে কেবল বাস্তবতা বোঝার উপায় নয়, এটি নীতিনির্ধারণেও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট চিত্র, জনসংখ্যার গতি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ভবিষ্যৎ বাস্তুচ্যুতি অঞ্চল চিহ্নিত করতে পারে, যা সময়মতো পুনর্বাসন ও অবকাঠামো পরিকল্পনায় সহায়ক। একইভাবে জনস্বাস্থ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আলোচনার ভিত্তিতে বা হাসপাতালের তথ্য বিশ্লেষণ করে মহামারি প্রাদুর্ভাবের প্রাথমিক সংকেত শনাক্ত করা সম্ভব। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে যে এআই কেবল সমাজ বোঝার উপকরণ নয়, বরং একটি সক্রিয় সামাজিক হস্তক্ষেপের মাধ্যম।
তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার গ্রহণে অন্ধ আশাবাদ নয়, বরং সমালোচনামূলক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি জরুরি। অ্যালগরিদম কে নিয়ন্ত্রণ করছে? এর ফলাফল কার স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে? কারা ডেটাসেট থেকে বাদ পড়ছে? বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে প্রযুক্তি গ্রহণ প্রায়শই রাজনৈতিক অর্থনীতি ও শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে পরিচালিত হয়, এই প্রশ্নগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সমাজবিজ্ঞান ও এআই-এর সংযোগকে গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা, ডিজিটাল অধিকার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের বৃহত্তর লড়াইয়ের অংশ হিসেবেই দেখতে হবে।
এআই সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামোকেও নতুন পথে নিয়ে যাচ্ছে। জটিল, অরৈখিক সামাজিক আচরণ মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে দৃশ্যমান হওয়ায় তত্ত্ব নির্মাণে নতুন ধারণা যেমন উদীয়মান আচরণ, স্ব-সংগঠন বা অ্যালগরিদমিক প্রভাব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই ধারণাগুলো ছাত্র আন্দোলনের দ্রুত সংগঠিত হওয়া, ডিজিটাল সংস্কৃতির ভাইরাল বিস্তার বা মোবাইল ব্যাংকিং ও ই-কমার্সের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর ব্যাখ্যায় সহায়তা করতে পারে।
প্রশ্ন হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমাজবিজ্ঞানের জন্য আশীর্বাদ হবে নাকি বৈষম্যকে আরও গভীর করবে? এটি কি মানুষের জীবনকে ডেটা পয়েন্টে সীমাবদ্ধ করবে, নাকি নতুন আলোয় আলোকিত করবে? বাংলাদেশের জন্য উত্তর নির্ভর করছে আমরা কীভাবে এআই ব্যবহার করি তার ওপর। যদি এটি স্থানীয় জ্ঞান, ব্যক্তিগত অধিকার ও সামাজিক ন্যায্যতার সঙ্গে সমন্বিত হয়, তবে এআই হবে এক শক্তিশালী হাতিয়ার, যা জলবায়ু অভিবাসন, লিঙ্গ বৈষম্য, যুব বেকারত্ব বা নগরজটের মতো জটিল সমস্যাগুলোর টেকসই সমাধানে সহায়তা করবে।
বিশ্ব যত বেশি আন্তঃসংযুক্ত ও তথ্যনির্ভর হচ্ছে, সমাজবিজ্ঞানের জন্য এআই গ্রহণ এক অনিবার্য বাস্তবতা। কিন্তু এই গ্রহণ যেন প্রযুক্তিনির্ভর শাসনব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ না হয়ে মানুষের কল্যাণকেন্দ্রিক অনুসন্ধান ও রূপান্তরের হাতিয়ার হয়—এটাই হবে ভবিষ্যৎ সমাজবিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।
লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী