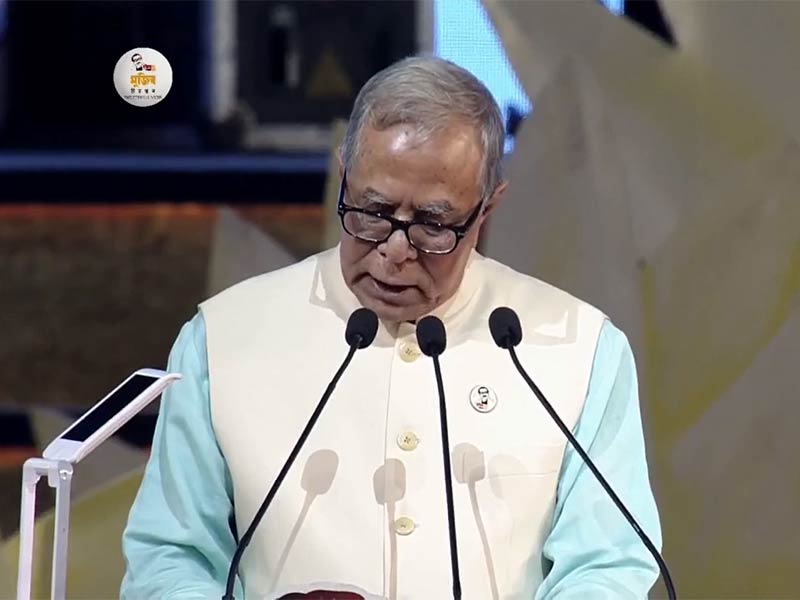১৯৭১ সালের মার্চ মাস। আমি তখন ৮ম শ্রেণীতে পড়ি। বয়স ও শারীরিক গঠনের কারণে কেউই আমাকে যুদ্ধে যাওয়ার উৎসাহ দিত না। ‘যুদ্ধে যাবার এখন শ্রেষ্ঠ সময়’ এ বিষয়টি মনে মনে অনেক বেশি উপলব্ধি করলেও, যুদ্ধের ভয়াবহতা বা যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও যে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পারি এমন উপলব্ধি তখনও হয়নি। কিন্তু যুদ্ধের প্রাকপ্রস্তুতি হিসেবে অস্ত্রের প্রশিক্ষণের যে বিকল্প নেই তা খুব সহজেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর সেজন্যই ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য তালিকাভুক্তির প্রাণপণ চেষ্টা করতে শুরু করলাম। কিন্তু কোনোভাবেই তালিকাভুক্ত হতে পারছি না। যেখানেই যাচ্ছি না কেন বয়সের ঝুঁকি মনে করে কেউই আমাকে সঙ্গে নিতে চাচ্ছে না। সবার এক কথা, আমার যুদ্ধে যাওয়ার বয়স হয়নি।
মন থেকে কিছু চাইলে তা মানুষ অবশ্যই পায়। সে সুযোগও আমার এসে গেল। মামা ও গ্রামের কয়েকজন কলেজ ছাত্র মিলে ভারতে যাওয়ার একটি দলগঠন করলেন। লুকিয়ে সে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করলাম। সময়টা ছিল জুলাই-আগস্ট, ১৯৭১। সিদ্ধান্ত হয়েছে নৌকা পথে মানকিয়ার চর বর্ডার হয়ে ভারতে প্রবেশ করবে দলটি। এরমধ্যে বড় একটা নৌকাও ভাড়া হয়েছে। নৌকাটির পেছনের অংশে পাটাতনের নিচে অনেকটা বড় খালি জায়গা। আমার মতো ছোট আকারের দেহ সহজেই পাটাতনের নিচে লুকিয়ে রাখা যায়। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে সেই জায়গাটিতে লুকিয়ে আমিও রওনা হলাম ভারতের উদ্দেশ্যে।
পাটাতনের নিচ থেকেই বুঝতে পারলাম, প্রবল বাতাসে ঝড়ের বেগে চলছে নৌকা। নদীপথে বাঙালিদের ভারতে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার খবর এরইমধ্যে পাকিস্তানি আর্মিরা আঁচ করতে পেরেছে। তাই নদীপথও সেসময় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বাহাদুরাবাদ ঘাট অতিক্রম করতে গিয়ে অনেকেরই সলিল সমাধি হয়েছে। সার্চ লাইটের মাধ্যমে পাকিস্তানি আর্মিরা নৌকার গতিপথ পর্যবেক্ষণ করতো। সন্দেহ হলে নৌকা ডুবিয়ে দিতো। কখনও কখনও ব্রাশ ফায়ার করতো। একদিন রাত তিনটায় হঠাৎ শুনতে পেলাম আল্লাহু আকবর ধ্বনি। বুঝতে পারলাম বাহাদুরাবাদ ঘাট অতিক্রম করেছি।
সবার জীবন বেঁচে গেছে। দীর্ঘ সময় পাটাতনের নিচে নিজেকে কোনোরকমে আটকে রাখা আমি বীরদর্পে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সবার অবাক আর আশ্চর্য দৃষ্টি, কিভাবে তাদের সঙ্গী হলাম! অনেকেই এমন সাহসী পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন। কিন্তু মামা খুব মন খারাপ করলেন। কারণ যুদ্ধ করার জন্য আমার শারীরিক যোগ্যতা নিয়ে তিনি খুবই সন্দিহান ছিলেন।
যাহোক, অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বাংলাদেশ সংলগ্ন ভারতের আসাম রাজ্যের মানকিয়ার চর বর্ডারে। সেখানে শুধু মানুষ আর মানুষ। বাংলাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দু শরণার্থীরাও আসছে। রাস্তার দু’পাশে তাঁবুর ভিতরে তাদের থাকার জায়গা। বৃষ্টিতে তাঁবুর ভেতর কাঁদা পানি, যা থাকার অযোগ্য। এমন করুণ দৃশ্য যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো মরনটিলা/ময়নটিলা ক্যাম্পে। মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণের যোগ্যতা নির্ধারণে এটি প্রাথমিক যাচাই বাছাইয়ের স্থান। টিলার উচ্চতা এতো বেশি যে, একবার সমতলে নামলে উপরে উঠার সাহস হারিয়ে যায়। যাচাই বাছাইয়ের সময়েও আবার একই বিপত্তি। অল্প বয়স এবং হালকা, পাতলা শরীর যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। বিচারকদের এমন ধারণা হলেও বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো অসম্ভব হওয়ায় সবার অনুরোধে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলো। সেখান থেকে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ভারতের দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ির পানিঘাটা ট্রেনিং ক্যাম্পে। কখনও স্থলপথে কখনও আবার জলপথে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে উপস্থিত হলাম সেখানে।
ক্যাম্পটি ছিল ৭ নম্বর সেক্টরের আওতাধীন। ক্যাম্পে সারিবদ্ধভাবে তাঁবু। ভেতরে খেজুরের পাটির ওপর কম্বলের বিছানা। প্রতিটিতে পাঁচ থেকে সাতজনের থাকার ব্যবস্থা। কোম্পানিতে বিভক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বর্ণক্রমে কোম্পানিগুলোর নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, এ ‘আলফা’ ‘বি’ ‘বেটা’ ‘সি’ কে ‘চার্লি’ ইত্যাদি। আমি অন্তর্ভুক্ত হলাম ‘এল’ বা ‘লিমা’ কোম্পানিতে। কোম্পানি পেয়ে লাইনে দাঁড়ালাম।
প্রত্যেককে দেওয়া হলো দু’টি গেঞ্জি, দু’টি হাফপ্যান্ট, দু’টি গামছা অর্থাৎ জোড়া জোড়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এসবই বিভিন্ন দেশ থেকে পাঠানো অসম আকৃতির। কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত গেঞ্জি, হাফপ্যান্টের এক পাতে দু’পা চলে যেতো। হাফপ্যান্টের হুকের মধ্যে গামছা ঢুকিয়ে কোমর বেঁধে রাখতাম আর নিচের অংশে পায়ের গোড়ালি ছুঁই ছুঁই করতো।
জনবসতিহীন পাহাড়ি এলাকা হওয়ায় ক্যাম্পের বাইরে দল ছাড়া একা চলাফেরা নিষেধ। অন্যদেশ থেকে আসা সাহায্যে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা হতো। তবে সেখানকার তাজা চা পাতার গন্ধ এখনও ভোলা যায় না। নাস্তা ও দুপুরের খাবারের জন্য খুব অল্প সময় বরাদ্দ থাকতো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাবার শেষ না হলেও সে অবস্থাতেই প্রশিক্ষণে উপস্থিত হতে হতো।
সকাল শুরু হতো পিটি দিয়ে। এরমধ্যে অন্যতম ছিল বল খেলা। ২০০ জনকে দু’টি দলে ভাগ করে খেলা হতো। যে দল হারবে তাদের প্রত্যেককে বিজয়ী দলের একজনকে কাঁধে করে ক্যাম্পে নিয়ে যেতে হতো। মজার বিষয় হলো, হার জিত যাই হোক না কেন, শারীরিকভাবে পাতলা এবং ছোট গড়ন হওয়ায় প্রতিবারই অন্যের কাঁধে ওঠে ক্যাম্পে যেতাম। এরপর নাস্তা খেয়ে দৌড় দিতাম প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং এর জন্য। প্রশিক্ষক ছিলেন ভারতের অভিজ্ঞ শিখ ও গারো সৈনিকেরা। তাদের আমরা ‘ওস্তাদ’ বলে সম্বোধন করতাম। রাইফেল, এসএমজি (স্টেনগান) এলএমজি এবং অন্যান্য সমমানের অস্ত্র সম্পর্কে বাস্তব এবং তাত্ত্বিক ট্রেনিং হতো। রাতের অন্ধকারে অস্ত্রের যন্ত্রাংশ খুলে আবার তা আগের মতো সাজানো সত্যি খুব জটিল ছিল। মাইন, গ্রেনেড, এক্সপ্লোসিভ ইত্যাদি ব্যবহারের যথাযথ জ্ঞান অর্জনে রীতিমত ক্লাস করতে হতো। স্বল্পসময় প্রশিক্ষণ নিয়ে বিশ্বের শক্তিশালী সেনাবাহিনী হিসেবে সুপরিচিত পাকিস্তানি আর্মিদের চ্যালেঞ্জ দেওয়া এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা মোকাবিলা করা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অবশ্যই খুব সাহসের বিষয় ছিল।
প্রশিক্ষকরা বেশিরভাগই হিন্দি ভাষায় কথা বলতেন। অল্পস্বল্প ইংরেজির ব্যবহার ছিল। প্রথমদিকে হিন্দি ভাষা না বোঝার কারণে কাজে ভুল হতো। সেজন্য ওস্তাদের চড়-থাপ্পড় লাথিও খেতে হয়েছে। পরে অবশ্য হিন্দি ভাষা বুঝতে পারা এবং বলা দুটোতেই পারদর্শী হয়েছিলাম। মজার বিষয় হলো, হঠাৎ একদিন এক বাঙালি অনুবাদককে দেখলাম কান ধরে বার বার উঠবস করছেন। তারপর বুকডন ও ক্রলিং। আমরা সকলে বিস্মিত! ব্যাপার কী? পরে জানতে পারলাম প্রশিক্ষক যা বলেছেন বাঙালি অনুবাদক ভুল অনুবাদ করায় আমরা অন্যভাবে রেসপন্ড করেছি। বয়স কম হওয়ায় কখনও কোনো ধরনের সুবিধা পাইনি। সবার মতো পারদর্শিতা না দেখাতে পারলে পেতে হতো শাস্তি।
একসময় প্রশিক্ষণ শেষ হলো। একেকজনের জন্য বরাদ্দ হলো ফ্রিডম ফাইটার নম্বর (এফ এফ নং)। রওনা হলাম তরঙ্গপুর ক্যান্টনমেন্টের উদ্দেশ্যে যেখান থেকে আমাদের প্রত্যেকের নামে অস্ত্রের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আবার মুক্তিযোদ্ধার উপস্থিতির কারণে প্রয়োজনীয় খাবার, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ অপ্রতুল ছিল। কলাপাতায় খাবার খেতাম। আর সেটি না পেলে কলাগাছের ডোঙ্গা খেতাম। কখনও আবার আখের রস জ্বাল দেওয়ার কড়াইয়ে ২০/২৫ জনের ভাত ও তরকারি একসঙ্গে মেশানো থাকতো। সেখানে আবার পা রাখারও জায়গা থাকতো। আমরা কড়াইয়ের মধ্যে ওঠে খেতাম। শেষ হলে নেমে আসতাম। একইভাবে অন্যরা খাবার খেতো।
মানকিয়ার চর হয়ে নদীপথে এবার এলাম নিজ জেলা সিরাজগঞ্জে। থাকার জন্য প্রথম আস্তানা হলো যোগাযোগবিহীন একটি চর এলাকায়। কখনও গোয়ালঘরে খড় বিছিয়ে কখনও খোদ গৃহস্থের শোয়ার ঘরে রাত্রি যাপন করতাম। খুব ঘনঘন স্থান পরিবর্তন করতাম, যাতে শত্রু বাহিনী আমাদের অবস্থান জানতে না পারে। এতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করার পরও রাজাকার আল বদরের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বিমানবাহিনী আমাদের নৌকা লক্ষ্য করে একদিন গুলি করে। লক্ষ্যভ্রষ্টের কারণে সে যাত্রায় আমরা বেঁচে যাই।
নভেম্বর মাস চলে আসলো। পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা তিনটি দলে ভাগ হয়ে তিন দিক থেকে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর থানা সদরে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করি। থানার পশ্চিম দিক থেকে গ্রুপ কমান্ডার মো. আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নেই। সব গ্রুপের সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন মো. লুৎফর রহমান। আমরা খোলা মাঠে অবস্থান নিয়ে ক্রলিং করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে অগ্রসর হতে থাকি। সংরক্ষিত বাঙ্কার থেকে পাকিস্তান বাহিনী আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। এতে সহযোদ্ধা চাঁন মিয়া নিহত এবং মো. আমজাদ হোসেন ও আবুল কাসেম গুলিবিদ্ধ হন। সারাদিনব্যাপী যুদ্ধ চলে। একসময় গোলাবারুদ ফুরিয়ে আসে। ফলে শেষ চেষ্টা করেও থানা দখলমুক্ত করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সুরক্ষিত বাঙ্কারে অবস্থানের কারণে যুদ্ধে ততটা সফলতা আসেনি। তবে পাকিস্তানিরা বুঝতে পেরেছিল মুক্তিযোদ্ধারা তাদের ঘিরে ফেলেছে। তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী সময়ে বিশেষ পাহারায় পর্যায়ক্রমে জেলা সদরে পালিয়ে যায়।
ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সিরাজগঞ্জ শহরের অদূরে শৈলমারী-ভাটপিয়ার নামক স্থানে আরও একটি ভয়াবহ যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। সেখানেও সকাল থেকে যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে সোহরাবসহ কয়েকজনের প্রাণ যায়। জনাব আমির হোসেন ভুলু সে সময় সিরাজগঞ্জের মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন।
ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ মুক্ত হয় সিরাজগঞ্জ শহর। দীর্ঘ সংগ্রাম ও নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর আসে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, লাল সবুজের বাংলাদেশ। বিজয় পরবর্তী কিছুদিন কাটলো জেলা সদরের মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে। অতঃপর বাংলাদেশ ও ভারতের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত যৌথ বাহিনীর নিকট সিরাজগঞ্জ মিলিশিয়া ক্যাম্পে অস্ত্র জমা দিয়ে রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। বিদায় লগ্নে সহযোদ্ধা এস এম তরিকুল ইসলাম, আবদুর রশীদ, আমজাদ হোসেন, সুজাবত আলী, আমিরুল, হাবিবুর, ওহাব, তোফাজ্জলসহ অনেকের চোখ ছলছল করছিল। একই গ্রামের অধিবাসী ও সহযোদ্ধা আব্দুস সামাদ, আবুল কাসেম, আজিজুর ও মামা সামসুল হক একযোগে বাড়ি পৌঁছলাম। গ্রামের অনেক লোকই আমাকে দেখতে আসলো। কিশোর বয়সের সাহসিকতা ও বীরত্বের জন্য তাদের ভালোবাসা ও প্রশংসা পেলাম। জীবনের শেষ লগ্নে এসে স্বাধীনতার সূর্বণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মবার্ষিকীতে মনে পড়ছে সেইসব সহযোদ্ধাদের। কবির ভাষায় বলি… ‘কোথা লিখি রাখি এত প্রিয় নাম, একদা যারা পাশাপাশি ছিলাম’।