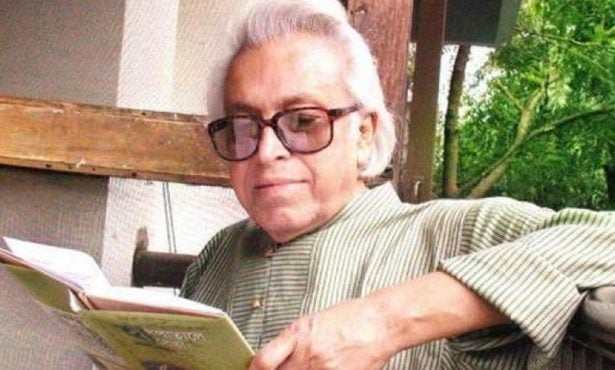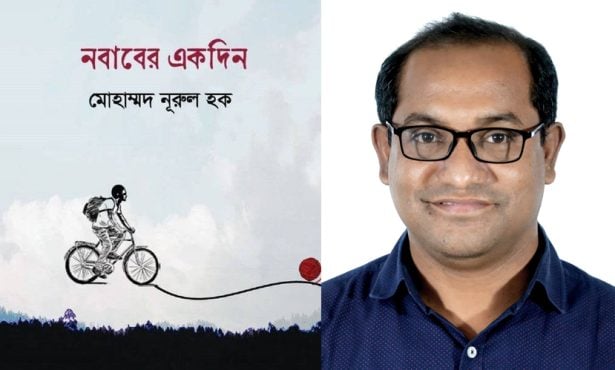একাত্তরের নৃশংসতার খণ্ডচিত্র
২০ এপ্রিল ২০২৩ ১৩:৫৫
সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী কিংবা মিত্র বাহিনীর সদস্যই নয়, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতিপক্ষ ছিল গোটা বাঙালি জাতি। সশস্ত্র যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তারা যেমন যুদ্ধ করেছে তেমনি সাধারণ মানুষকেও প্রতিপক্ষ ভেবে নৃশংসভাবে খুন করেছে। তাদের বাড়িঘর লুট ও আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে এভাবে সাধারণ মানুষকে খুন করার উদাহরণ খুবই কম। একটা গোটা জাতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার মানসে চালিত এই যুদ্ধকে পুরোপুরিই গণহত্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। অন্যদিকে একটা জনগোষ্ঠীর সবাই যখন প্রতিবাদি হয়ে ওঠে আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হয় তখন তাকে প্রচলিত অর্থের যুদ্ধ না বলে জনযুদ্ধ হিসেবেই আখ্যায়িত করতে হয়। কী নৃশংসতা তারা চালিয়েছে সারা বাংলাদেশে? বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কয়েকটি গ্রামের খুনের কিছু তথ্য থেকে অনুমান করা যাবে কী পরিমাণ মানুষকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে।
সিদ্দিকুর পাটক্ষেতে লুকিয়ে দেখেন পাকিস্তানিরা বেয়নেট খুঁচিয়ে মারছে প্রিয়জনদের _
কুমিল্লা-আখাউড়া জেলা পরিষদ সড়কের আকসিনা নামে ছোট সুন্দর একটি গ্রাম। প্রধান সড়ক থেকে পশ্চিমে কিছুদূর গেলেই মসজিদ। পশ্চিমপাশে পুকুর। পুকুরের পশ্চিমদিক ঝোপঝাড়ে ভরা। ঝোপের উত্তরে সাজানো একটি বাড়ি।
ওই পুকুরপাড় একাত্তরে রক্তাক্ত হয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে। পুকুরের উত্তর-পশ্চিমে মেম্বারের বাড়ির সিঁড়িতে কথা হয় কুল্লাবাড়ির সিদ্দিকুর রহমানের সঙ্গে। একাত্তরে ছিলেন টগবগে তরুণ। কত হবে বয়স ১৯/২০। ক্ষেতে খামারে কাজ করেন। পাকিস্তানি বাহিনীর খোঁজখবর নেন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে আগে থেকেই। চারিদিক থেকে শুধু দুঃসংবাদ আসে। আজ এই গ্রামে এত জন কাল ওই গ্রামে এতজনকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি বাহিনী। গ্রামের সবাই আতঙ্কের মধ্যে আছে। তাদের গ্রামে না জানি কবে হামলে করে হানাদার বাহিনী। চূড়ান্ত অনিশ্চিত একটা অবস্থায় দিন যায়।
এমন অবস্থায় বৈশাখ মাসের ১৫ থেকে ২০ তারিখ হবে। মানুষজন সকালের খাবার খেয়ে ক্ষেতে-খামারে যাবে। দৈনন্দিন কাজ করবে। এমন সময় শোনা যায় মানুষের চিৎকার। পাঞ্জাবি আইয়েরে। ছিদ্দিকুর রহমান তখন ছিলেন মন্নাফ কন্ট্রাক্টরের বাড়ির সামনে। দেখেন বাঁচার উপায় নেই। উত্তর দিক থেকে পাকিস্তানিরা আসছে। তিনি দক্ষিণে যেতে থাকেন। কিছুদূর যেতেই দেখেন পূর্বদিক থেকেও আসছে। পুকুরের কোণা পর্যন্ত আসতেই ধরা পড়ে যান পাকিস্তানিদের হাতে। গাঙকুলের সোনা মিয়া বুদ্ধি করে লম্বা করে ওদের সালাম জানায়। বাকিরা একে একে ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং সালাম জানায়। একে একে সবাই হাত মিলায়। বলে হামারা মুসলমান তোমারা মুসলমান তোমহারা হামার ভাই লাগতা হ্যায়। সালামের জবাব দিলেও বিনিময়ে শুরু হয় রাইফেলের বাট দিয়ে পেটানো। কিল-ঘুষি। লাথি দিতে থাকে পাষণ্ডের মতো। ছিদ্দিক বুঝতে পারেন এবার আর রক্ষা নেই। ওর সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশি কয়েকজনও ধরা পড়ে। অনেক আকুতি মিনতি করার পারও তাদের ছাড়া হয় না। নিয়ে যাওয়া হয় পুকুরের পশ্চিমপাড়ে-এখন যেখানে ঝোপঝাড়ে ভরা সেই জায়গটায়। বাড়ি থেকে সমান্য উচু পুকুরপাড়। সেখানে উত্তরে দক্ষিণে লাইন করে দাঁড় করানো হয় তাদের।
২০২২ সালের নভেম্বর মাসে যখন কথা হয়, সিদ্দিকুর রহমান বয়সের ভারে নুহ্য। কথা বলতে পারছিলেন না স্পষ্ট। কিছুটা দাঁড়িয়ে শুনছিলেন মোকাদ্দাস ভুঁইয়া। এগিয়ে আসেন তিনি। যে পুকুরপাড়ে ওদের দাঁড় করানো হয়েছিল ওই পুকুরের দক্ষিণপাড়ে তাদের বাড়ি। ঘরের ভিতর থেকেই দেখা যায় উত্তর ও পশ্চিমের অনেকটা। বললেন, তিনি দেখছিলেন পুরো ঘটনা। বললেন, উত্তর দিক থেকে প্রথমে আসে ৪/৫জন পাকিস্তানি সৈন্য। অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্বদিক থেকে আরও আসে অন্তত ১০/১২জন। পূর্বদিক থেকে আসা সৈন্যগুলো ছিল অধিক উগ্র। ওদের এগিয়ে যাওয়া দেখেই ভয় পাচ্ছিলেন মোকাদ্দাস। দ্রুত তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পুকুরপাড়েই একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে যান। তাকিয়ে থাকেন পুকুরের পশ্চিম পাড়ের দিকে। দেখেন, পুকুরের পশ্চিমপাড়ে সিদ্দিকুর রহমান ছাড়াও হুমায়ূন, মালু, জজু, মোশকত আলী, আজীজ, জলিল, আরু মিয়া, ইউনুস ও গাঙকুলের সোনা মিয়াকে দাঁড় করানো হয়েছে। এলপাতারি বেয়নেট চার্জ শুরু করে পাকিস্তানিরা। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে একেকজনের শরীর থেকে। সিদ্দিকুর রহমান ছিলেন সর্বদক্ষিণে। শেষ চেষ্টা হিসেবে পশ্চিম দিকে ডোবায় দিলেন ঝাপ। পানিতে পড়েই তিনি পাট পঁচানোর স্তুপের আড়ালে চলে যান। সেখান থেকে পাটক্ষেতে ঢুকে একবারে পশ্চিমে। তার সঙ্গে সঙ্গে কাদির মিয়া ও মালু মুহুরীও পূর্বদিকে পুকুরে ঝাপ দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পানিতে ডুব দিয়ে থাকার পর ভেসে উঠেন অক্সিজেন নিতে। নজরে পড়ে যান পাকিস্তানিদের। পানিতেই ওদের গুলো করা হয়। রক্তে লাল হয়ে যায় পুকুরের পানি। এদিকে পুকুরের পাড়ে যাদের বেয়নেট চার্জ করা হচ্ছিল তাদেরও গুলো করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।
মোকাদ্দাস ভুঁইয়া ও সিদ্দিকুর রহমান ওই নৃশংসতায় মৃতদের নাম নিশ্চিত করেন একমত হয়ে। আইএ পরীক্ষার্থী হুমায়ুন, পঞ্চাশোর্ধ বয়সের জজু মিয়া, মালু মিয়া, আব্দুল আজিজ, মোশকত আলী, আব্দুল জলিল, বারু মিয়ার ভাই আরু মিয়া, গাঙকুলের সোনা মিয়া, ইউনুস মিয়া, ও ঈদন মিয়ার কথা। ঈদন মিয়া লাইন থেকে বেরিয়ে গিয়ে দৌড় দিয়েছিলেন, ওই অবস্থায়ই তাকে গুলো করে হত্যা করে।
পাকিস্তানি সৈন্যরা মানুষগুলোকে খুন করে দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে। সামনেই ধরা পড়েন মোকাদ্দাস ভুঁইয়ার বাবা লাল মিয়া ভুঁইয়া ও জোরালী হাজীকে ধরে ফেলে। ২জন রাজাকার ওদের বলে, তোমাদের মারা হবে না। তোমরা নৌকার ব্যবস্থা করে দাও। কাছেই নৌকা ছিল। এনে দিতেই তাদের বলা হয়, পানিয়ারুপ নিয়ে যেতে। বাধ্য হয়ে তারা পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে রওনা হয় পানিয়ারুপ। তাদের ভাবনায় ছিল, তাদের ভাগ্যেও হয়তো বুলেটের আঘাতই আছে। কিন্তু সৈন্যরা ওদের গুলো না করে পানিয়ারুপ গিয়ে ছেড়ে দেয় এবং বলে, এই নৌকা দুটি তোমাদের দিয়ে গেলাম।
পরে তারা জানতে পারেন এই হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিল টি আলীর বাড়িতে থাকা দুই রাজাকার। তাদের বাড়িও আশেপাশের গ্রামের। কিন্তু উপস্থিত কেউই তাদের নাম বলতে রাজী হলেন না। তবে এটা জানালেন, ওই রাজাকাররা পাকিস্তানি সৈন্যদের বলেছিল গ্রামের দিলু মেম্বারের বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি করেছে। অন্য রাজাকার দুইজন পাকিস্তানি বাহিনীকে গ্রামে নিয়ে এলেও ভুল করে তারা দিলু মেম্বরের বাড়ির পরিবর্তে নুরুল ইসলাম মেম্বারের বাড়ির সামনেই এই খুনের ঘটনা ঘটিয়েছে।
তাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ওই গ্রামে কি আর কোনও ঘটনা ঘটায়নি? ভুলে গিয়েছেন বলার পরও একজন বললেন, ও হ্যাঁ আরেকটা ঘটনা আছে। ওই ঘটনার ১৫/২০দিন পর এটা। ওইভাবেই হঠাৎ পাকিস্তানিরা চলে আসে গ্রামে। স্থানীয় রাজাকাররা নাকি খবর দিয়েছে, এখানে মুক্তিবাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করেছে। ওরা এসেই পুরো গ্রামের কয়েক শ মানুষকে বন্দী করে। সবাইকে নিয়ে যায় স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলে। হিন্দু মুসলমান পরখ করে তাদের। মহিলাদের নিয়ে যাওয়া হয় অন্য কক্ষে। মহিলাদের নির্যাতন করেছে কি না, এই প্রশ্নের জবাব দেননি তারা।
এরমধ্যে আরেক ঘটনা ঘটায় পাকিস্তানিরা। পাকিস্তানি একজনের নাম ছিল ইকবাল। সে মোল্লাপাড়ার এক মেয়েকে বিয়ে করে। ঈদন সর্দারের বাড়ির সেই মেয়ের কাছে পাকিস্তানি সৈন্য টি আলীর বাড়ি থেকে আসত। আবার চলে যেত। অনেক লুটের সামগ্রি সে ওই মেয়েকে উপহার দিয়েছে। আর গ্রামে এসে পরিস্থিতি অবলোকন করত। খবর দিত তার বাহিনীকে। সেই অনুযায়ী তারা অপারেশন চালাতো।
এরবাইরেও রাস্তায় ফেলে অনেককে হত্যা করেছে পাকিস্তানিরা। তবে কসবা টি আলীর বাড়ির পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প থেকে এসে মাঝে মাঝেই ওরা গ্রামের মানুষকে খুন করত। তরকারি থেকে শুরু করে হাঁস-মুরগি, গরু ছাগল নিয়ে যেত গৃহস্ত বাড়ি থেকে। এসব কাজেসহযোগিতা করত স্থানীয় রাজাকাররা।
প্রিয়জনদের বেয়নেট খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারে পাকিস্তানি সৈন্যরা বাঁশঝাড় থেকে দেখেন বিজয়_
রাউৎ হাট পুরোটাই হিন্দু বসতি। আনুমানিক ৬০০ পরিবারের বাস। কসবা থেকে সামান্য দূরে অবস্থান। অকল্পনীয় ঘনবসতি। ঋষিপাড়া নামেও অনেকে চিনে। কথা হয় রাউৎ হাটের বিজয় ঋষির সঙ্গে।
বললেন, একাত্তরে তার সামনে ঘটে যাওয়া নৃশংসতার কথা। রাউৎ হাট এ সুন্দর দুর্গা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে কথা বলার সময় পাড়ার ছেলে বুড়ো প্রায় ২৫/৩০জন জমা হয়ে যায় মন্দিরের সামনে। প্রত্যেকেরই নিকটজন ছিল একাত্তরের শহিদেরা।
বিজয় ঋষিই বলছিলেন সেদিনের কথা। তখন তার বয়স ছিল ১৭ বছর। বেশ টগবগে তরুণই বলা যায়। সময়টা ছিল বৈশাখের মাঝামাঝি। যতটা মনে আসে শুক্রবার ছিল সেদিন। দেখেন আড়াইবাড়ির দুইজন হুজুর এগিয়ে আসছে তাদের বাড়ি থেকে। সন্দেহ থাকার পরও মনে করলেন, তারা তো আমাদের এলাকারই মানুষ। কী আর হবে। কিন্তু এক দুই মিনিটও যায়নি। দেখেন তাদের পেছনে আসছে পাকিস্তানি সৈন্যদের কয়েকজন। কানে বাজে গ্রামের ভিতর থেকে চিৎকার। পাঞ্জাবি আইয়েরে। চোখে পড়ে মানুষজন দৌড়ে পালাচ্ছে। যে যেদিকে পারে দৌড়াচ্ছে। কিন্তু ধরা পড়ে যায় কয়েকজন। তাদের নিয়ে যায় হাজিপুর স্কুলে। লাইন ধরে দাঁড় করানো হয়। জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা কি মুসলমান।
আসলে পাকিস্তানি সৈন্যদের কথা তো আর কেউ বুঝে না। পেটাতে থাকে বেধরক। এরপর লাইন ধরানো হয় সবাইকে। বলে লুঙ্গি খুলে ফেলো। লুঙ্গি খুলে সিদ্ধান্ত নেয় কে মুসলমান আর কে হিন্দু। হিন্দুদের সবাইকে আলাদা করা হয়। মোট ১৩জনকে পশ্চিম দিকে নিয়ে যায় রাইফেলের বাট দিয়ে লাঠি দিয়ে পিটাতে পিটাতে।
পাকিস্তানিরা কাছাকাছি হওয়ার আগেই বিজয় দেয় দৌড় দক্ষিণ দিকে। সোজা গিয়ে বাঁশঝাড়ের ভিতর লুকিয়ে পড়ে। তাকিয়ে দেখে পেছনে। হায়রে কী নৃশংস দৃশ্য। একেকটি মানুষকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মাটিতে ফেলে দিচ্ছে। একেকটি খোঁচার পর ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।
একবারে সামনের দিকে ছিল বিজয়ের বাবা শুক্র চন্দ্র ঋষি। অবস্থা খারাপ দেখে তিনি দেন দৌড়। একটা সৈন্য তার বাবাকে লক্ষ্য করে গুলো চালায়। দৌড়ানোর সময়ই মাটিতে পড়ে যায় বিজয়ের বাবা। বিজয় এর আগেই ঘন বাঁশঝাড়ের ভিতর মোটা একটা বাঁশ বেয়ে উপরে গিয়ে বসেছিলেন। আর দেখছিলেন পলায়নরত তার বাবাকে কিভাবে একটা সৈন্য গুলো করে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। একে একে ১৪জনকে হত্যা করে ওই পশুরা। মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য সবাইকে আবার গুলো করে। যুদ্ধজয়ী সৈনিকের মতো একসময় পাকিস্তানিরা আড়াল হয়ে যায়। বিজয় ঋষি দ্রুত নেমে আসেন বাঁশঝাড় থেকে। দৌড়ে আসেন বাবার কাছে। তার উপুর হয়ে শুয়ে আছেন। তাজা রক্তে ভিজে গেছে মাটি। কী করবেন বুঝতে পারছিলেন না। বাবার নাকের কাছে হাত নিয়ে অনুভব করেন নিঃশ্বাস পরছে কি না। না নিস্তেজ দেহটা থেকে প্রাণও বেরিয়ে গেছে তার বাবার।
হাত রাখেন কাঁধে। শরীর তখনও গরম। হয়তো দুয়েক মিনিটও হয়েছে কি না সন্দেহ তার বাবা মারা গেছেন। বাবার মৃতদেহ দেখার পর তিনি নড়তে পারছিলেন না। ততক্ষণে মানিক এসে যুক্ত হয়েছেন। বড়জোড় দুই মিনিট মানিক ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে-বিজয়রে ঐ দেখ।
বিজয় তাকিয়ে দেখেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা এগিয়ে আসছে এই দিকে। মানিক আর বিজয় দৌঁড়াতে থাকেন। যতক্ষণ শরীরে কুলোয় তারা দৌড়ান। পেছনে পড়ে থাকে ১৩জনের লাশ।
মৃতদেহগুলো সৎকার করার কোনও মানুষ রইলো না পাড়ায়। দ্রুত গতিতে তারা গ্রাম ছেড়ে সোজা চলে যান ভারতে। পরবর্তী সময় আশেপাশের মুসলমানরা লাশগুলো নিয়ে যায় তাদের বাড়ির পশ্চিমে পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোনায়। বাঁশঝাড়ের নিচে মাটিচাপা দেওয়া হয় তাদের। কিসের ধর্মীয় রীতিনীতি আর কিসের কি।
ওই ঘটনায় প্রাণ হারান-
১. রাসু চন্দ্র ঋষি বাবা-দেবেন্দ্র চন্দ্র ঋষি
২. মন্টু চন্দ্র ঋষি বাবা- দেবেন্দ্র চন্দ্র ঋষি
৩. রমানাথ ঋষি বাবা- শ্রীধাম চন্দ্র ঋষি
৪. বিপীন চন্দ্র ঋষি-বাবা, পিয়ারী মোহন ঋষি
৫. রজত চন্দ্র ঋষি বাবা- রোহি দাস ঋষি
৬. হরিলাল ঋষি বাবা- বিদু ঋষি
৭. রথীন্দ্র ঋষি, বাবা-ব্রজমোহন ঋষি
৮. চক্র ঋষি বাবা- অটল ঋষি
৯. লবচন্দ্র ঋষি বাবা-রবি ঋষি
১০. রবি ঋষি- লবচন্দ্র ঋষির বাবা
১১. রাজ্যশ্বর ঋষি-বাবা- অনীল ঋষি
১২. উপেন্দ্র চন্দ্র ঋষি বাবা- প্রদীপ চন্দ্র ঋষি
১৩. ইন্দ্রমোহন ঋষি-রাখাল ঋষির দাদা।
হঠাৎ লুঙ্গি খুলে মুসলমানিত্ব চেক করা বন্ধ করে দেয়, বেঁচে যান নৃপেন্দ্র ঋষি
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবার নিকটবর্তী গ্রাম রাউৎ হাট। পুরো গ্রামের অধিবাসী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। যুদ্ধ শুরু হলেও সেখানে কিছু মানুষ থেকে যায়। কারণ ফসলের মৌসুম এটা। কিন্তু আতঙ্ক চারিদিকে। কখন যে পাকিস্তানি সৈন্যরা গ্রামে হামলা করে ঠিক নেই। পাকিস্তানি সৈন্যরা তখন কসবা টিআলীর বাড়িতে অবস্থান করছিল। টি আলী ছিলেন মুসলিম লীগের নেতা এবং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বাংলাদেশ হওয়ার পর ১৯৭৫ এরপর যখন নিষিদ্ধ ঘোষিত সাম্প্রদায়িক দলগুলো রাজনৈতিক অধিকার পেলো এই টি আলীও রাজনীতি শুরু করেন। একসময় বাংলাদেশ মুসলিম লীগের সভাপতি হয়েছিলেন।
অন্যদিকে আড়াইবাড়ির পীর ছিলেন ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামি থেকে এমএনএ প্রার্থী। কাছাকাছিই দুইজনের বাড়ি। দুই বাড়িতেই রাজাকার ও পাকিস্তানি আর্মির অবস্থান। রাজাকাররা জানে এই গ্রামে শুধু হিন্দুদের বাস। সুতরাং যে কোনও মুহূর্তে তাদের ওপর হামলা হতে পারে এমন সন্দেহ সবারই ছিল। তাই রাউৎ হাট গ্রামে বলতে গেলে খুব একটা মানুষ ছিল না।
স্মৃতিচারণকারী নীখিল ঋষি বললেন, তার পরিবারও তখন ভারতে ছিলেন। শরণার্থী জীবন অনেক কষ্টের। ভাবলে বাড়িতে কিছু গম আছে, সেগুলো আনতে পারলে কিছুটা খাদ্য চাহিদা পূরণ হতো। নৃপেণ ঋষি আর নিরঞ্জন ঋষি দুই ভাই। পরামর্শ করলেন বাড়ি থেকে গমগুলো নিয়ে যাবেন ভারতে। সেই অনুযায়ী দুই ভাই বাড়ি আসেন। দ্রুত ভাড়ে গম ঢুকিয়ে ঘর থেকে বের হবেন। কিন্তু নৃপেন্দ্র ঋষি ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। ভাই নিরঞ্জন ঋষি বার বার তাগাদা দিয়েও ভাইকে বের করতে পারছিলেন না। নৃপেন তার ভাইকে বলে, তুমি যাও আমি একটু পর আসছি। নিরঞ্জন ঋষি শেষ পর্যন্ত তাকে ফেলেই গমের ভার নিয়ে ভারতে চলে যান।
এদিকে কিছুক্ষণ পরই নৃপেন্দ্র শুনতে পান-মানুষ চিৎকার করছে, পাঞ্জাবি আইয়েরে। দরজা থেকে উঁকি দেন বাইরে। হায়রে বাড়ির সামনে পাকিস্তানি আর্মি। উপায় না দেখে তিনি ঘরের শিলিং-এ উঠে যান। পাকিস্তানিরা ঘরের দরজা খোলা দেখে ঢুকে ঘরে। ঘরের এই কোনায় ওই কোনায় খোঁজ করে কোনও মানুষ আছে কিনা। না, ক্উাকে দেখতে পেলো না। একসময় দেখে শিলিং-এ মনে হয় কেউ নড়াচড়া করছে। ওমনি শিলিং- এ খোঁজ নিয়ে নৃপেন্দ্রকে ধরে ফেলে।
নিয়ে যায় বাড়ির ওপাশে যেখানে অনেককে আনা হয়েছে। এবং লাইন করা হয়, হয়তো গুলো করবে বলে। তিনিও লাইনে দাঁড়ান। তার পাশে ছিল হাজিপাড়ার কয়েকজন মুসলমান। ওই সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা বলে, তোমরা যারা হিন্দু আছো হাত ওঠাও। একে একে হিন্দু সবাই হাত উঁচিয়ে ধরে। নৃপেন্দ্রও হাত উঁচু করতে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশে থাকা হাজিপাড়ার মুসলমান একজন তার হাত চেপে ধরে। আর তিনি হাত উঁচু করতে পারেননি। যারা হাত উঁচু করেছিল তাদের আলাদা লাইন করা হল।
এরপরও পাকিস্তানিদের বিশ্বাস হয়নি। মুসলমানদের সামনে গিয়ে বলে, লুঙ্গি খুলে দেখাও। এভাবে কয়েকজনকে লুঙ্গি খুলে চেক করে আসলেই তারা মুসলমান কি না। নৃপেন্দ্রর তখন ঊর্ধশ্বাস ওঠে গেছে। এদিকে কয়েকজনের মুসলমানিত্ব চেক করার পর শুরু করে লাথি গুতো কিল ঘুষি। ইশারা করে সব ভাগো। ভাগো বলতেই নৃপেন্র দৌড় দিতে উদ্যত হয়। ওমনি একটা আর্মি এসে তাকেও কষে লাথি মারে। ঘুষি দিতে থাকে। আর বলে ভাগো এখান থেকে।
কিল ঘুষি খেয়ে নৃপেন্দ্র দৌড়াতে থাকেন। এমন জোরে দৌড়ান অল্প সময়ের মধ্যে পাকিস্তানিদের দৃষ্টি সীমার বাইরে চলে আসেন।
এক ফোঁটা পানি দিতে পারিনি মৃত্যুপথযাত্রীদের মুখে-মফিজুল মাস্টার _
সালদানদী রেল স্টেশন থেকে সামান্য উত্তরে রেলসেতু পেরিয়ে একটা সরুর রাস্তা। রাস্তা সরু হলেও নামডাক বড়। কুল্লাপথর শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের কবরস্থানকে চিহ্নিত করার জন্য এমনি এমনি রাস্তার নাম হয়ে যায় কুল্লাপাথর সড়ক। রেললাইন থেকে দুই কিলোমিটার ভেতরে একটা গ্রাম-হরিপুর। হরিপুর গ্রামের জয়নুল আবেদীনের ছেলে মফিজুল ইসলাম। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হওয়ার পর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় মাস্টার। একাত্তরে মরতে মরতে বেঁচে যাওয়া একজন মানুষ। নিজ বাড়িতে ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। সেই ক্যাম্পে পাকিস্তানি বাহিনী বোমা হামলা করে সালদানদী থেকে। সে এক ভয়ংকর চিত্র। তাই বর্ণনা করে মফিজুল মাস্টার।
পাকিস্তান আমলে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শুরু করত একটু বেশি বয়সে। সেই হিসেবে ক্লাস সেভেনের ছাত্র মফিজুল ইসলামকে ১১/১২ বছর বয়সের বলার সুযোগ নেই। তার ভাষ্যমতে হয়তো ১৪ বা বেশি হবে তার বয়স। আর বয়স যদি কমও হতো তারপরও একাত্তরের কথা তার ভুলে যাওয়ার মতো নয়। কারণ খুব কম মানুষের জীবনেই এমন নৃশংসতা দেখা সম্ভব হয়। এত আতঙ্ক, এত বিদ্রোহ একটা জাতির জীবনে দুইবার ঘটে না। কোনও কোনও জাতির জীবনে ঘটেইনি। এমন অস্বাভাবিক ঘটনা যে দেখেছে, তার সামান্য বোঝার বয়স হলেও বাকি জীবনে সেটা ভুলে যাওয়া সম্ভব হয় না। আর ঘটনার ভুক্তভোগী যদি সেই শিশু কিংবা কিশোর নিজেই হয়ে থাকে, তাহলে তো ভুলে যাওয়া সম্ভবই না। আর সেই শিশু কিংবা কিশোর ছিলেন মফিজুল ইসলাম মাস্টার।
তখন আতঙ্ক চারিদিকে। যুদ্ধ কী ভয়ংকর তাও দেখা হয়ে গেছে তার। সেই ভয়ংকর মুহূর্তে তাকে বাড়িতেই থাকতে হয়েছে বিভিন্ন কারণে। বাইরে কোথায় গিয়ে কোনও নিরাপত্তাহীনতায় পড়েন এমনই ছিল তাদের পরিবারের ভাবনা। সুতরাং বাড়ি ছাড়লেন না বাড়ির অনেকেই। রয়ে গেলেন মফিজুল ইসলামের পরিবারও। যদিও তাদের বাড়ির সামনে দিয়েই হাজার হাজার মানুষ ভারতে গিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে।
চরম একটা অনিশ্চয়তা চলছে তখন তাদের। একেবারে সীমান্ত এলাকায় তাদের বাড়ি। তৎকালীন কুমিল্লা জেলার এই এলাকাটি ছিল নিভৃতপল্লী এবং ভারতীয় পাহাড়ের পাদদেশে। প্রথম ভাবছিলেন, পাকিস্তানিরা ভারতীয় সীমান্তের এত কাছে কখনও আসবে না। তাদেরও গুলো করে হত্যা করবে না। হ্যাঁ ঠিকই, সালদানদীর কাছাকাছি এলাকায় পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন গ্রামে হত্যাকাণ্ড চালালেও তাদের গ্রামে আসেনি। এটাও তাদের আত্মবিশ্বাসের একটা কারণ হতে পারে।
মুক্তিযোদ্ধাদেরও তাদের গ্রামে আনাগোনা বেড়ে যায়। অনেক বড় বড় মুক্তিযোদ্ধার নিয়মিত আসা-যাওয়া চলে তাদের গ্রামে। ইতিহাসের বিখ্যাত বীর যোদ্ধা মেজর খালেদ মোশাররফ, ক্যাপ্টেন এ টি এম হায়দার, ক্যাপ্টেন আবু সালেক চৌধুরীর মতো মুক্তিযোদ্ধারা এক দুই দিন পর পরই আসতেন তাদের বাড়ি। মাঝে মাঝে তাদের কেউ কেউ দুয়েকদিন থাকতেনও। পাশের কৈখলা গ্রাম পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে গিয়ে সালদানদীতে পাকিস্তানি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটিতে আক্রমণ করতেন। কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতো যুদ্ধ কখনও কখনও স্বল্পসময়ের মধ্যেই তারা চলে আসতেন। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনী যাতে সালদানদী থেকে আর এগিয়ে আসতে না পারে সেই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে রাখেন তারা।
তাদের বাড়িতে সেইদিন অন্তত ৩০/৪০ জন মুক্তিযোদ্ধা অবস্থান করছিলেন। চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সুবেদার মনির সেই মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাদের বাড়িটা এমন জায়গায় অবস্থিত যেখানে মুক্তিবাহিনীর জন্য অনেকটা নিরাপদ ছিল। সালদানদীর কাছে হওয়ার পরও গাছগাছালিতে ঘেরা গ্রামটি ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়া এলাকা। সালদানদী ঘাঁটি থেকে নদী পেরিয়ে এই এলাকায় আসা পাকিস্তানি বাহিনীর জন্য ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরও পাকিস্তানি বাহিনী ছিল উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাদের শক্তি ছিল মুক্তিবাহিনীর চেয়ে অনেক বেশি। যদিও মনোবল ছিল মুক্তিবাহিনী তুলনায় অনেক কম ছিল অধিকাংশ সময়। শক্তিবলে এই পাকিস্তানিরা একসময় বড়বাগ মসজিদের সামনেও চলে আসত। কিন্তু মুক্তিবাহিনীর আক্রমণে তাদের পিছু হটতে হতো। একসময় মাজারের কাছেও বাংকার করে অবস্থান নিয়েছিল। কিন্তু টিকে থাকতে পারেনি।
তাদের বাড়ি থেকে মুক্তিবাহিনী পশ্চিমে গিয়ে আক্রমণ পরিচালনা করত। তাদের খাবারদাবারও সরবরাহ করা হতো তাদের বাড়ি থেকে। অনেক সময় গ্রামের মানুষজনও খাবারের ব্যবস্থা করত। মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে যাওয়ার সময় মফিজুল ইসলামও তাদের সঙ্গী হতেন। না, যুদ্ধ দেখার উদ্দেশে নয়। সহযোগিতা করার জন্যই যেতে হতো তার কিংবা তার বয়সের শিশুকিশোরদের। বিশেষ করে খাবার দিয়ে আসা এবং অস্ত্রসস্ত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করতেন তারা। ফলে সামান্য দূরে সালদানদীতে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর বাংকারও তার দেখার সুযোগ হয়েছিল। এত কাছাকাছি থেকে যে যুদ্ধ করা সম্ভব সেটাও তার দেখা সম্ভব হয়েছিল সেই সুবাদে।
পরিস্থিতির কারণেই যুদ্ধের শেষ পর্যায়েও তাদের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। বলতে গেলে পুরো গ্রামের মানুষই তখন একেকজন মুক্তিযোদ্ধা হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করছিল। সেই গ্রামেই একাত্তরের অক্টোবর মাসের প্রথম দিক হবে। শুক্রবার ছিল সেদিন। রোজা শুরু হয়েছে সেদিন। সকাল ৮টার দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন বাংকারে। দ্রুত ফিরে আসেন বাড়িতে। কারণ তখন ৮/৯ মাইল দূরে কালামুইড়া ব্রিজ থেকে পাকিস্তানি বাহিনী আর্টিলারি শেল নিক্ষেপ করছিল একটু পর পর। যে কোনও সময় মৃত্যু ঘটতে পারে সেসব বোমার আঘাতে।
বাড়িতে তখন অনেক মানুষ। প্রায় সবই ছিল মুক্তিযোদ্ধা। নিজেদের বাড়ির লোকজনও ছিল। প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ হচ্ছিল। মনে হয় পুরোদিনে তাদের গ্রামেই মাজার থেকে তাদের গ্রাম হরিপুর পর্যন্ত অন্তত শখানেক বোমা পড়েছে।
সকাল থেকে বোমা পড়তে থাকলেও দুপুরের দিকে তাদের গ্রামেও পড়তে শুরু করে। মানুষ এই বোমা থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছিলো না। বাড়ির বাইরে গেলে যদি বোমায় মারা যায় এই ভেবে বাড়িও ছাড়তে পারছিল না।
তাদের বাড়ির তিন ভিটায় ছিল তিনটি ঘর। পশ্চিমের ঘরে তিনি ঢুকলেন। দেখেন, তিল ধারণের ঠাঁই নেই ঘরে। দুপুরের দিকে হঠাৎ একটা বোমা এসে পড়ে উঠানে। একবারে মাঝখানে। আগুনের হুলকি দিয়ে স্প্লিন্টারগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। বিদ্যুৎ চমকাতে যতটা সময় লাগে ততটা সময়ও মনে হয় লাগেনি। ঘরের বেড়া ভেদ করে স্প্লিন্টারগুলো ভেতরে থাকা মানুষগুলোর গায়ে পড়ে। পূর্বদিকের ঘরের দরোজায় দাঁড়ানো ছিলেন মফিজুল ইসলাম। স্প্লিন্টারের আঘাতে তিনি নেতিয়ে পড়েন মাটিতে। কানে আসতে থাকে চিৎকারের শব্দ। গোঙানির শব্দ। কিন্তু ওঠে গিয়ে কাউকে টেনে বের করবেন কিংবা সেবা-সশ্রুষা করবেন সেই অবস্থা নেই তার। নজরুল কোম্পানির কমান্ডার প্রকৌশলী নজরুল ইসলামও ছিলেন তার অধিনস্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। উত্তরের ঘরের দরজার সামনে উঠানে ছিলেন বায়েক হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আব্দুল মালেক। মনে হয় তিনি বেশি মানুষের ঘর পশ্চিমের ভিটায় আসতে চাইছিলেন। বোমার বিকট শব্দের ঝাঁঝ তখনও কানে বাজছে। আর্তনাদও কানে আসছে এরই মধ্যে।
ঘাতক বোমার আঘাতে ইতোমধ্যে রক্তাক্ত হয়ে গেছে পুরো ঘরের মানুষ। নজরুল কোম্পানির অধিনায়ক প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, মফিজুল ইসলামের চাচী সুফিয়া খাতুন এবং আব্দুল মালেক মারাত্মক আহত হয়ে কাৎরাচ্ছিলেন। আব্দুল মালেক সাহেবও যায় যায় অবস্থা। ইপিআর এর আব্দুল আজিজ শাহাদত বরণ করেন। ঘটনাস্থলেই মোট তিনজন শাহাদত বরণ করলেন।
গ্রামের মানুষ এই বোমা বর্ষণের মধ্যেও দৌড়ে এল। খুব বেশি নয়। তারপরও জীবিতরা যেন বেঁচে থাকার আশা দেখলেন। মফিজুল ইসলাম সবই দেখছিলেন। দ্রুত গ্রামের মানুষেরা দরজা ভেঙ্গে তক্তা আলাদা করে নিলেন। ৯জন মানুষ মারাত্মক আহত তাদের দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে। একমাত্র চিকিৎসার জায়গা ভারতের কোনাবন ও আগরতলা। আহতদের তক্তায় শুইয়ে দড়ি দিয়ে কাঁধে করে গ্রামের মানুষ নিয়ে গেলেন কোনাবন। ওখানে পৌঁছানোর পরও আব্দুল মালেক এর জ্ঞান ছিল। তিনি তার পাশে তক্তায় শোয়া ছাত্রকে বললেন, আমাকে মাফ করে দিও। মনে হয় কথাটা বলার কিছু সময়ও যায়নি। আব্দুল মালেক মফিজুল ইসলামের সামনেই মৃত্যুবরণ করলেন। এদিকে সেই অবস্থায়ই আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হতে থাকে। কিন্তু কাউকেই হাসপাতালে ভর্তি না করিয়ে চিকিৎসা চালানো সম্ভব নয়। পাঠিয়ে দেওয়া হয় আগরতলা জিবি হাসপাতালে।
এদিকে আব্দুল মালেক মাস্টার এর লাশ দাফন করতে তার ছাত্ররা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের কথা- তাদের শিক্ষককে ভারতে দাফন করা যাবে না। কিন্তু বাংলাদেশ এলাকায় যেভাবে বোমা পড়ছে সেখানে তাদের নিরাপত্তাই অনিশ্চিত। এমন কঠিন অবস্থায় ছাত্র এবং অভিভাবকরা সিদ্ধান্ত নিলেন ধর্মীয় মর্যাদায় তাদের শিক্ষককে দেশের মাটিতে দাফন করা হবে। শেষ পর্যন্ত সবাই মিলে মাদলা কবরস্থানে এনে দাফন করা হয়। কয়েকজন লাশ নিয়ে যাবে মাদলা এমন সিদ্ধান্ত হয়। তারমধ্যে ছিলেন আবু তাহের, আব্দুল জব্বার মিয়া। নিয়তির কী নির্মমতা। আব্দুল জাব্বার কী জানতে পারতেন এর কদিন বাদেই তাকে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলোতে প্রাণ হারাতে হবে?
কিন্তু মফিজুল ইসলাম তার প্রিয় শিক্ষক কিংবা তার মাতৃসম চাচীর জানাজায় শরিক হতে পারলেন না॥ তাদের গ্রামের বেশ কজন মারা যায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলো ও বোমায়। কারও জানাজা পড়ার সুযোগ পেলেন না মফিজুল।
এদিকে মফিজুল ইসলামের চাচীর লাশ পড়ে থাকে বাড়িতেই। দুর্ঘটনার দিন কারও পক্ষেই সম্ভব হয়নি লাশ দাফন করার। কারণ সবাই আহতদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পরদিনকয়েকজন এসে সাধ্যমত ধর্মীয় মর্যাদায় তার গোসল জানাজা পড়ান। কয়েকজন মিলে গ্রামের ঈদগাহ ময়দানের পাশে মফিজুলের চাচীর দাফন সম্পন্ন করেন।
স্বাধীনতা লাভের ৫১ বছর পরও মফিজুল ইসলাম সেই দুর্বিসহ স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি লেখককে নিয়ে যান তার বাড়ি, যেখানে হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল। তিনি উত্তরের ঘরের বেড়ার কিছু অংশ দেখান। বলেন, ওই সময় ঝাঁঝড়া হয়ে গিয়েছিল বেড়ার টিনগুলো। সেগুলো থেকে বেঁচে যাওয়া কিছু টিন তারা আবার বেড়ায় ব্যবহার করেছেন। ৫১ বছর পরও টিনের ছিদ্রগুলো দেখে মনে হয় কিছু সময় আগে যেন টিনগুলো কেউ ছেনি দিয়ে ছিদ্র করে গিয়েছে। আর এই টিনের ছিদ্রের মতোই মানসিক ক্ষত নিয়ে বেঁচে আছেন মফিজুল ইসলাম।
রাজাকার তবদিল ডেকে নিয়ে হত্যা করে হারুণকে _
ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কসবা উপজেলার কাইমপুর গ্রামের অশতিপর বৃদ্ধ আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া। বাবা সুবেদ আলী ভূঁইয়া। শ্রবণশক্তি নেই বললেই চলে। চোখেও দেখেন কম। কিছু ইশারা এবং কিছু উচ্চ স্বরে কথা বলে শ্বশুরের সেবা করেন তার পুত্র বধূ। কিন্তু স্মৃতি তার অমলিন।
বয়স জিজ্ঞেস করতেই দ্রুত জবাব দিয়ে দিলেন ৯৫। মনে আছে কি একাত্তরের কথা? আঞ্চলিক ভাষায়ই জবাব দিলেন- এইডা কয় কিতা? (এটা কি বলেন?)
ভাদ্র মাসেরই কোনও একদিন। সকাল ১১টা বাজে মনে হয়। হঠাৎ শোনা গেল- মানুষ সোরগোল করছে। যে যেভাবে পারে পালাচ্ছে। এমন দৃশ্য তো আর নতুন নয়। তারপরও সতর্ক থাকতে হয়। কারণ পাকিস্তানিদের সামনে পড়লে তো রক্ষা থাকবে না।
তাই অনুমান হতেই মান্নান ভূঁইয়ারা বাড়ির পশ্চিমে জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। তার সাথে মেয়ে লোক ও শিশুরাও আছে।
সেখানে জঙ্গলে থেকেই দেখলেন কিছু বাড়িতে আগুন জ্বলছে। তার মানে বাড়িগুলোতে এখনও পাকিস্তানিরা অবস্থান করছে। কিংবা সদ্য স্থান ত্যাগ করেছে। আগুন নিভানোর জন্য যাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। তাই বসে বসে আল্লাহকে ডাকছিলেন।
ঘন্টাখানেকও যায়নি। কানে বাজলো গুলোর শব্দ। বেশি গুলো নয়। দুই তিনটা হবে হয়তো। ভয়ে কাঁপতে থাকলেন আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া। ভাবলেন, হায়রে কে না জানি জীবন হারালো পাকিস্তানিদের হাতে। আতঙ্ক আর সন্দেহ নিয়ে কাটিয়ে দিলেন আরও প্রায় ঘন্টাখানেক। মনে হল আশেপাশের মানুষজন চলাফেরা শুরু করেছে। তখন বেরিয়ে এলেন জঙ্গল থেকে।
বেরিয়েই শুনলেন মিস্ত্রি বাড়ির হরিপদ সূত্রধরকে পাকিস্তানিরা গুলো করেছে। একজন বলল, ওর মাথাটা গুড়িয়ে ফেলেছে। মান্নান ভূঁইয়া চিন্তা করলেন হায়রে বেচারা। সেই ছোট বেলা থেকে ছেলেটাকে দেখছেন। যখন তখন ডাক দিলে দৌড়ে চলে আসে। এমন একটা ছেলেকে কিনা গুলো করল!
দৌড়ে গেলেন মিস্ত্রি বাড়িতে। অন্তত ৫/৬জন মানুষ তখন মিস্ত্রি বাড়িতে। কাছে গিয়ে দেখেন, হরিপদর কপালে গুলো লেগেছে। চোখের উপর দিয়ে হাড্ডি স্পর্শ করে বাম থেকে ডাইনে চলে গেছে। মনে হয় চিকিৎসা করলে বেঁচে যেতে পারে।
তিনি ও গ্রামের ২/৩জন মিলে তাকে ভারতে পাঠানোর আয়োজন করলেন। তখনও হরিপদকে নিয়ে মানুষ ভারতে রওনা হয়নি। (২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে তথ্য সংগ্রহকালেও হরিপদ জীবিত ছিলেন।) এমন সময় একজন এসে বলে, ভুঁইয়া আপনার ভাইকে গুলো করেছে পাকিস্তানিরা। থতমত খেয়ে যান মান্নান।
এক দৌড়ে নিজ বাড়ির দিকে রওনা হন। বাড়ির সামনে গিয়ে দেখেন কয়েকজন দৌড়াচ্ছে বাড়ির পূর্বদিকে। তিনিও গেলেন সেখানে।
দেখেন পুকুরের কোণায় পড়ে আছে তার ভাই হারুণ ভূঁইয়া। পিঠ দিয়ে রক্ত পড়ছে। উরুতেও গুলো লেগেছে। বুক ভেদ করে একটা গুলো গেছে তার ভাইর। তখনও কথা বলতে পারে। তার কাছ থেকেই তিনি শুনতে পারেন সব কথা। হারুণ জানায়- পাকিস্তানিদের এদিকে আসতে দেখে তিনি পুকুরের পূর্বদিকে হাঁটতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি পুকুর পাড়ের একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু চোখ পড়ে যায় রাজাকার তবদিলের। তবদিলের বাড়ি মন্দবাগ গ্রামে। আগেরই পরিচিত মানুষ। তবদিল তাকে কাছে ডাকে। বলে হারুণ এসো তোমাকে কিছু করা হবে না।
সরল বিশ্বাসে হারুণ রাজাকার তবদিলের ডাক শুনে এগিয়ে যায়। তার হাতে তখনও ঘাস কাটার কাঁচি ও টুকরি। দুটো নিয়েই সে এগিয়ে যায় তবদিলের কাছে।
পুকুরের কোণায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি এক সৈন্য পরপর তিনটি গুলো করে। সেখানেই লুটিয়ে পড়ে হারুণ ভূঁইয়া।
অতঃপর মান্নান ভূঁইয়া লোক খুঁজতে থাকেন তার ভাইকে ভারতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু তেমন মানুষ পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ গ্রামে যারা তখনও ছিল তাদের প্রায় সবাই বয়সের দিক থেকে খুবই প্রবীণ। তরুণ যুবকদের সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত গ্রামের হাকিম ডাক্তার ও দুইজনকে পাওয়া গেল যারা তাকে বয়ে নিয়ে যাবে ভারতে।
ঘরের দরজার একটা পাল্লা খুলে সেই পাল্লায় শোয়ানো হল হারুণকে। তারপর মাথায় করে নিয়ে রওনা হলেন তারা। মাইল দুয়েক নিয়ে যেতে পারলেই ভারতের কোনাবন। সেখানে গাড়ি চলে। গাড়িতে করে আগরতলা নিতে পারলে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো যাবে।
মাঝখানে অদূরে শালদানদীতে আবার পাকিস্তানিদের ক্যাম্প। বায়েকেও। সুতরাং পথ পারি দেওয়া যেমন তেমন কথা নয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাছ দিয়ে যেতে হবে চোখ ফাঁকি দিয়ে। যদি দেখে ফেলে তাহলে নিশ্চিৎ গুলো খেতে হবে।
এমন ঝুকি নিয়েই রওনা হলেন মান্নান ভূইয়া তার ভাইকে নিয়ে। ভালয় ভালয় পাড়ি দিলেন মন্দবাগ স্টেশন। ভারতের কোনাবন পৌঁছানোর পর মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ভাবলেন তার ভাইকে বাঁচানো সম্ভব হবে।
আলাদা গাড়ি রিজার্ভ করা সম্ভব হবে না ভেবে তিনি ভাইকে একটি হলার জাতীয় গাড়িতে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ওঠালেন। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হারুণ ভুঁইয়া ইন্তেকাল করেন। কী বিপদের মধ্যে যে তখন তাকে পড়তে হয়েছে তাদের! কোনও আত্মীয় স্বজন নেই কোথাও। বাস থেকেও নেমে যেতে হয়। এরমধ্যে সিদ্ধান্ত নেন। লাশ দাফন করতে হবে বাংলাদেশের ভিতর। কিন্তু সেটা খুবই ঝুকিপূর্ণ। তারপরও চেষ্টা করতে হবে।
সেই ভেবে লাশ নিয়ে তারা রওনা হন চাটুয়াখোলায়। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের একটি গ্রাম। উচু জায়াগা। ওখানে লাশ এনে কাছাকাছি আত্মীয়-স্বজন যারা ছিল তাদেরকে খবর দেন। ঐ গ্রামেও কিছু মানুষ ছিল। তাদের সহযোগিতায় সেখানেই ভাইয়ের দাফন করেন।
মান্নান ভূঁইয়া প্রায় শত বছরের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। দীর্ঘ জীবনে এত বড় ঘটনা আর দেখেননি। বিশ্বযুদ্ধের কথাও তার মনে আছে। কিন্তু তিনি মনে করেন না সেই বিশ্বযুদ্ধও আমাদের জন্য কোনও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একাত্তরে যেভাবে রাজাকাররা এদেশের মানুষ হত্যা করার জন্য অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে তা ভোলার মতো নয়।
সারাবাংলা/এসবিডিই
ঈদসংখ্যা ২০২৩ একাত্তরের নৃশংসতার খণ্ডচিত্র মুক্তিযুদ্ধ মোস্তফা হোসেইন সাহিত্য