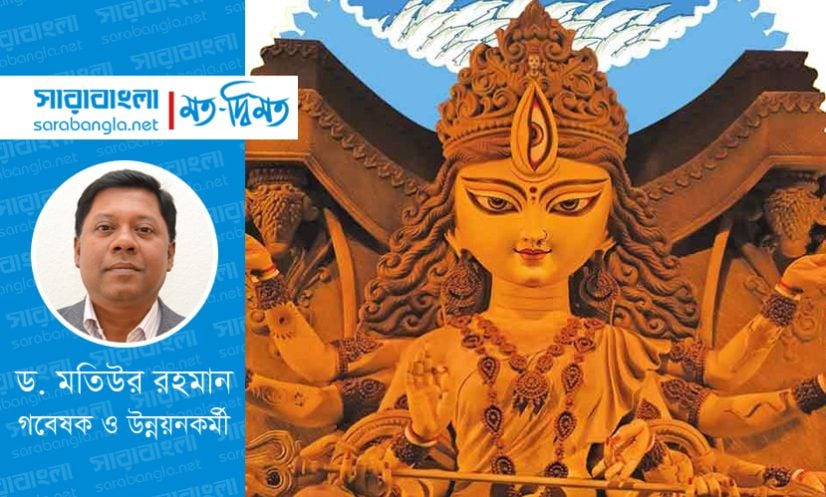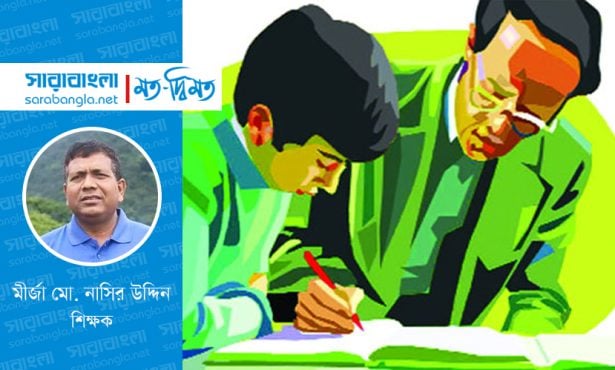দুর্গাপূজা কেবল একটি বার্ষিক ধর্মীয় আরাধনা নয়; এটি দক্ষিণ এশিয়ার, বিশেষত বাঙালি সংস্কৃতি ও সমাজের, এক জটিল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম ও ওড়িশার মতো অঞ্চলে এই উৎসব কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রকে আলোকিত করে না, বরং সামাজিক সংহতি, সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ, অর্থনৈতিক গতিশীলতা এবং আত্মপরিচয়ের প্রতীকী যুদ্ধকেও প্রভাবিত করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে, দুর্গাপূজা হলো এক বহুমাত্রিক লেন্স, যার মাধ্যমে আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিচয় কীভাবে একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে সমাজের কাঠামো ও গতিশীলতাকে প্রভাবিত করে, তা পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই উৎসব চিরায়ত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে এক সক্রিয় সেতুবন্ধন রচনা করে, যা আধুনিক দক্ষিণ এশিয়ার জীবনযাত্রার জটিলতা ও বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তোলে।
দুর্গাপূজার মূলে রয়েছে দেবী দুর্গার মহিষাসুরের উপর বিজয়, যা শুধুমাত্র ধর্মীয় আখ্যান হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং এটি সৃষ্টির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রতীক হিসেবে সমাজের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে কাজ করে। এই বিজয় অশুভ শক্তি, অন্যায় ও বিশৃঙ্খলার উপর শুভ, ন্যায় ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠার প্রতীক। এই পৌরাণিক কাহিনীর মাধ্যমে সমাজ তার নৈতিক কাঠামোকে বার্ষিক চক্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে, যা সামাজিক নিয়মাবলী (norms) মান্য করার জন্য এক অন্তর্নিহিত প্রেরণা যোগায়। দেবী দুর্গা তাই কেবল উপাস্য নন, তিনি সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তি এবং নৈতিক নির্দেশিকার প্রতিচ্ছবি।
ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ এমিল দুরখেইমের কার্যকারিতা তত্ত্ব এই উৎসবের সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণে মুখ্য। তাঁর মতে, দুর্গাপূজা হলো সামাজিক সংহতির এক শক্তিশালী আধার। উৎসবের প্রস্তুতির শুরু থেকে—যেমন স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ, প্যান্ডেল নির্মাণ, প্রতিমা স্থাপন—এবং সমাপ্তি পর্যন্ত—যেমন সম্মিলিত আরতি, ভোগ বিতরণ ও বিসর্জন—প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান মানুষের মধ্যে এক গভীর সমবায় চেতনা সৃষ্টি করে। এই সম্মিলিত অংশগ্রহণ এক ধরনের ‘সম্মিলিত উচ্ছ্বাস’ (Collective Effervescence) তৈরি করে, যেখানে ব্যক্তিগত আবেগ ও বিচ্ছিন্নতা সমষ্টিগত অভিজ্ঞতা ও একাত্মতায় বিলীন হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়া ব্যক্তি এবং বৃহত্তর সমাজের মধ্যে একটি গভীর নৈতিক বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে, যার মাধ্যমে সামাজিক আদর্শ ও নিয়মাবলীগুলি পুনরায় সমর্থিত ও দৃঢ় হয়, এবং সমাজ নিজেই তার ‘পূজনীয় প্রতীক’ (Sacred Symbol) রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই সম্মিলিত আচার-অনুষ্ঠান সমাজের স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অপরিহার্য।
দুর্গাপূজার বর্তমান রূপের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো শৈল্পিকতা ও সৃজনশীলতার উপর অত্যাধিক গুরুত্বারোপ, যা ‘থিম পূজা’-র মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মণ্ডপের থিম, স্থাপত্যশৈলী, প্রতিমার নির্মাণশৈলী এবং আয়োজিত সাংস্কৃতিক পরিবেশনা—এসবই স্থানীয় ও সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি অত্যাধুনিক প্রকাশ। এই থিমগুলি প্রায়শই সামাজিক, রাজনৈতিক বা পরিবেশগত বার্তা বহন করে, যা উৎসবকে একটি সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত করে।
পিয়েরে বুর্দিউর সাংস্কৃতিক পুঁজির তত্ত্ব এই শৈল্পিক দিকটিকে গভীরতরভাবে ব্যাখ্যা করে। থিম পূজা বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করা সমাজের মধ্যে সামাজিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির প্রদর্শনের একটি মাধ্যম। প্যান্ডেলের স্থাপত্যের জটিলতা, ব্যবহৃত উপকরণের গুণগত মান, এবং থিমের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিনবত্ব কেবল ধর্মীয় অনুরাগ বা ভক্তি প্রদর্শন করে না, বরং এটি সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জ্ঞান, নান্দনিক বোঝাপড়া এবং সামাজিক গৌরব প্রদর্শন করে। শহরাঞ্চলে, বিশেষত মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত শ্রেণী, এই উৎসবের মাধ্যমে তাদের উন্নত সাংস্কৃতিক পরিচয় ও স্বাদ (Taste) প্রতিফলিত করে, যা ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক স্বীকৃতি ও বৈধতা লাভে সহায়তা করে। পূজা কমিটিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিযোগিতা কার্যত এক ধরনের ‘প্রতীকী সংঘাত’ (Symbolic Struggle), যেখানে বিজয় সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদাকে সুদৃঢ় করে এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজস্ব ‘হ্যাবিটাস’ (Habitus) বা স্বভাবগত পরিচিতি গড়ে তোলে।
দুর্গাপূজা কেবল আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র নয়, এটি এক বিশাল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র, যা প্রথা এবং আধুনিক অর্থনৈতিক কাঠামোর সংযোগস্থল হিসেবে কাজ করে। এই উৎসবের কারণে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার একটি অস্থায়ী বাজার তৈরি হয়, যা কুমারটুলির মৃৎশিল্পী, প্যান্ডেল কারিগর, আলোকসজ্জা শিল্পী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ইভেন্ট ম্যানেজার এবং কর্পোরেট স্পন্সরদের নিয়ে গঠিত এক গতিশীল অর্থনৈতিক বাস্তুতন্ত্র তৈরি করে। এই অর্থনৈতিক ভূমিকা উৎসবটিকে আধুনিক সমাজে এক অপরিহার্য ‘ইন্ডাস্ট্রি’তে পরিণত করেছে।
অ্যান্থনি গিডেন্সের কাঠামোবাদী তত্ত্ব (Structuration Theory) ব্যবহার করে, আমরা দেখতে পাই কীভাবে প্রথা (ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় আচার) সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো দ্বারা প্রভাবিত হয় (যেমন কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশ) এবং একইসাথে, সেই কাঠামোও নতুন সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (যেমন থিম ও বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে) পুনরায় উৎপাদিত হয়। কর্পোরেট স্পন্সরশিপ, গণমাধ্যমের ব্যাপক প্রচার এবং পর্যটন শিল্পের সঙ্গে সংযোগ এই উৎসবকে বাণিজ্যিকীকরণ এবং বৈশ্বিকীকরণের প্রভাবে এক জটিল সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছে। পূজা তাই কেবল ধর্মীয় ব্যয় নয়, এটি এক ধরনের ‘উপভোগের অর্থনীতি’ (Economy of Consumption) তৈরি করে, যা গ্রামীণ শিল্প ও শহুরে বাণিজ্যের মধ্যে এক নতুন আর্থ-সামাজিক যোগসূত্র তৈরি করেছে। এই অর্থনৈতিক কাঠামো দেখায় যে ধর্মীয় আচারগুলি কীভাবে আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় টিকে থাকে এবং এর অংশ হয়ে ওঠে।
নগর জীবনে দুর্গাপূজা সামাজিক স্থান (Social Space) এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের পরিচয়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। আধুনিক নগরে যেখানে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা প্রায়শই দেখা যায়, সেখানে পাড়া বা মহল্লাভিত্তিক পূজা কমিটিগুলো তাদের প্যান্ডেলকে সবচেয়ে আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে এক তীব্র স্থানীয় একতা (Local Solidarity) সৃষ্টি করে। এই প্রতিযোগিতাটি কেবল সৌন্দর্য প্রদর্শনের নয়, এটি সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক মানচিত্র (Social Mapping) এবং সামাজিক পুঁজিকে (Social Capital) পুনর্বিন্যস্ত করার একটি প্রক্রিয়া।
প্রতীকী মিথস্ক্রিয়া তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই অস্থায়ী মণ্ডপগুলি এক ধরনের ‘তৃতীয় স্থান’ (Third Place) বা অস্থায়ী সম্প্রদায়ের (Temporary Community) জন্ম দেয়। এই স্থাপনাগুলি বহু প্রজন্ম ও ভিন্ন আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষকে একত্রিত করে, যারা সাধারণত শহুরে জীবনযাত্রার কারণে বিচ্ছিন্ন থাকে। প্যান্ডেল ও তার থিমের মাধ্যমে তারা তাদের স্থানীয় পরিচিতি বা ‘পাড়া’-র গৌরব এবং সামাজিক সামর্থ্যকে প্রতীকীভাবে তুলে ধরে। এই প্রকাশ শুধু ধর্মীয় অনুরাগ বা ভক্তির প্রতিফলন নয়, বরং সামাজিক অর্থবোধ, গোষ্ঠীগত পরিচয় নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক সামর্থ্যের প্রতীকী প্রকাশ। উৎসবটি এই অস্থায়ী কাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে নগর পরিসরের দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি ভেঙে দেয় এবং এক সাময়িক সময়ের জন্য স্বেচ্ছাচারী আনন্দের (Carnivalesque) পরিবেশ সৃষ্টি করে।
দুর্গাপূজা লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতা এবং নারীর প্রতীকী অবস্থানের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেবী দুর্গার কেন্দ্রীয় অবস্থান নারীর শক্তি (শক্তি তত্ত্ব), সুরক্ষা এবং ন্যায়ের প্রতীক, যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রতীকীভাবে চ্যালেঞ্জ করে। দেবী রূপে নারী ক্ষমতাবান, স্বায়ত্তশাসিত এবং নৈতিক কর্তৃত্বের প্রতীক।
তবে, এই প্রতীকী আধিপত্যের পাশাপাশি উৎসবের বাস্তব সামাজিক আচারে একটি গভীর দ্বৈততা (Duality) লক্ষ্য করা যায়। যদিও প্রতীকীভাবে নারীশক্তি পূজিত হয়, কিন্তু উৎসবের সাংগঠনিক, আর্থিক ও নীতিনির্ধারক নেতৃত্বে সাধারণত পুরুষদেরই প্রাধান্য থাকে। অন্যদিকে, ঘরোয়া পূজা, আলপনা, রন্ধন, দেবীর সাজসজ্জা এবং প্রথাগত দায়িত্বগুলোতে নারীরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই দ্বৈততা দেখায় যে কীভাবে সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠান একইসঙ্গে লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতা কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে (দেবীর মূর্তির মাধ্যমে) এবং ঐতিহ্যবাহী লিঙ্গ-ভূমিকাগুলোকেও বজায় রাখে (বাস্তব সংগঠনের মাধ্যমে)। এটি নারীকে একইসঙ্গে ‘পূজনীয় দেবী’ এবং ‘সামাজিক নিয়ন্ত্রণে’ রাখার এক সূক্ষ্ম কৌশল, যা নারীর সামাজিক অবস্থানকে পুনর্বিবেচনা করার সুযোগ দেয়।
প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের জন্য দুর্গাপূজা কেবল একটি উৎসব নয়, এটি সাংস্কৃতিক স্মৃতি এবং সামাজিক বন্ধন সংরক্ষণের একটি অপরিহার্য মাধ্যম। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং অন্যান্য দেশে প্রবাসীরা এই উৎসবকে কেন্দ্র করে একত্রিত হয়, যা তাদের সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে।
বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসনের কল্পিত সম্প্রদায়ের তত্ত্ব (Imagined Communities) অনুসারে, দুর্গাপূজা ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন বাঙালি সম্প্রদায়কে একজাতীয় সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যুক্ত করে। এই উৎসব প্রবাসে তাদের আত্মপরিচয় পুনর্নির্মাণে এবং মূলভূমির সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে সাহায্য করে। প্রবাসী পূজাগুলো প্রায়শই ‘বাঙালিয়ানা’ রক্ষার এক প্রতীকী সংগ্রাম হিসেবে কাজ করে, যা অভিবাসী প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য ও ভাষাকে জীবন্ত রাখে। এটি কেবল ধর্মীয় আচার নয়, বরং বৈশ্বিক বাঙালি সংস্কৃতির এক স্থিতিস্থাপক প্রদর্শনী (Resilient Exhibition)।
উৎসবটি ঐক্যের প্রতীক হলেও, এটি বিদ্যমান সামাজিক স্তর ও বৈষম্যকেও প্রতিফলিত করে। কার্ল মার্কসের তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ অনুসারে, প্যান্ডেলের প্রতিযোগিতার মাত্রা, স্পন্সরশিপের ধরণ এবং জনসমাগমের প্রকৃতি প্রায়শই আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং ক্ষমতার কাঠামোর ভিন্নতাকে স্পষ্ট করে তোলে। বড় ও থিম-ভিত্তিক পূজাগুলো সমাজের উচ্চবিত্তের আর্থিক ও সামাজিক আধিপত্যকে প্রতীকীভাবে প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে ছোট ও স্থানীয় পূজাগুলো সীমিত সম্পদের সঙ্গে সংগ্রাম করে। দুর্গাপূজা তাই সামাজিক শক্তির কাঠামো এবং সম্পদ বিতরণের একটি আয়না, যা বিদ্যমান শ্রেণী বিভাজনকে প্রতিফলিত করে এবং কখনো কখনো পুনঃউৎপাদন করে।
সাম্প্রতিককালে পরিবেশগত প্রভাব একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক আলোচনার বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রতিমা নির্মাণে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পেইন্ট ব্যবহার এবং বিসর্জনের ফলে জলজ পরিবেশের দূষণ—এই প্রথাগত আচারকে পরিবেশগত ও নৈতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানায়। সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সংঘাতটি দেখায় যে কীভাবে ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক আচারগুলি আধুনিক পরিবেশগত এবং নৈতিক চাপের মুখে পরিবর্তিত হতে বাধ্য হচ্ছে। জীব-বৈচিত্র্য বান্ধব উদ্যোগ এবং সচেতনতা কর্মসূচিগুলো পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক আচারের সমন্বয়ের উদাহরণ। দুর্গাপূজা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতি, সমাজ এবং পরিবেশের মধ্যেকার চলমান এবং জটিল সম্পর্ককে উন্মোচিত করে।
লেখক: গবেষক ও উন্নয়নকর্মী